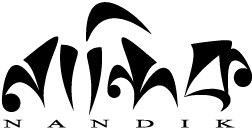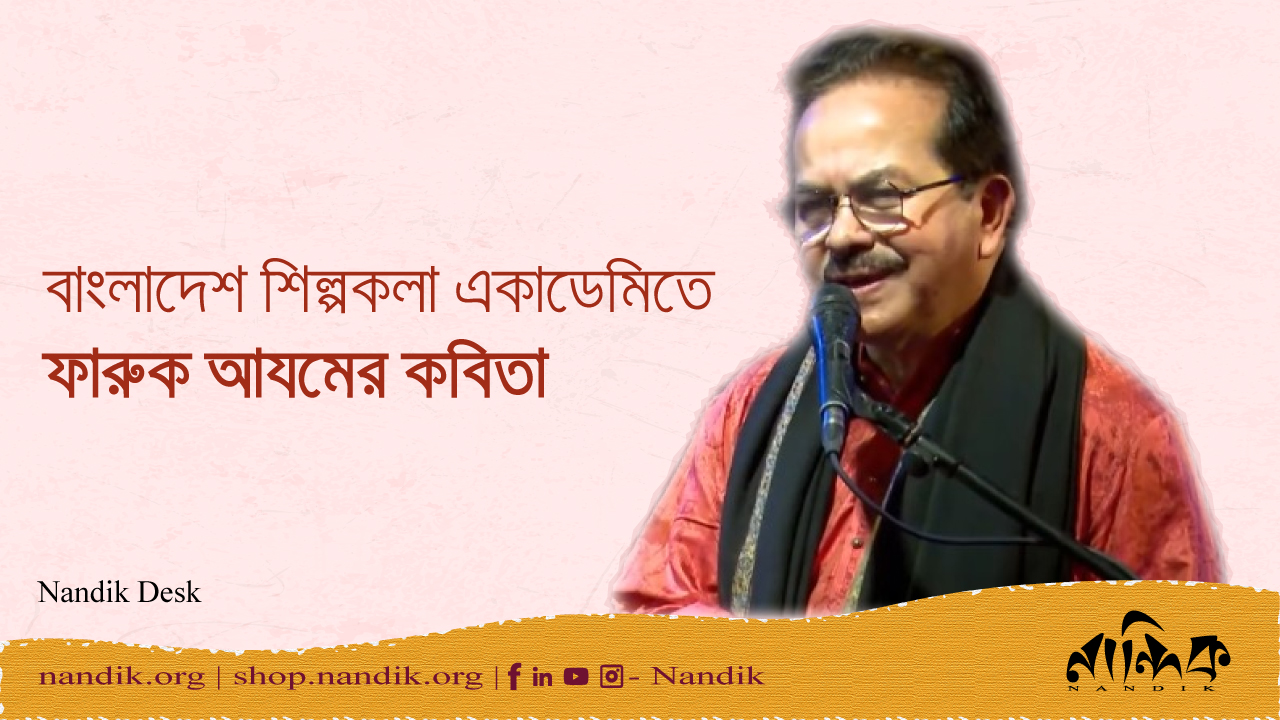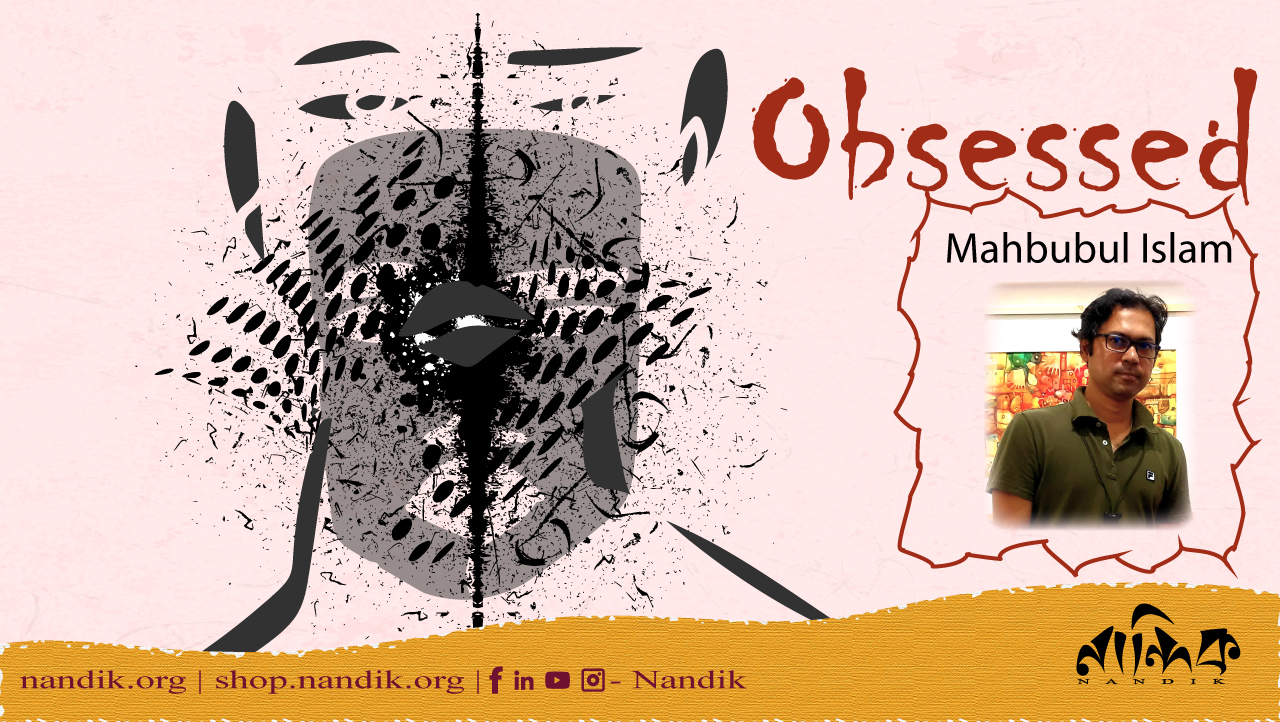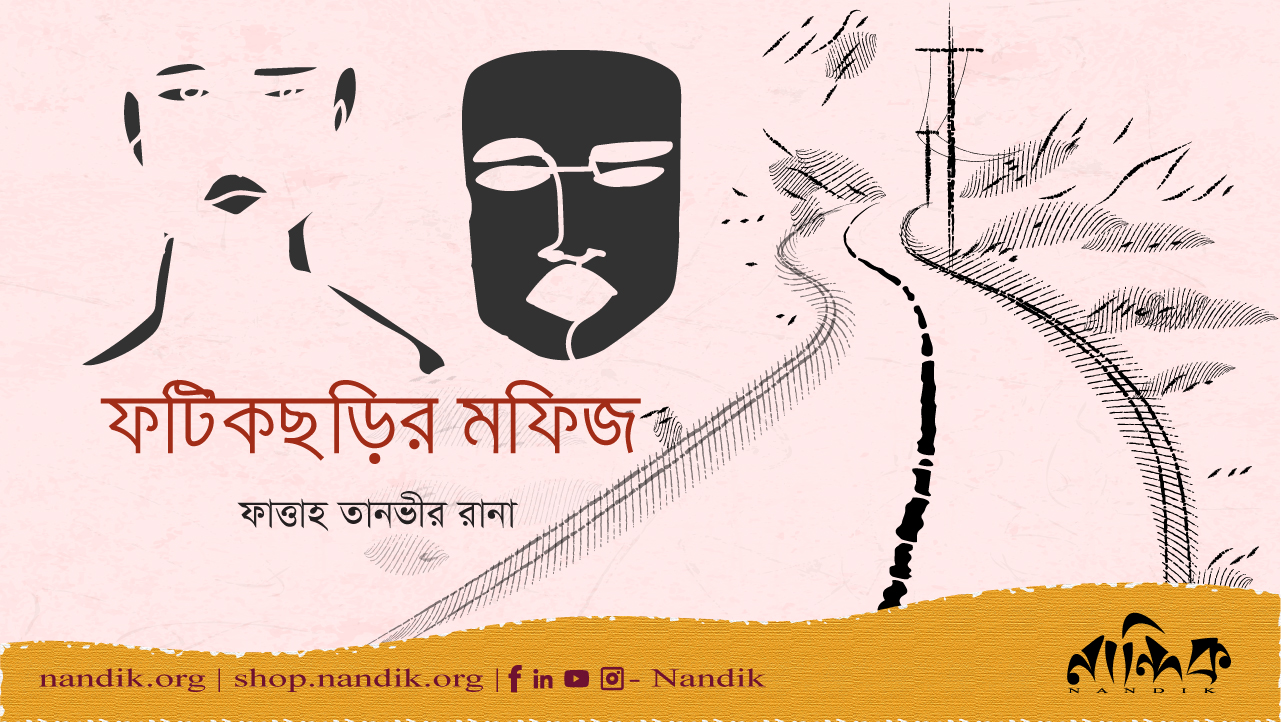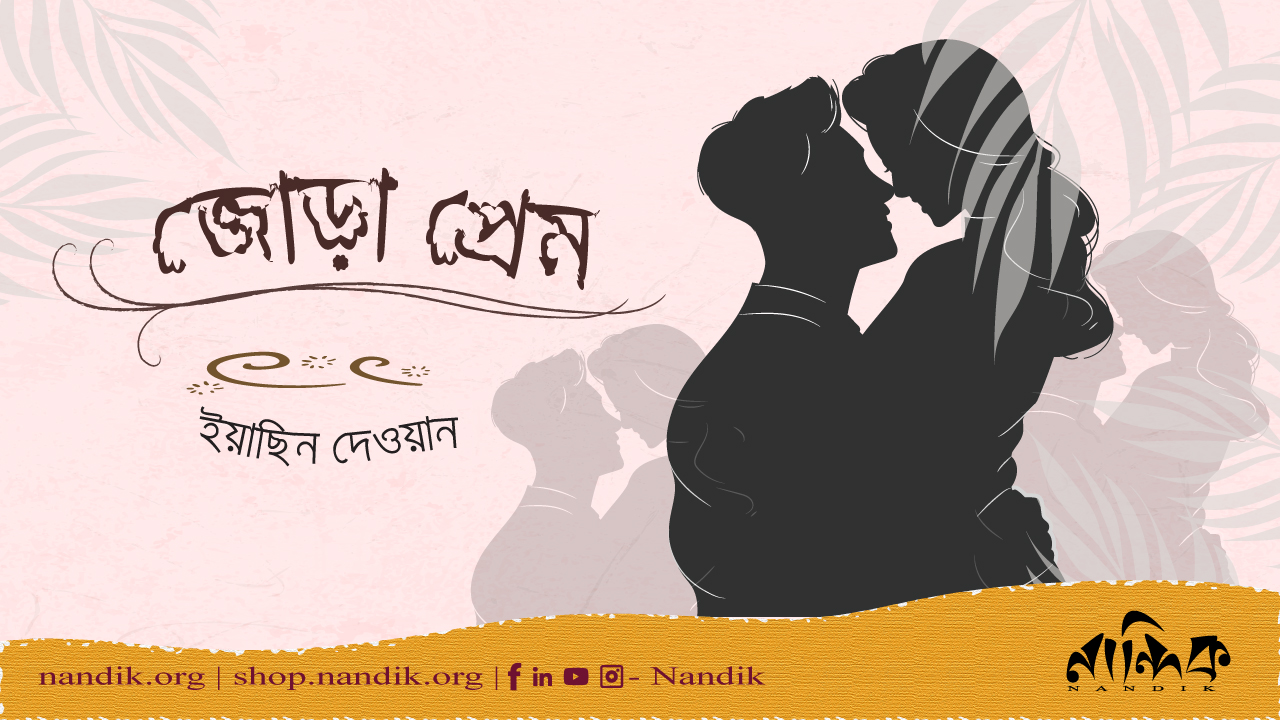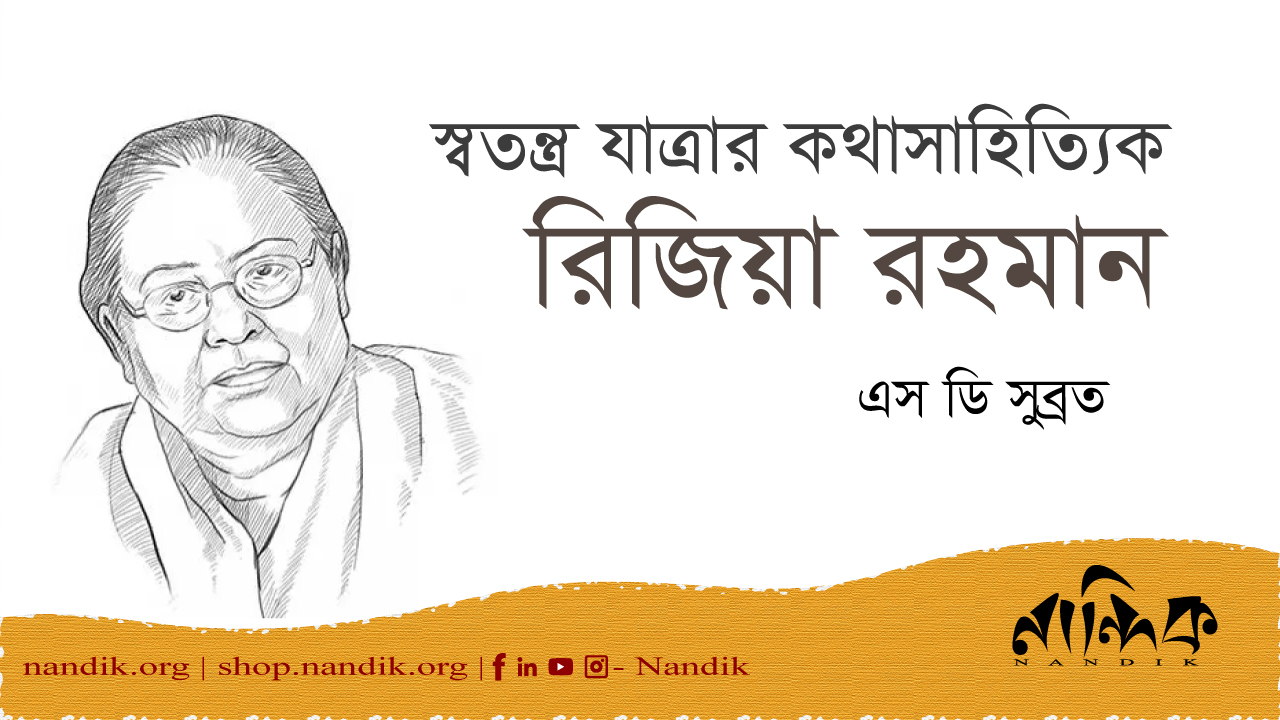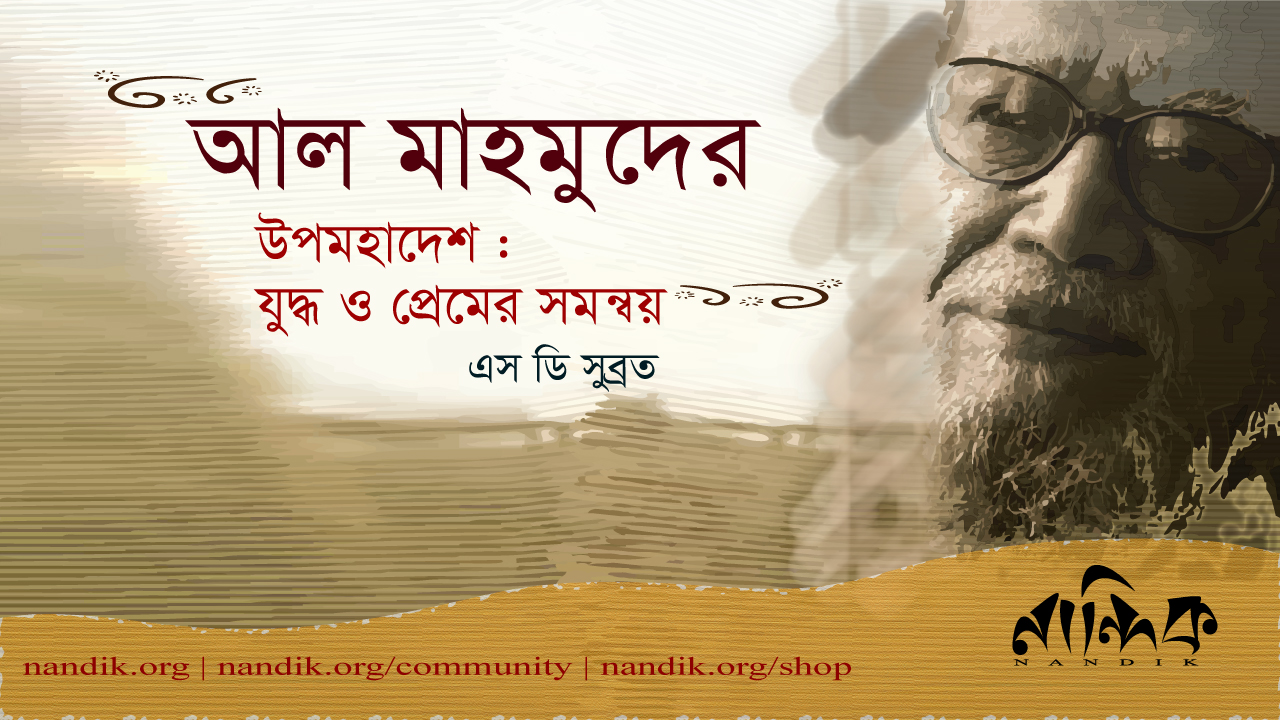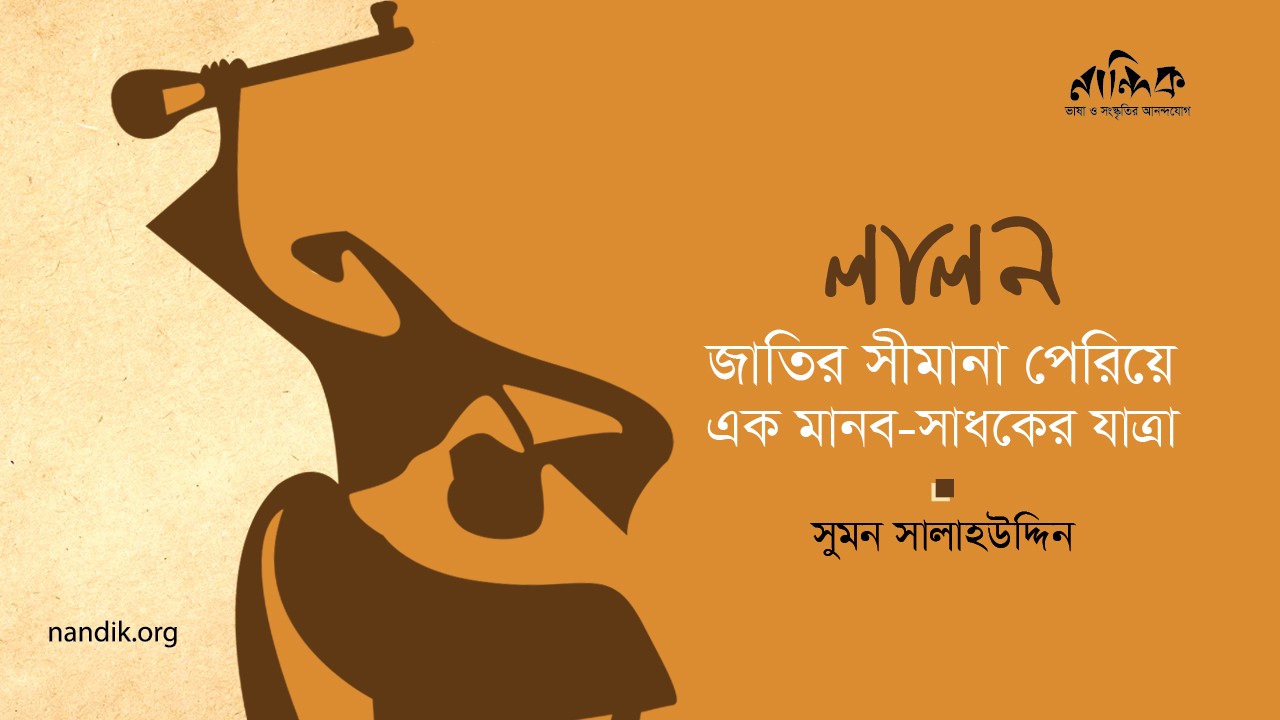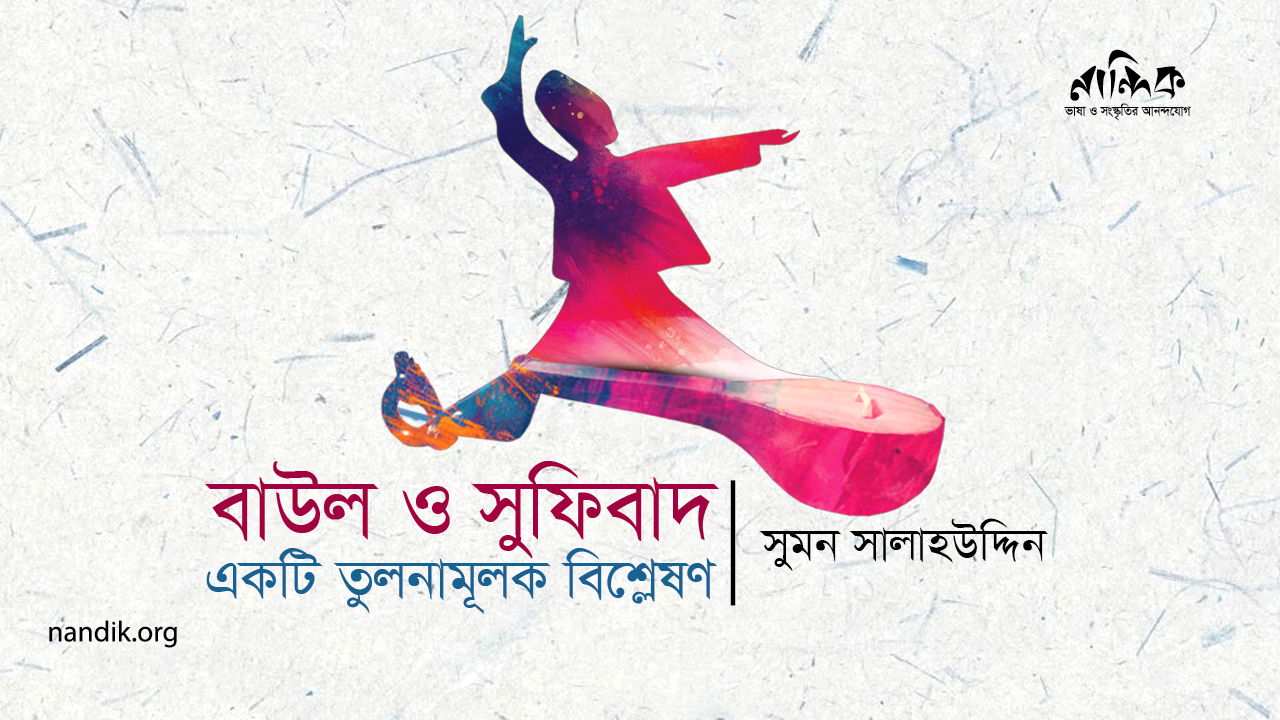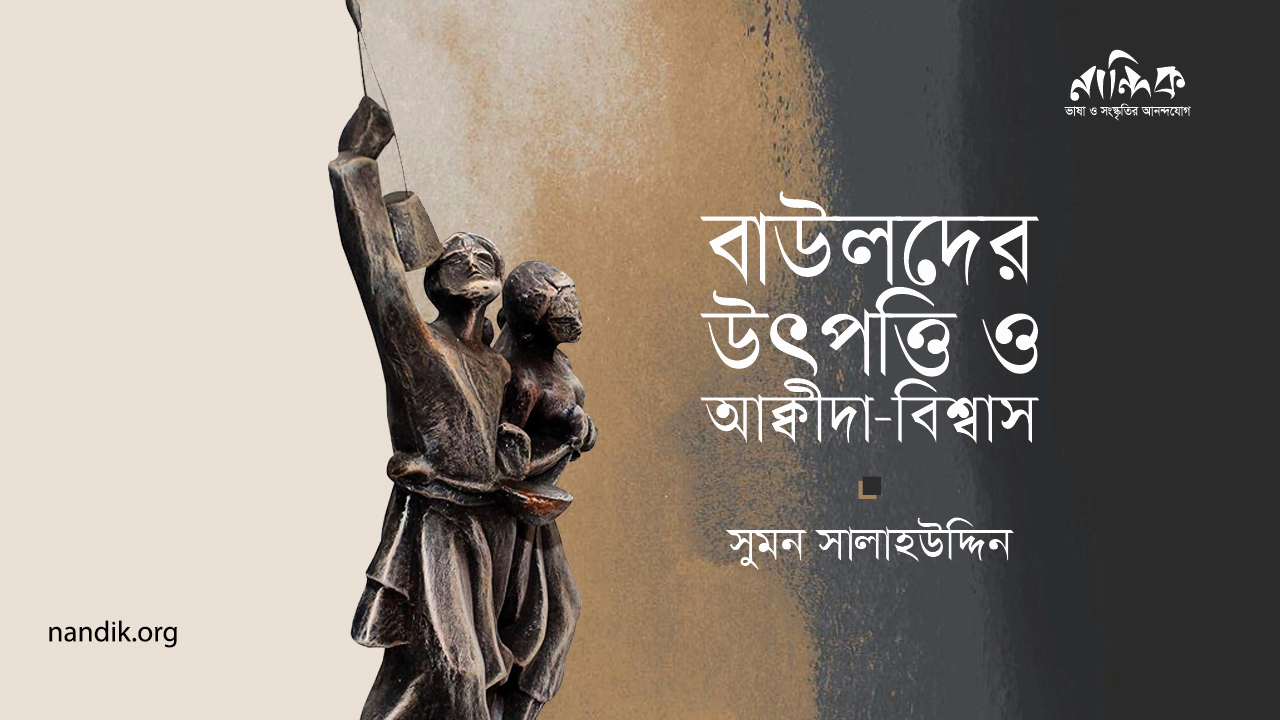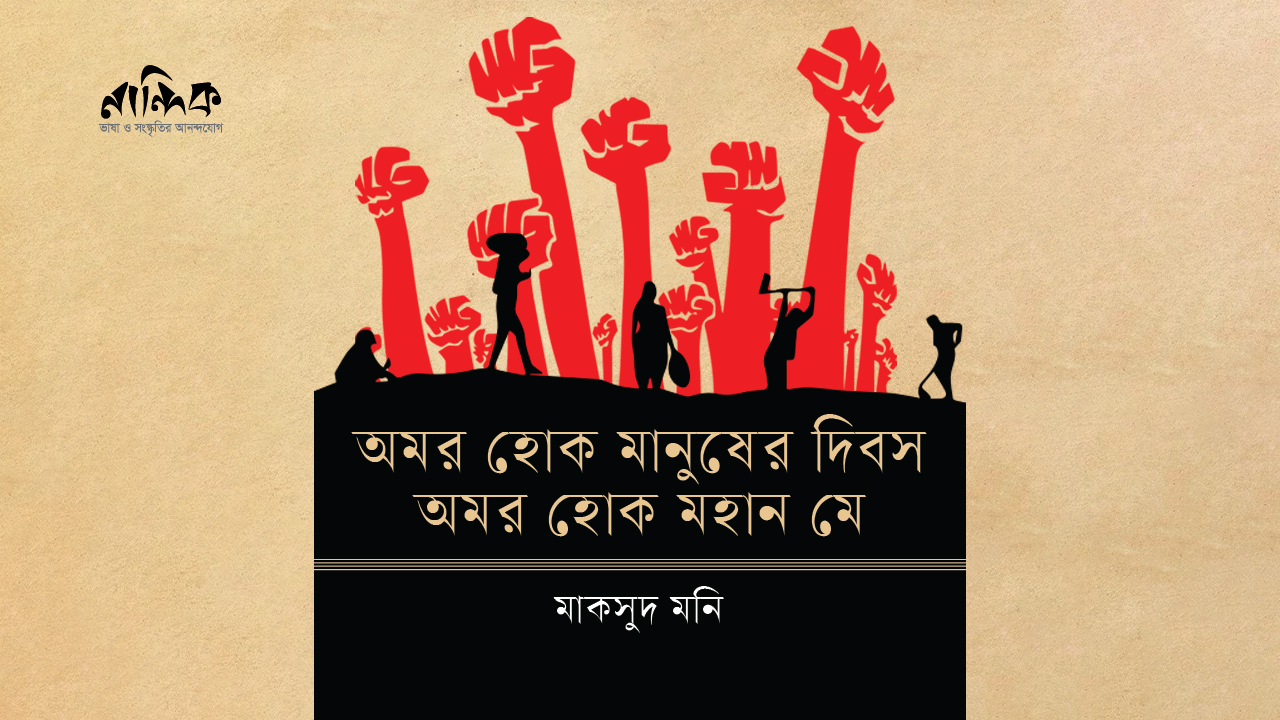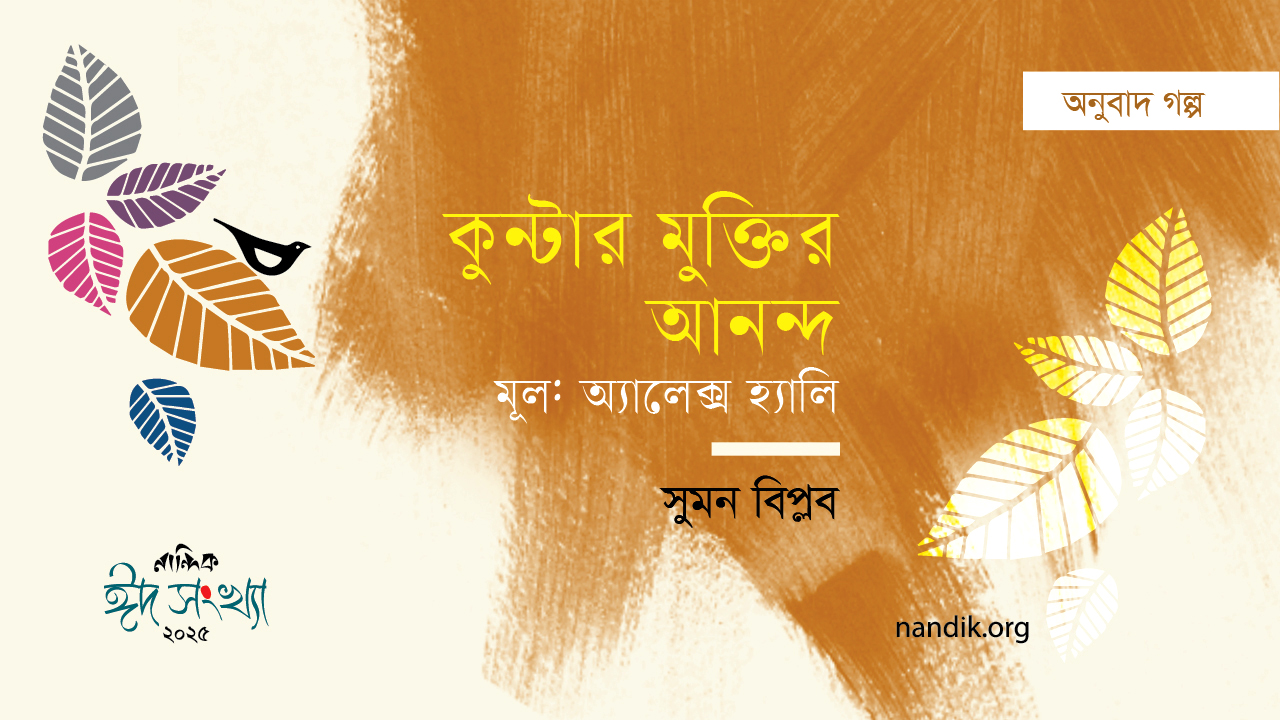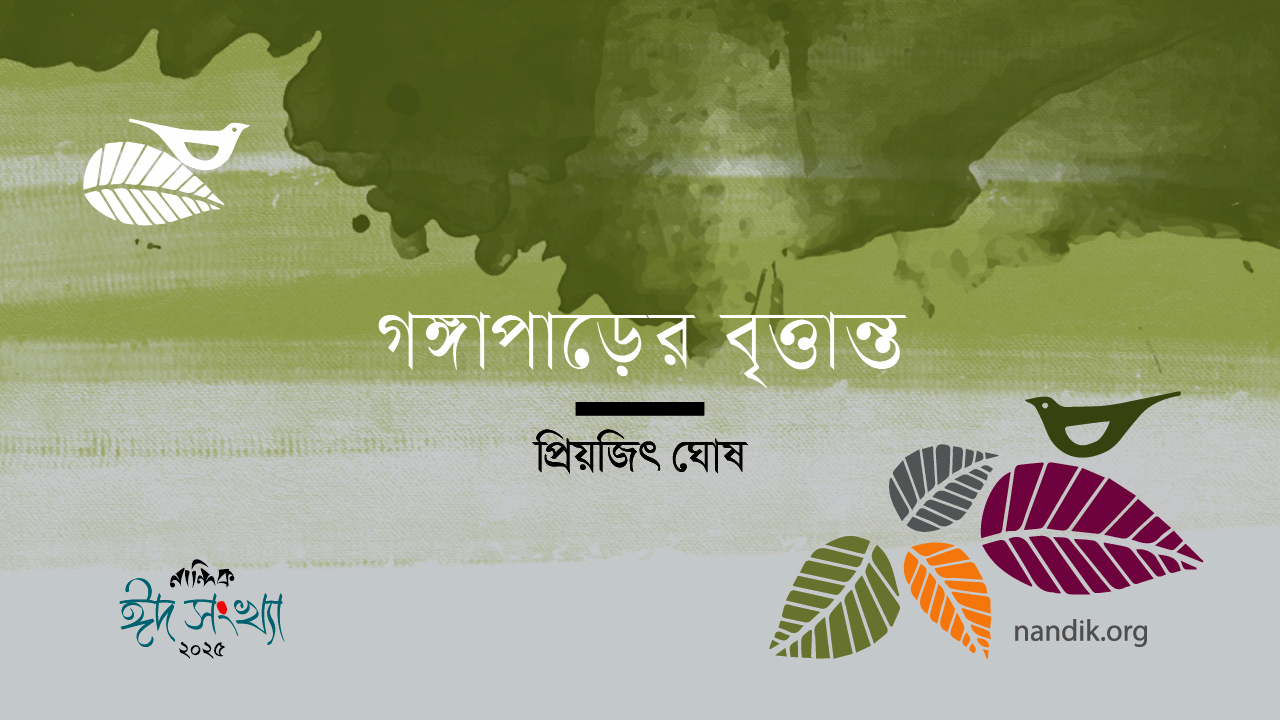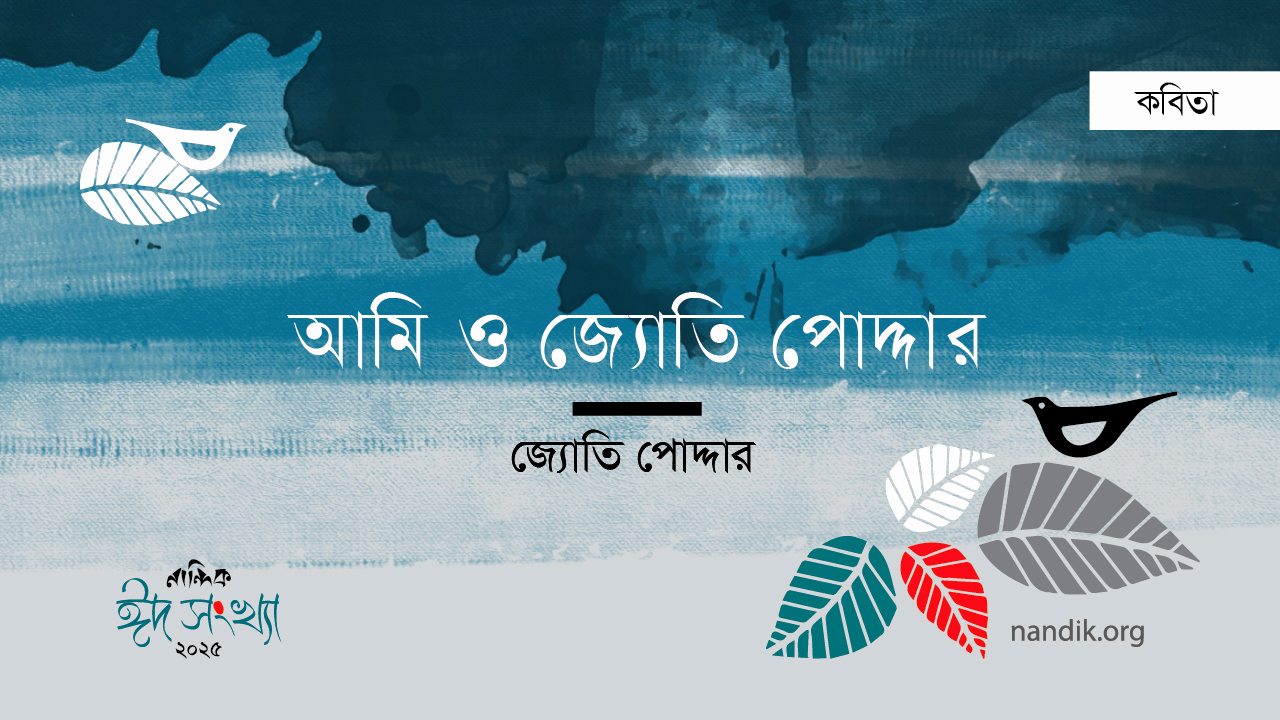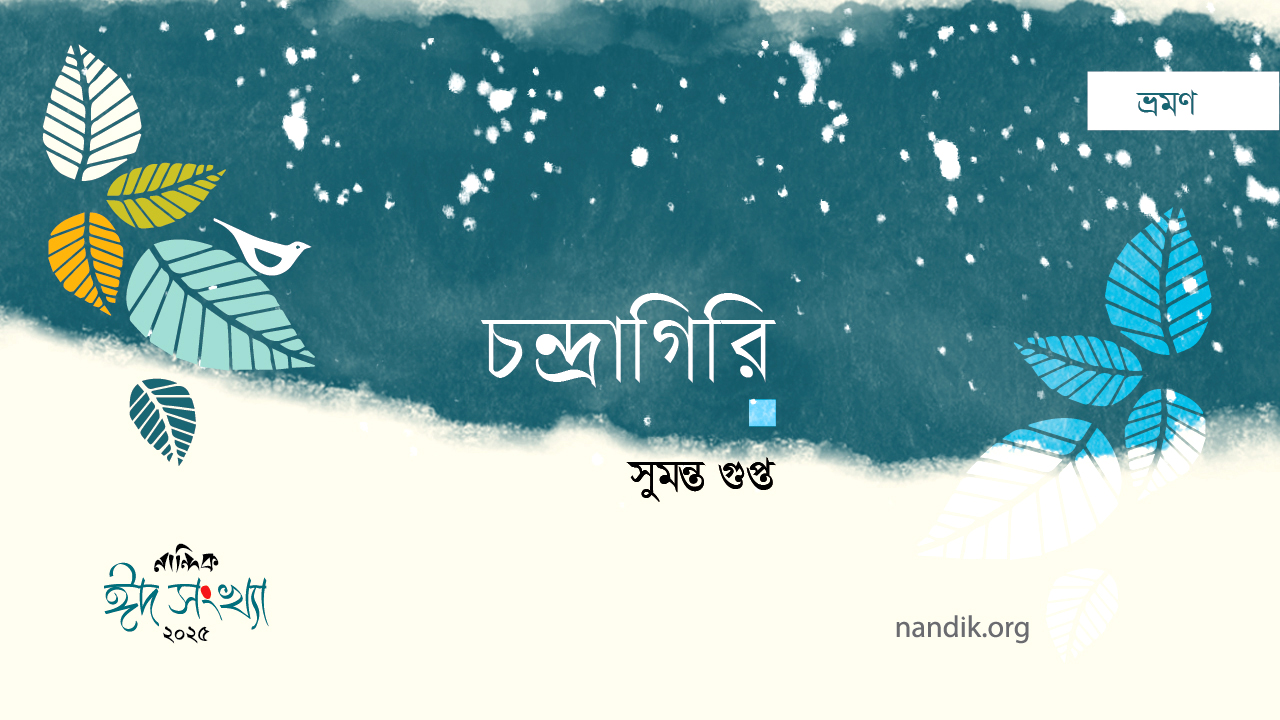ভারতবর্ষে আর্যদের ইতিহাস ও জীবন যাপন
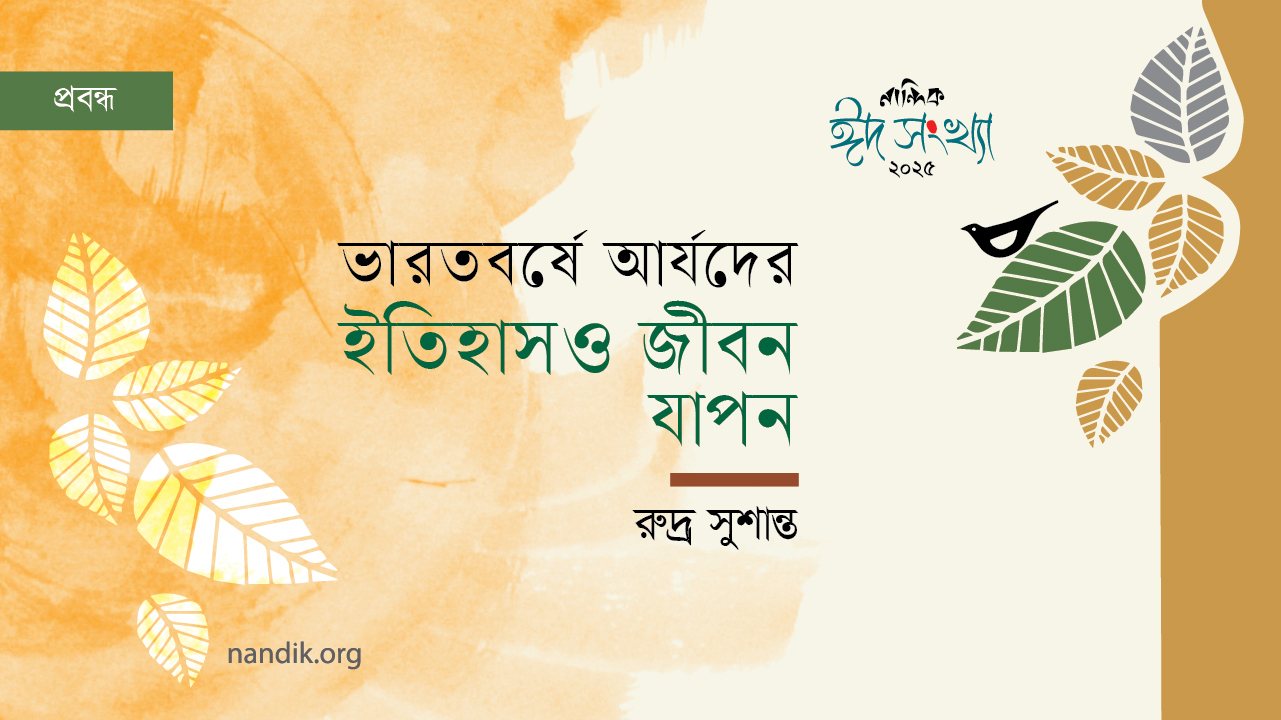
ভারতবর্ষে আর্যদের ইতিহাস ও জীবন যাপন
রুদ্র সুশান্ত
আর্য সম্প্রদায় ভারতবর্ষে ঠিক কোন সময় থেকে বসবাস শুরু করেন সে নিয়ে তুমুল বিতর্ক আছে ঐতিহাসিকগণদের মাঝে। সিন্ধু সভ্যতার পতনের পর ভারতবর্ষে ধীরে ধীরে একটি জাতি প্রকাশ পায়, তারা ‘আর্য’ জাতি নামে পরিচিত। মূলত যখন সিন্ধু সভ্যতার পতন ঘটে তখন একটি জাতি ভারতবর্ষের বসবাস শুরু করে এবং নিজেরা আলাদা সংস্কৃতি ধারণ করে তারা নিজেদের আর্য নামে পরিচিত দিত। আর্য শব্দের অর্থ হলো বিশ্বস্ত মানুষ বা একই জাতির মানুষ। আর্যরা দলবদ্ধ হয়ে গুষ্টিবদ্ধ হয়ে বসবাস করত। “সংস্কৃতিতে এই শব্দটি আর্য (Arya) ,প্রাচীন পার্সীয়দের ধর্মগ্রন্থ ‘আবেস্তায়’ আইর্য(Ariya), আর প্রাচীন পার্থিব সাধারণ ভাষায় আরীয় (Ariya) বলা হতো ।(১) সিন্ধু সভ্যতার পতনের পর আর্য সম্প্রদায়ের লোকদের আলাদা করে বর্ণনা করা হলেও আর্যরা মূলত ভারতবর্ষের আদি সন্তান। আর্যদের আদি বাসস্থান হল ভারতবর্ষ । ইতিহাসবিদ শ্রী নীলকন্ঠ শাস্ত্রী আর্যদের আদি বাসস্থান নির্ণয় করার জন্য ঋগ্বেদের আশ্রয় নেন। ঋগ্বেদ যেহেতু ভারতবর্ষের আদিতম গ্রন্থ সেহেতু শ্রী নীলকন্ঠ শাস্ত্রী মনে করেন ঋগ্বেবেদের ভৌগলিক অবস্থান সম্পর্কে নিশ্চিত হতে পারলে বা ঋগ্বেবেদের বর্ণনা অনুযায়ী ভৌগোলিক অবস্থান নির্ণয় বা নির্দিষ্ট করা গেলে আর্যদের প্রকৃত বাসস্থান এবং তাদের আদিবাসী সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট ও সুসম্পন্ন ধারণা পাওয়া যায়। তিনি ঋকবেদের ভৌগোলিক বর্ণনা বিবেচনা করে সিদ্ধান্তে আসেন যে পঞ্চনদীর আশেপাশে আর্যদের বসবাস ছিল। অনেক গবেষকরা মতামত দিয়েছেন আর্যরা যথেষ্ট পরিশ্রমী, সংগঠিত, উদ্যমী এবং নিষ্ঠাপরায়ণ লোক ছিল। নৃতাত্ত্বিক দিক দিয়ে এরা গৌড় বর্ণের। আর্যরা ভারতবর্ষের আদি সন্তান । তারা অন্য অঞ্চল থেকে এখানে আসেননি বরং ভারতবর্ষ থেকে এরা পারস্য ও ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ে । আরেকটি যুক্তি আছে যে- “আর্যরা ভারতবর্ষের আদি সন্তান” সেটা হলো যদি তারা ভারতবর্ষের বাইরে কোন অঞ্চল থেকে আসতো তাহলে পরবর্তীতে কোন না কোন সময় পূর্ব-পুরুষের বসতির দিকে ফিরে যেতে চাইতো কিন্তু আর্যরা কখনোই ভারতবর্ষ ছেড়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়নি। এবং আর্য সম্প্রদায় ধীরে ধীরে পুরো ভারতবর্ষ জুড়ে তাদের বসতি গড়ে তোলে। প্রথমের দিকে আর্যরা বসতি গড়ে তোলে পূর্ব পাঞ্জাবে, শতদ্রু ও যমুনা নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চলে। পরে বিপাশা, ইরাবতী, চন্দ্রভাগা, ঝিলান, সিন্দু ও সরস্বতী নদীর আশেপাশে বসবাস করেন। আরো পরে তারা উত্তর ভারতে ছড়িয়ে পড়েন, এরপরে আর্য সম্প্রদায়ের লোক পুরো ভারতবর্ষে বসতি গড়ে তোলে। ধীরে ধীরে ইতিহাসে এই অঞ্চল ‘আর্যবর্ত’ নামে পরিচিত লাভ করে। আর্য সম্প্রদায়ের লোকজন ভারতবর্ষে অনার্য সম্প্রদায়ের সাথে দূরত্ব বজায় রেখে বসবাস করত, পরবর্তীতে অবশ্য আর্য এবং অনার্যদের মাঝে সম্পর্ক গড়ে উঠে, তারা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয় পরস্পরের সাথে।
(যেহেতু বলা হচ্ছে যে ঋগ্বেবেদের সময় থেকে আর্যরা ভারতবর্ষে বসতি গড়ে তোলে সেহেতু ঋগ্বেবেদের সময় নির্ণয় করা হয়েছে, ঋগ্বেদ প্রথমে লিখিত রূপে পায়নি। বহুকাল বেদ মানুষের মুখে মুখে প্রচলিত ছিল, সময় নির্ণয় করার জন্য ম্যাক্স মুলার (Max muller, 1823-1909, A.D) সময়কে পেছনের দিকে গণনা পদ্ধতি উদ্ভাবন করেন, এই পদ্ধতিকে বলা হয়- Date reckon backward. এই পদ্ধতি ব্যবহার করে ম্যাক্স মুলার মতামত দিয়েছেন যে ঋগ্বেবেদের গঠনকাল ১৪০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ। কিন্তু পরবর্তীতে তুরস্কের বোঘাজকুই (Boghajkoy) অঞ্চলে একটি শিলালিপি পাওয়া যায় এই শিলালিপিটি ছিল দুই হাজার সন্ধি চুক্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল ১৪০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে। চুক্তির সাক্ষী হিসেবে চারজন দেবতার নাম লেখা হয়েছে। এদের মধ্যে দুজন হলেন ইন্দ্র ও বরুণ। ঋগ্বেদ থেকে জানা যায় ইন্দ্র ও বরুণ বৈদিক আর্যদের দেবতা। এর থেকে জানা যায় আর্যদের বসবাস আরো শতাধিক বছর পূর্বে,(১)। তারমানে এরও পূর্বে বেদ প্রচলিত ছিল। গবেষকগণ গবেষণা করে বেদ উদ্ভাবনের নির্দিষ্ট সময় পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে নির্ণয় করতে পারেননি)।
আর্যদের ধর্ম ও ধর্মীয় জীবন:-
আর্যদের প্রধান ধর্মীয় গ্রন্থ বেদ বেদে মূলত প্রকৃতি এবং স্রষ্টার বন্দনা করা হয়েছে। ধর্মগ্রন্থ বেদ মানুষের জন্য চির ও শাশ্বত কল্যাণময় বাণী বলা আছে- “বেদোহখিলো ধর্মমূলম” অর্থাৎ- বেদ হল সমস্ত ধর্মের মূল । আবার বলা হয়- “সর্বজ্ঞানময়ো হি সঃ” অর্থাৎ- সর্বময়ত্ব বেদের দেবত্ব। বেদ কোন মানুষের দ্বারা রচিত নয় । বেদ ও অপৌরষেয় এবং নিত্য। ধর্মগ্রন্থ বেদে অনেক দেবতার কথা উল্লেখ আছে- অগ্নি, ইন্দ্র, সোম, বরুণ, বায়ু, সূর্য, রুদ্র, পৃথিবী, পর্জন্য…। পবিত্র ধর্মগ্রন্থ বেদে শক্তিকেই দেবতা বা দেবত্ব রূপে বর্ণনা করে পূজা করা হয়েছে। আর্যদের প্রধান ধর্মগ্রন্থ বেত চার খন্ডে বিভক্ত।
১. ঋগ্বেদ (সর্বমোট মন্ত্র সংখ্যা-১০,৫৫২টি)
২. সামবেদ (সর্বমোট মন্ত্র সংখ্যা-১,৮৭৫টি)
৩. যজুর্বেদ (সর্বমোট মন্ত্র সংখ্যা-১,৯৭৫টি) এবং
৪. অথর্ববেদ (সর্বমোট মন্ত্র সংখ্যা-৫,৯৭৭টি)।
চারখন্ডে বিভক্ত বেদে সর্বমোট মন্ত্র সংখ্যা- ২০৩৭৯। (উইকিপিডিয়া)
প্রত্যেকটি বেদ আবার চারটি খন্ডে বিভক্ত-
(ক) সংহিতা- সংহিতায় মন্ত্র, স্তোত্র, স্তব, স্তুতি প্রার্থনা এবং আশীর্বচনের সংকলন।
(খ) ব্রাহ্মণ- মন্ত্রের আলোচনা যজ্ঞে মন্ত্রের ব্যবহার যজ্ঞের বিবরণ এবং বিধান দেওয়া আছে।
(গ) আরণ্যক- আরণ্যকে ধর্মীয় আচার ব্যবহার, উপাসনার বর্ণনা রয়েছে।
(ঘ) উপনিষদ- উপনিষদকে বর্তমানে মূলত বেদান্তরূপে বর্ণনা করা হয়। বেদের সারসংক্ষে স্বরূপ বিবেচনা করা হয় বেদান্তকে। ধ্যান পদ্ধতি, ধ্যান, দর্শন এবং আধ্যাত্মিক আলোচনা রয়েছে উপনিষদে।
আর্য সম্প্রদায়ের ধর্মবিশ্বাসে প্রকৃতির ব্যাপক গুরুত্ব ছিল। প্রত্যেক দেবতাকে ভক্তি সহকারে পূজা করা হতো । প্রত্যেক পূজায় অগ্নি দেবতার উপাসনা করা হতো। ধর্মীয় অনুষ্ঠানে দেবতাদের উদ্দেশ্যে বলিদান এর প্রতাপ প্রচলিত ছিল ঋগ্বেবেদের যুগেও। আর্য সম্প্রদায়ের ধর্মভাব ছিল সহজ-সরল ও প্রাকৃতিক। প্রকৃতির ফুল দিয়ে দেবতাদের পূজা করা হতো, প্রকৃতির ফল দিয়ে দেবতাদের নৈবেদ্য দেওয়া হতো। দেবতাদের কাছে সন্তান লাভ, গোধন লাভ, সুস্থতা লাভ এইসবের জন্য প্রার্থনা করা হতো। কখনো কখনো যুদ্ধে জয়লাভ করার জন্য দেবতাদের কাছে প্রার্থনা করা হতো। আর্যদের ধর্মীয় জীবনে ধ্যান দর্শনের চর্চা করা হতো কঠোরভাবে। ঋগ্বেবেদ পরবর্তী সময়ে আর্য সম্প্রদায়ের লোকদের মধ্যে চারটি প্রথা বা আশ্রমের উল্লেখ পাওয়া যায়।
(ক) ব্রহ্মচর্য- ব্রহ্মচর্য হলো গুরুগৃহে গিয়ে শিক্ষা লাভ করা, জীবনের প্রারম্ভিক্ষ কালে অর্থাৎ শিশুকালে ছেলে-মেয়ে উভয়ই গুরুগৃহে গিয়ে ধর্মীয় জীবন এবং নানান বিষয়ে শিক্ষা লাভ করে।
(খ) গাইস্থ্য- সংসার জীবন, বিবাহ, সন্তান লাভ, পিতা-মাতার প্রতি দায়িত্ব পালন ইত্যাদি।
(গ) সাত্ত্বিক জীবন- সংসারের মায়া ত্যাগ করে দূরে কোথাও বসবাস করা, এই সময় মূলত ঈশ্বর সাধনাকে প্রাধান্য দেওয়া হয়।
(ঘ) সন্ন্যাস- চতুরাশ্রম বা চারটি প্রথার মধ্যে সবচেয়ে কঠিন এবং কঠোর প্রথা হলো “সন্ন্যাস”। বয়সের শেষে এসে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করার জন্য এবং জীবনের মোক্ষলাভের জন্য সন্ন্যাস ধর্ম নিয়ে গহীন বনে সাধনার উদ্দেশ্যে গৃহ ত্যাগ করা। সন্ন্যাস গ্রহণ করার পরে লোকালয় থেকে অনেক দূরে নির্জনে কোন মন্দিরে বা বড় বৃক্ষের নিচে সাধনায় রত থাকা।
সামাজিক জীবন:-
ভারতবর্ষে আর্য সম্প্রদায় যখন বসবাস শুরু করেন তখন তারা অনার্যদের সাথে সহজে মিশে যেত না। তখন পরিবার গড়ে ওঠে। বৈদিক যুগে সমাজ বা রাষ্ট্রের চিন্তা গড়ে ওঠার পূর্বেই পরিবার গড়ে ওঠে। পিতৃতান্ত্রিক পরিবার নিয়ে গড়ে উঠে গ্রাম। আর্য সম্প্রদায় পরিবারকে তখন বর্ণপ্রথা বা বর্ণভেদ ছিলো না। তবে যারা যজ্ঞ ইত্যাদি করতেন তাদেরকে অন্যরা সবাই অধিক শ্রদ্ধা করতেন। পুরুষ একটি মাত্র বিয়ে করতো নারীরা পুরুষের সাথে সমান অধিকার ভোগ করতো। পুরুষদের পাশাপাশি নারীরাও বাড়ির বাইরে কাজ করার সমান সুযোগ পেতেন। পরবর্তী সময়ে আর্য সম্প্রদায়ের মানুষের ভিতরে কিছু লোক উচ্চ-নিন্ম বর্ণের প্রথা চালু করে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র। নিজেদের ক্ষমতা টিকিয়ে রাখার জন্য বর্ণপ্রথাকে ধর্মীয় অনুশাসন বলতে থাকে উচ্চবর্ণের লোকেরা।
অর্থনৈতিক জীবন:-
গবাদি পশু পালন ছিল এদের প্রধান পেশা। ঋগ্বেবেদে জমি চাষ সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে। চাষ করা জমিকে বলা হতো “উর্বরা” । আর যেসব জমি চাষ অনুপযোগী অর্থাৎ চাষ করা হতো না সেগুলোকে “অকৃষিবল” নামে বলা হতো । ঋগ্বেবেদের সময়ে লাঙ্গল দিয়ে জমি চাষ করার প্রচলন ছিল এবং ষাঁড় দিয়ে লাঙ্গল টানা হতো। তবে তখন সময়ও বিনিময় প্রথা প্রচলিত ছিল। একজনের প্রয়োজনে অন্যের কাছ থেকে দ্রব্য আদান-প্রদান চালু ছিল। ঋগ্বেবেদের সময়ে জমির মালিকানা ছিল না, বৈদিক পরবর্তী সময়ে একশ্রেণীর লোক জমির মালিকানা ভোগ করে, উৎপাদন না করেও তারা ফসল ভোগ করতো।
রাজনৈতিক অবস্থা:-
ঋগ্বেবেদের সময়ে আর্য সম্প্রদায়ের লোকজন গোষ্ঠীবদ্ধ হয়ে বসবাস করতো। তখন রাষ্ট্রচিন্তা ছিল না। রাষ্ট্র ছিল না, নির্দিষ্ট সীমানা নিয়ে রাষ্ট্র বা গড়ে তোলার চিন্তাভাবনা তখনও আর্য সম্প্রদায়ের কাছে স্পষ্ট হয়নি। দলবদ্ধ হয়ে বসবাস করাটাই ছিল তখন প্রধান। তখন পারিবারিক বন্ধন সুদৃঢ চমৎকার ছিল, এখন যেটাকে যৌথ পরিবার বলা হয় তখন মূলত সেটাই ছিল পারিবারিক বন্ধন। ঋকবেদে দিবদাসের পুত্র সুদাস নামে এক রাজার কথা উল্লেখ পাওয়া যায়। সুদাসের প্রধান পুরোহিত ছিল বিশ্বমিত্র মুনি, পরে রাজা সুদাস বিশ্বমিত্র মুনির স্থানে বশিষ্ট মুনিকে নিয়োগ দেন এতে বিশ্বমিত্র মুনি অপমান বোধ করেন এবং তিনি ক্ষুণ্ন হন। বিশ্বমিত্র মনি রাগ এবং ক্রোধ থেকে অন্য আর্য রাজাদের নিয়ে জোট গঠন করেন। পরবর্তীতে তিনি অন্য আর্য রাজাদের নিয়ে রাজা সুদাসকে আক্রমণ করেন, এতে সুদাস বিজয় লাভ করেন। আর্যদের শাসন ব্যবস্থায় প্রধান ছিলেন রাজা। রাজার ছেলে রাজা হতেন। সকল যুদ্ধ হতো তীর এবং ধনুক দিয়ে। তখনকার সময়ে সেনাপতির পদবী ছিলো- “সেনানী”।
ধাতুর ব্যবহার:-
ঋগ্বেবেদে ধাতু হিসেবে তামা, সোনা, ব্রেঞ্জের কথা উল্লেখ পাওয়া যায় । পরবর্তীতে টিন, সীসা, রুপার কথাও বেদের বিভিন্ন শ্লোকে উল্লেখ করা আছে। তারমানে ঋগ্বেবেদের সময়ও আর্য সম্প্রদায় ধাতু চিহ্নিত করেছিলেন।
বৈদিক পরবর্তী যুগের শেষের দিকে রচিত হয় রামায়ণ ও মহাভারত নামে দুটি মহাকাব্য। আর্যরা বসতির জন্য রাজ্য বিস্তার করে এবং ধীরে ধীরে পুরো ভারতবর্ষে বসতি গড়ে তোলে। আর্য সম্প্রদায়ের লোক প্রাচী ( বারাণসী, বিহার, বাংলা) এবং আরো পরে মালব, সৌরাষ্ট্র, গুজরাট অঞ্চলে বসতি স্থাপন করে। আর্য সম্প্রদায়ের লোক নদীর অববাহিকা অঞ্চল, পাহাড় পর্বত সমতলের দিকে ধীরে ধীরে বসতি স্থাপন করে । এখানে আর্য সংস্কৃতির সাথে স্থানীয় সংস্কৃতির অর্থাৎ অনার্য সংস্কৃতির একটা সংমিশ্রণ ঘটে। বৈদিক পরবর্তী সময়ে আর্য এবং অনার্য সম্প্রদায়ের সম্মিলিত এবং একত্রিতভাবে বসবাসের ফলে নিজেদের ভিতর ধর্ম এবং সংস্কৃতির সুপ্তভাবে সংমিশ্রণ হয়।
তথ্যসূত্র-
১. বিশ্ব সভ্যতা - এ কে এম শাহনাওয়াজ - প্রতীক প্রকাশনা সংস্থা- সূত্রাপুর, ঢাকা, নবম মুদ্রণ- এপ্রিল ২০১৯ ইংরেজি ।
২. উইকিপিডিয়া।
৩. বাংলাপিডিয়া। বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমিতে ফারুক আযমের কবিতা
nandik2026-01-11T20:35:04+00:00January 11, 2026|
Obsessed by Mahbubul Islam
Mahbub Islam2025-11-14T16:55:18+00:00November 14, 2025|
ফটিকছড়ির মফিজ
Fattah Tanvir2025-11-10T17:45:19+00:00November 10, 2025|
জোড়া প্রেম
Yasin Dhawan2025-11-06T16:46:09+00:00November 6, 2025|
শারীরিক সম্পর্ক কোনো দুর্ঘটনা নয়
Sudipto Mahmud2025-11-05T19:33:30+00:00November 5, 2025|