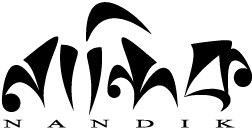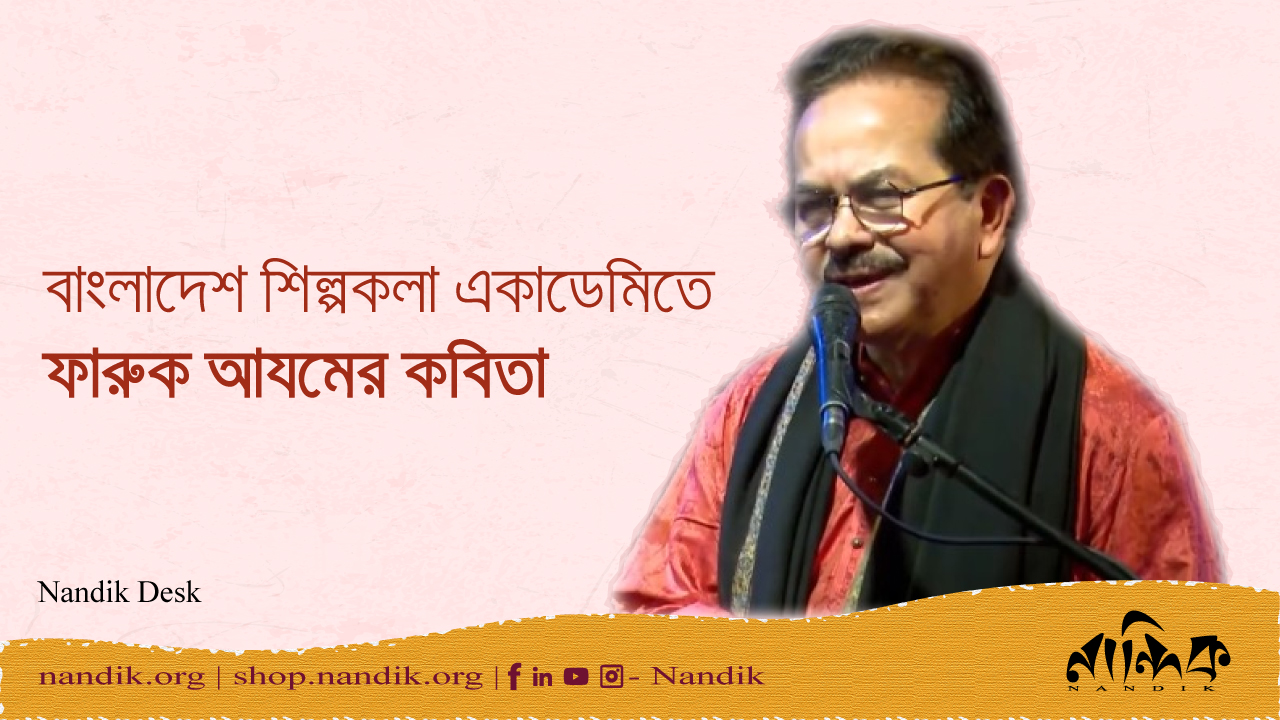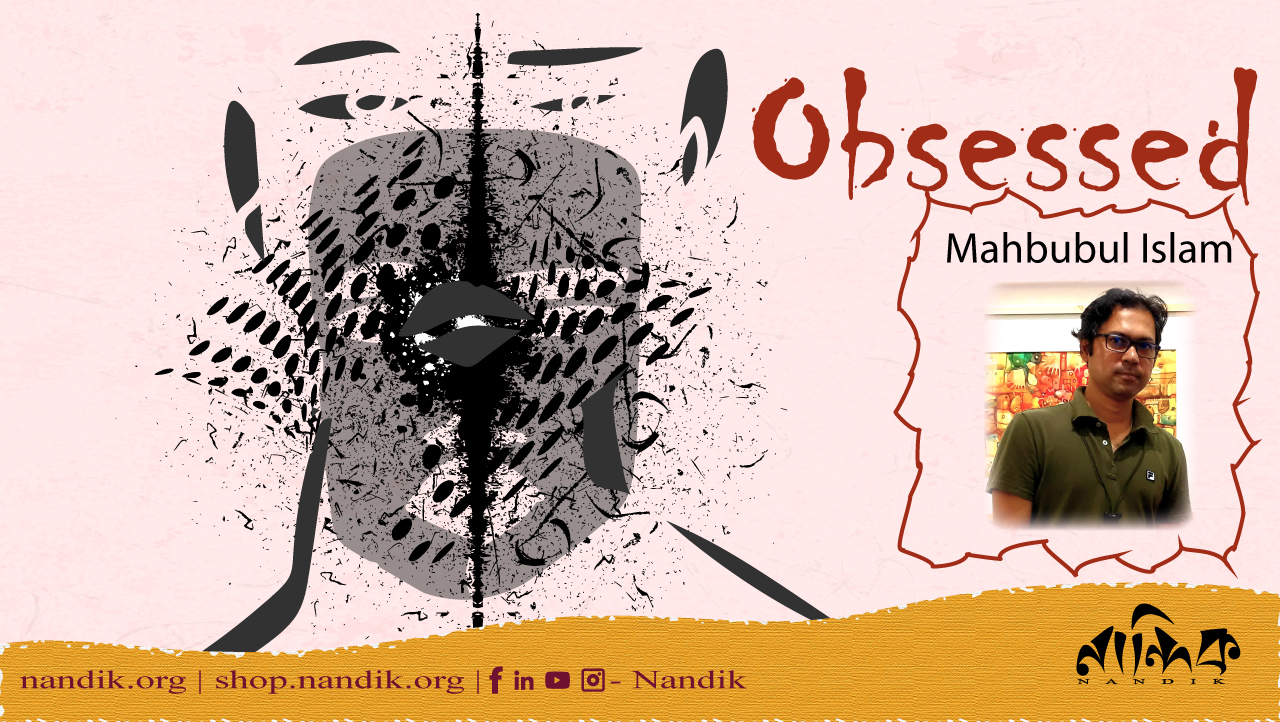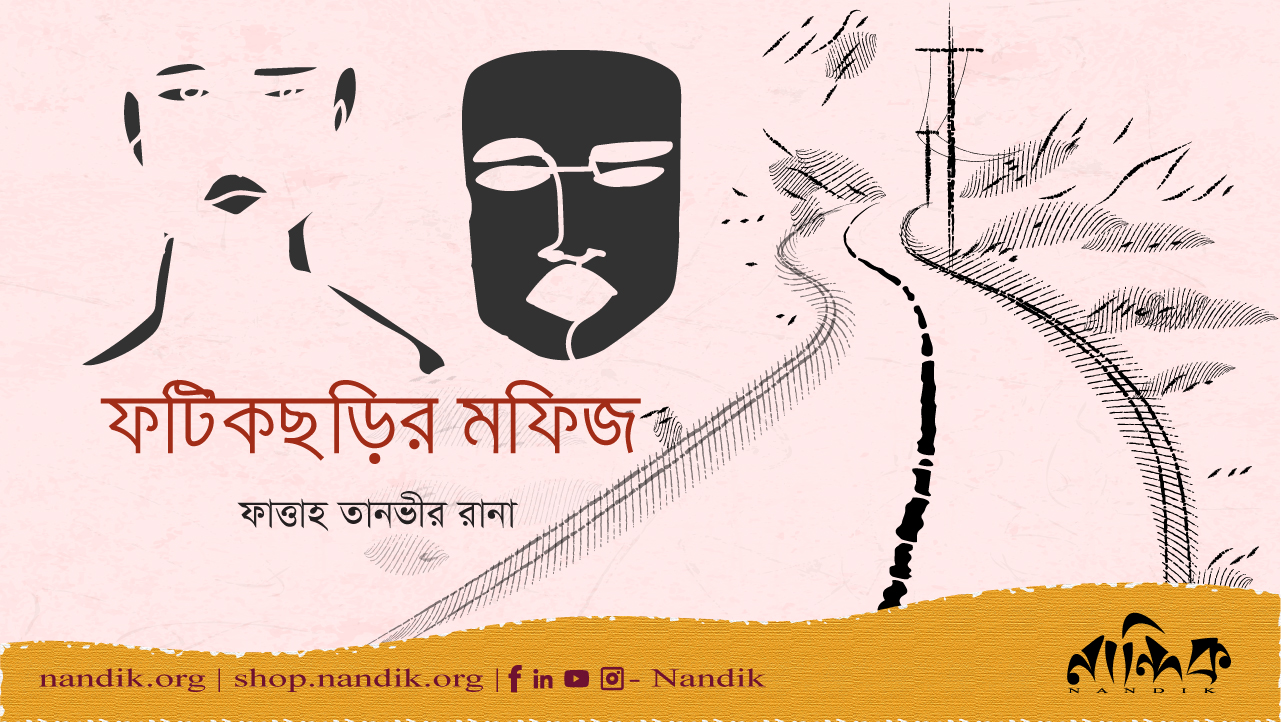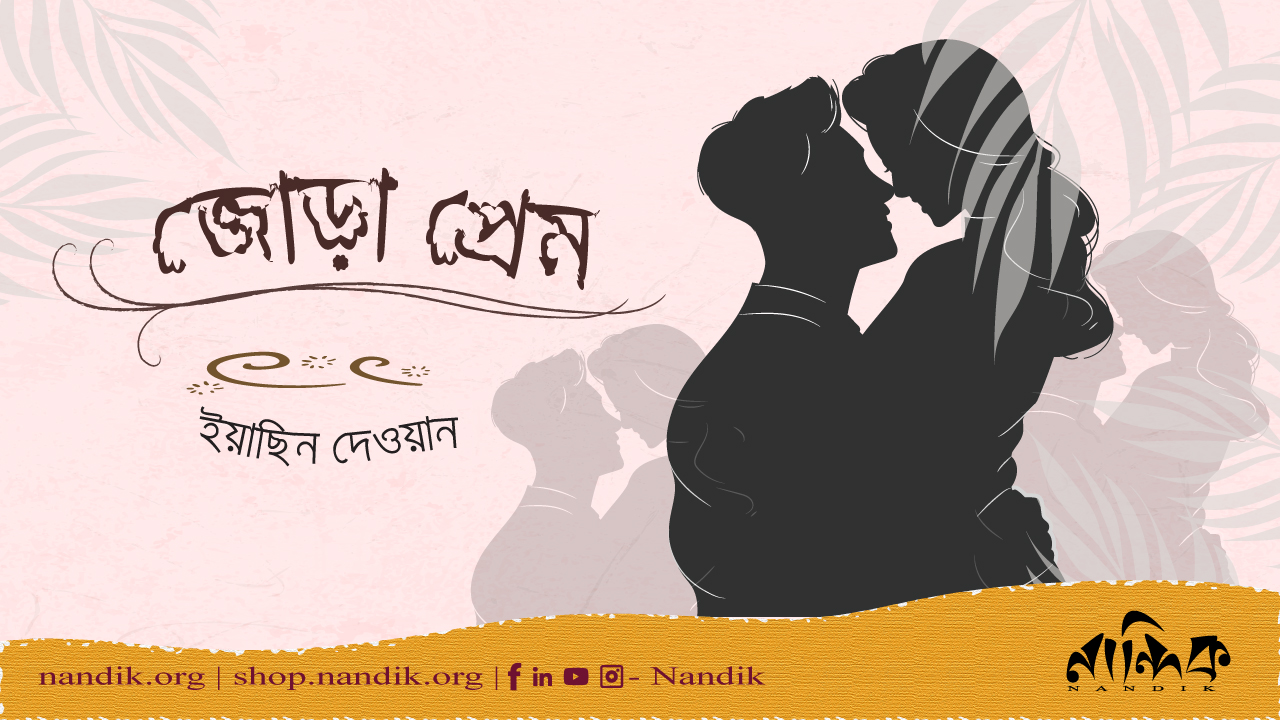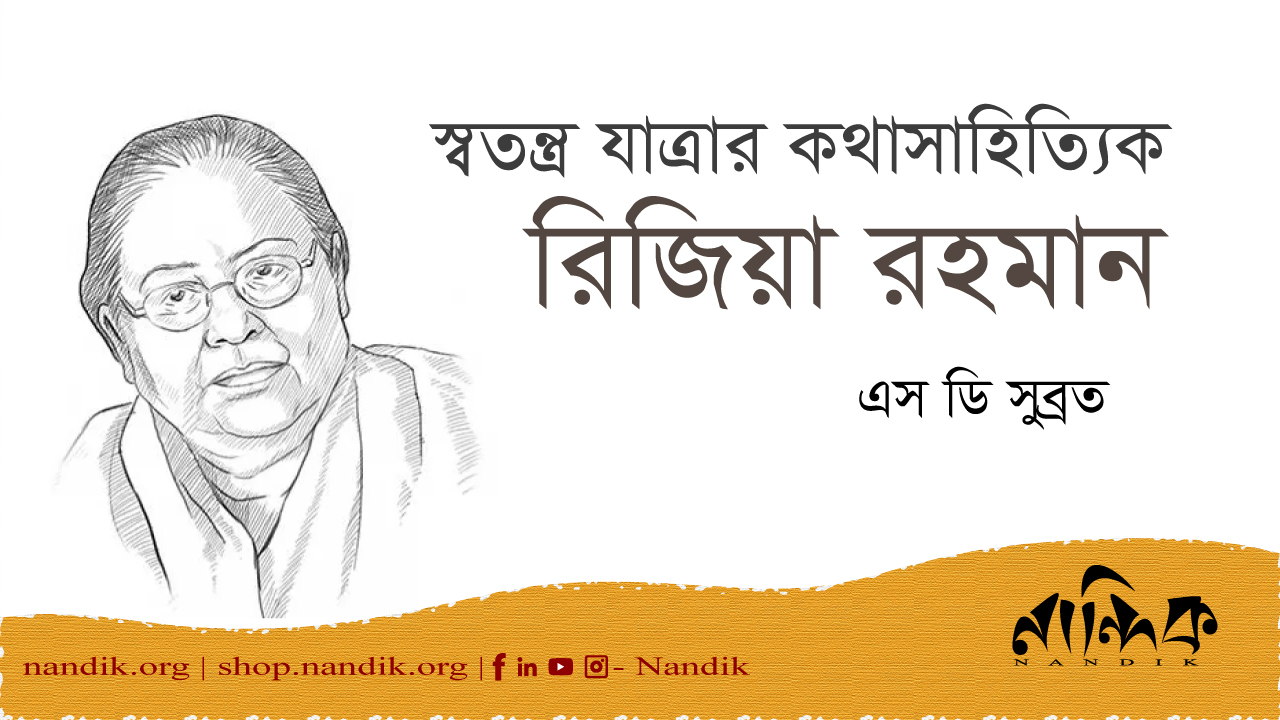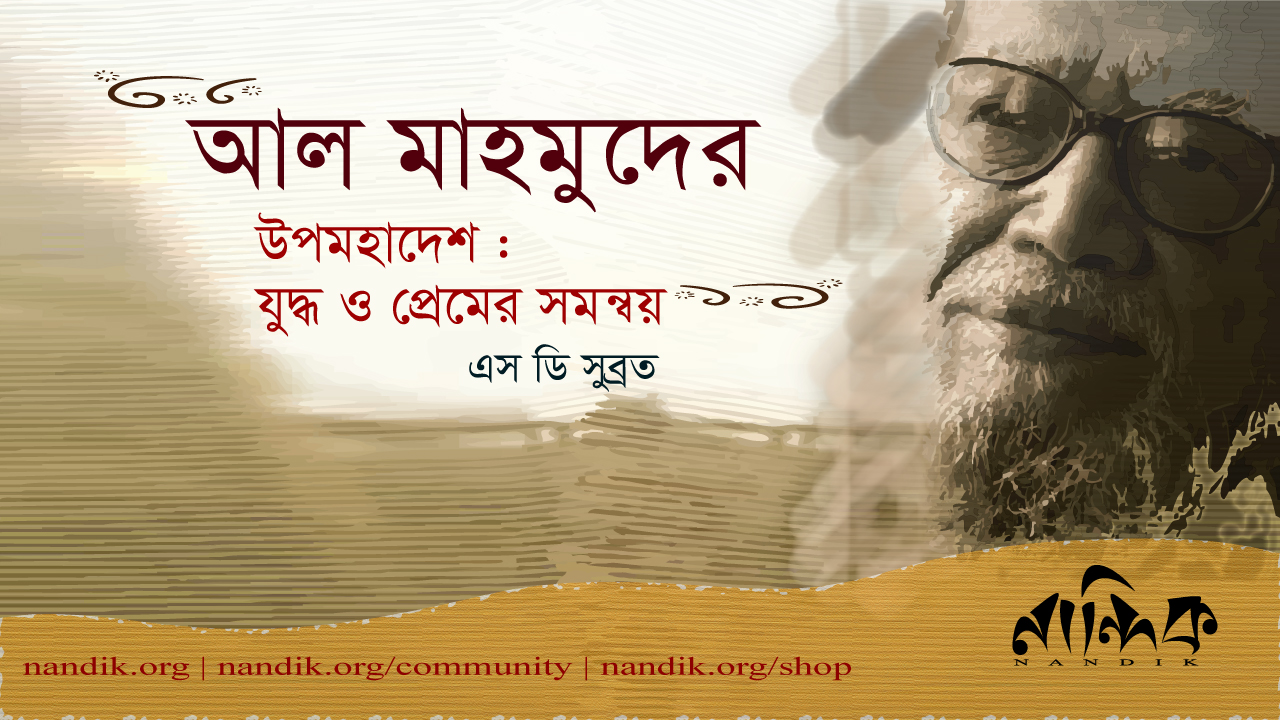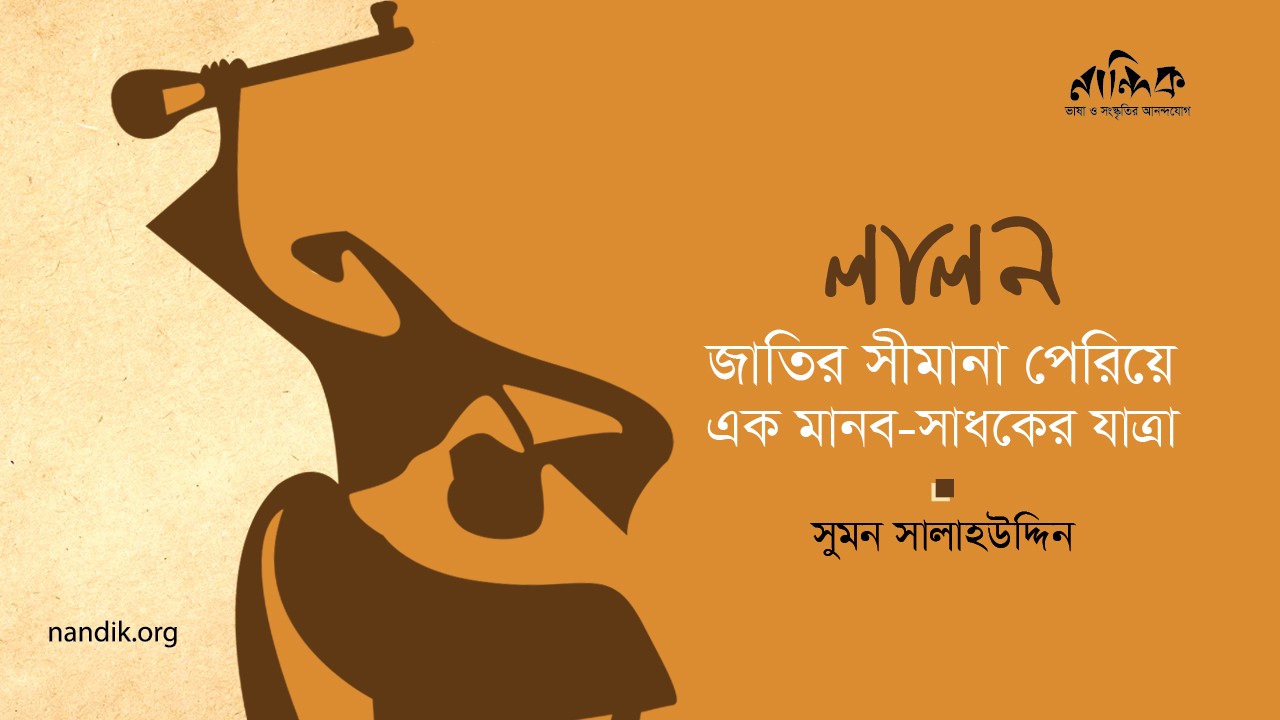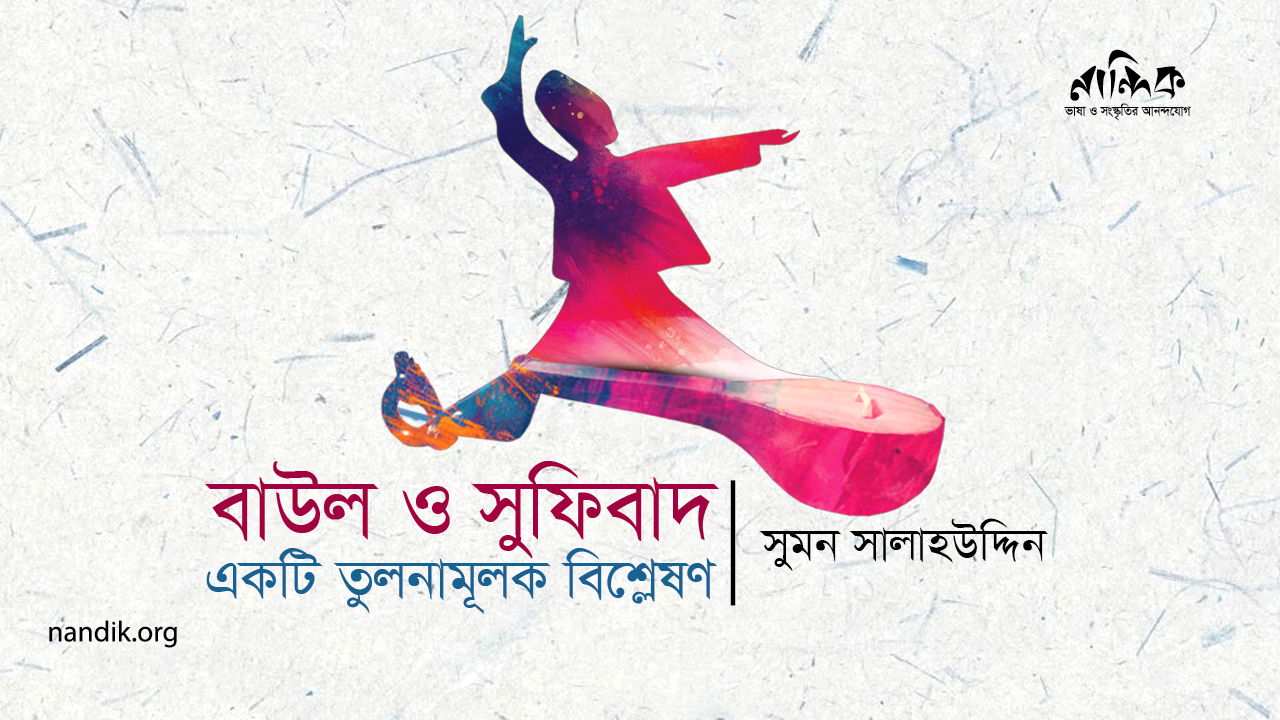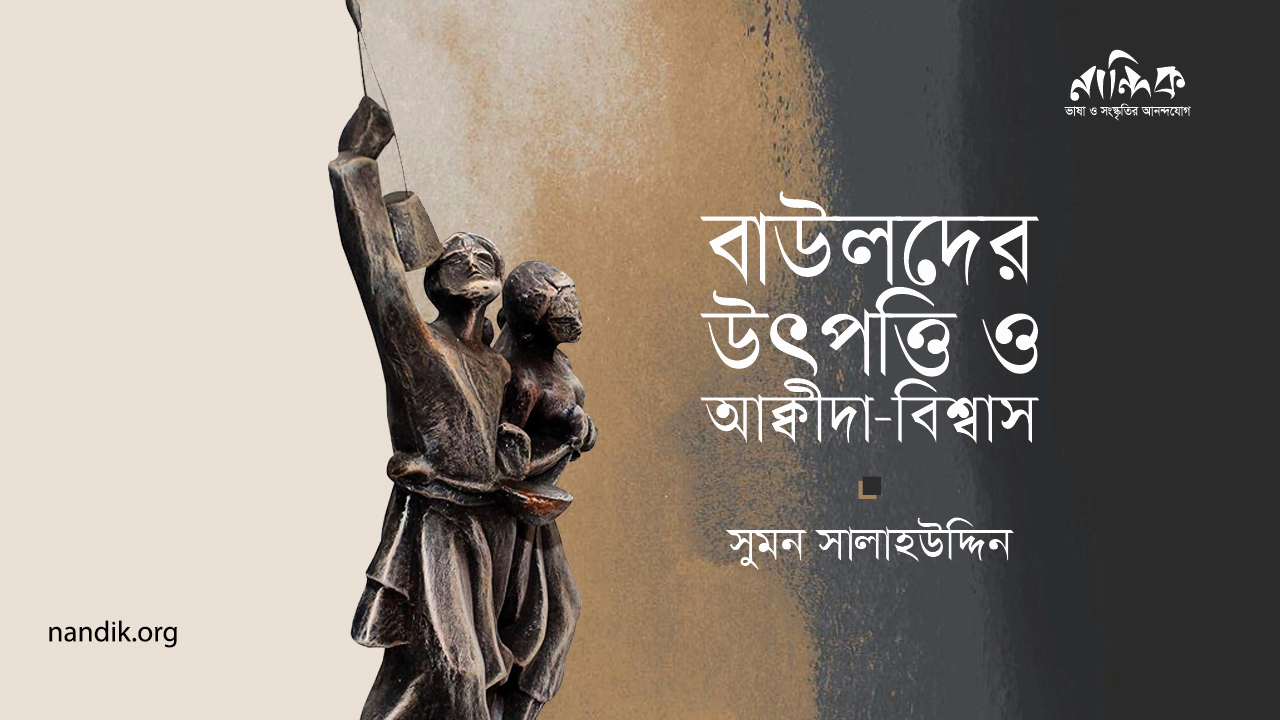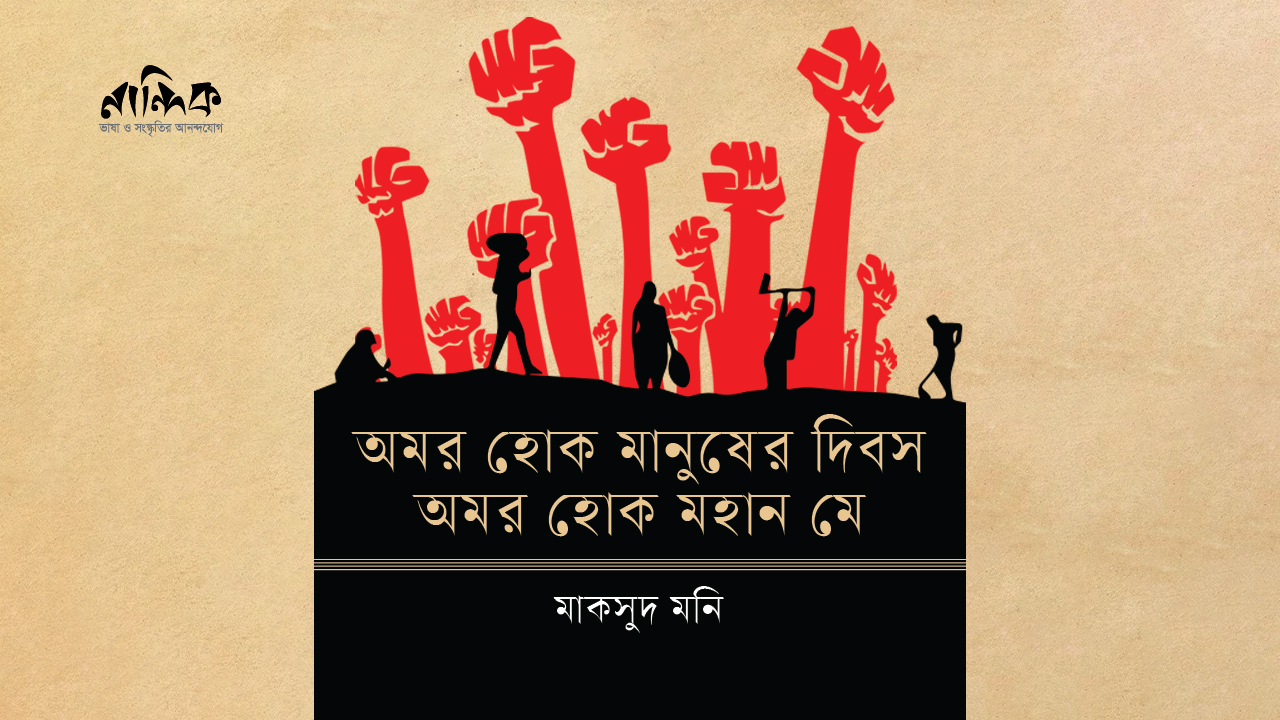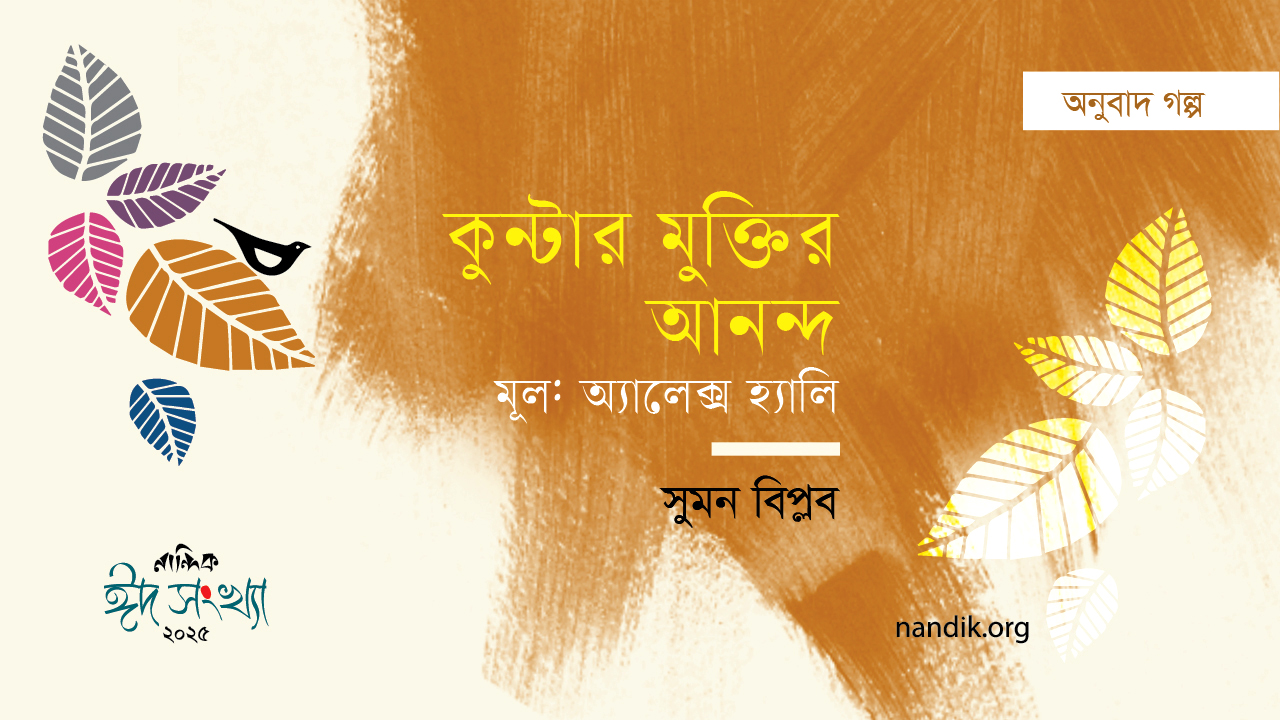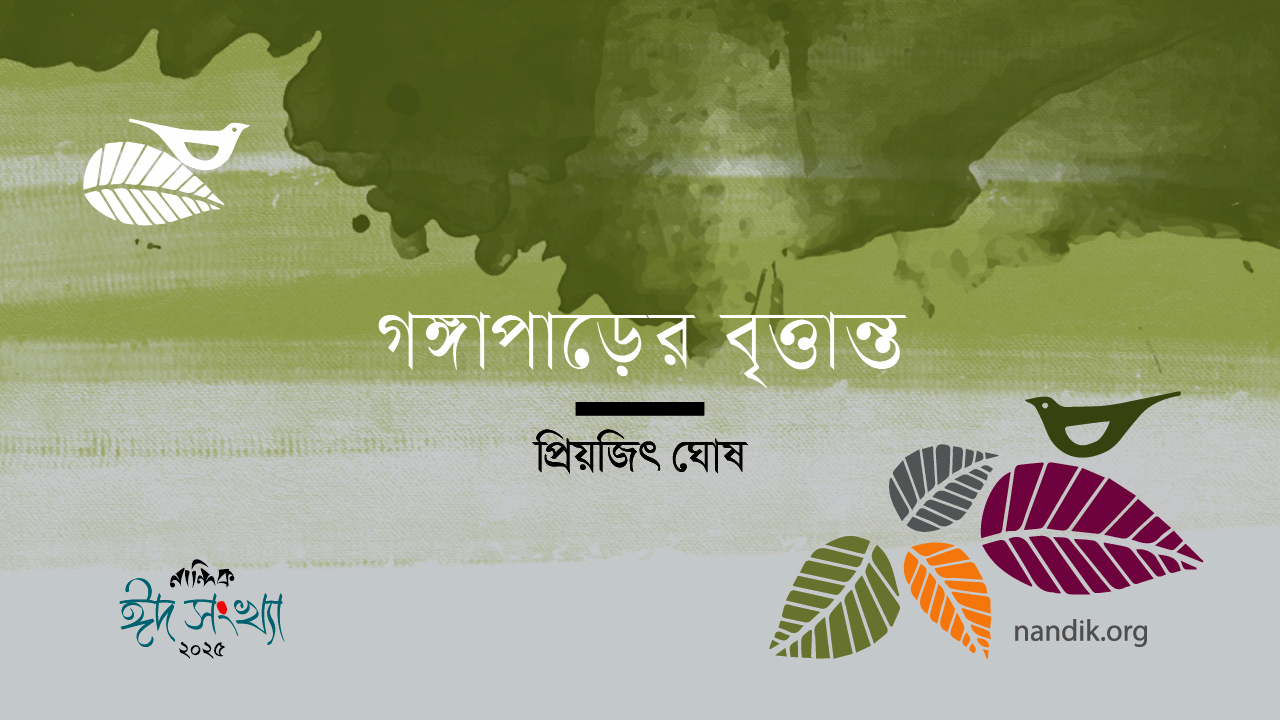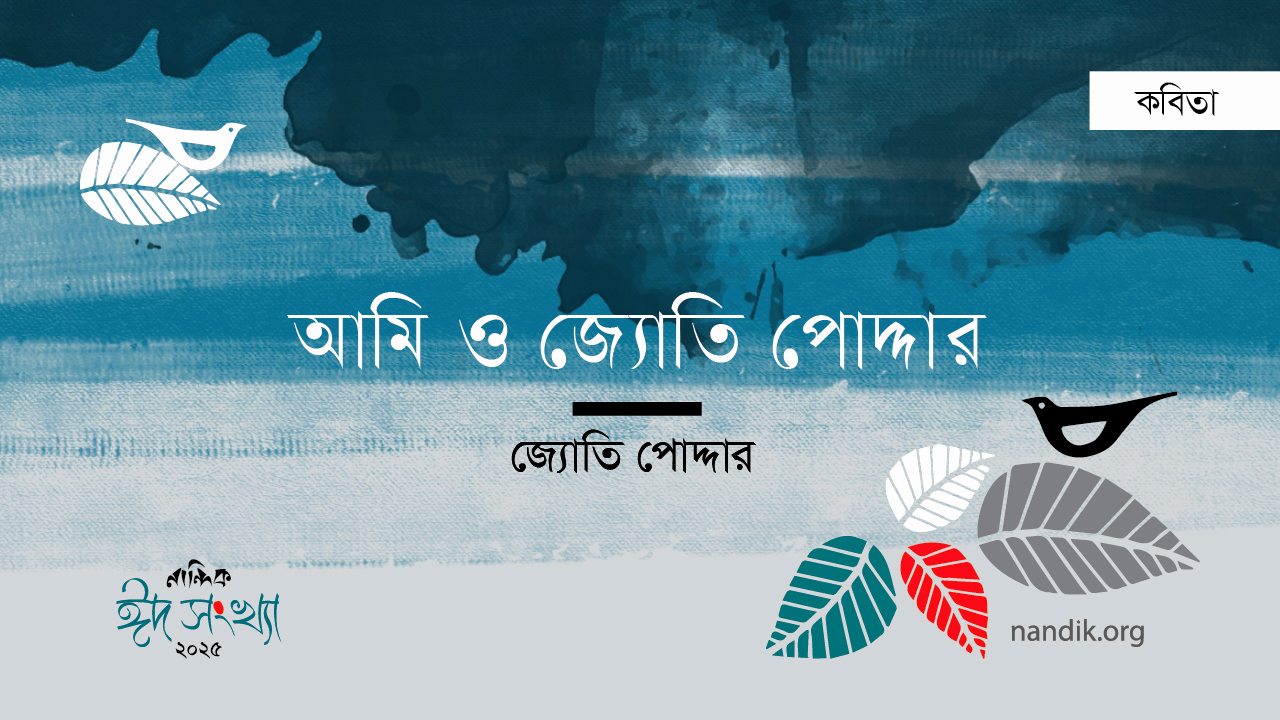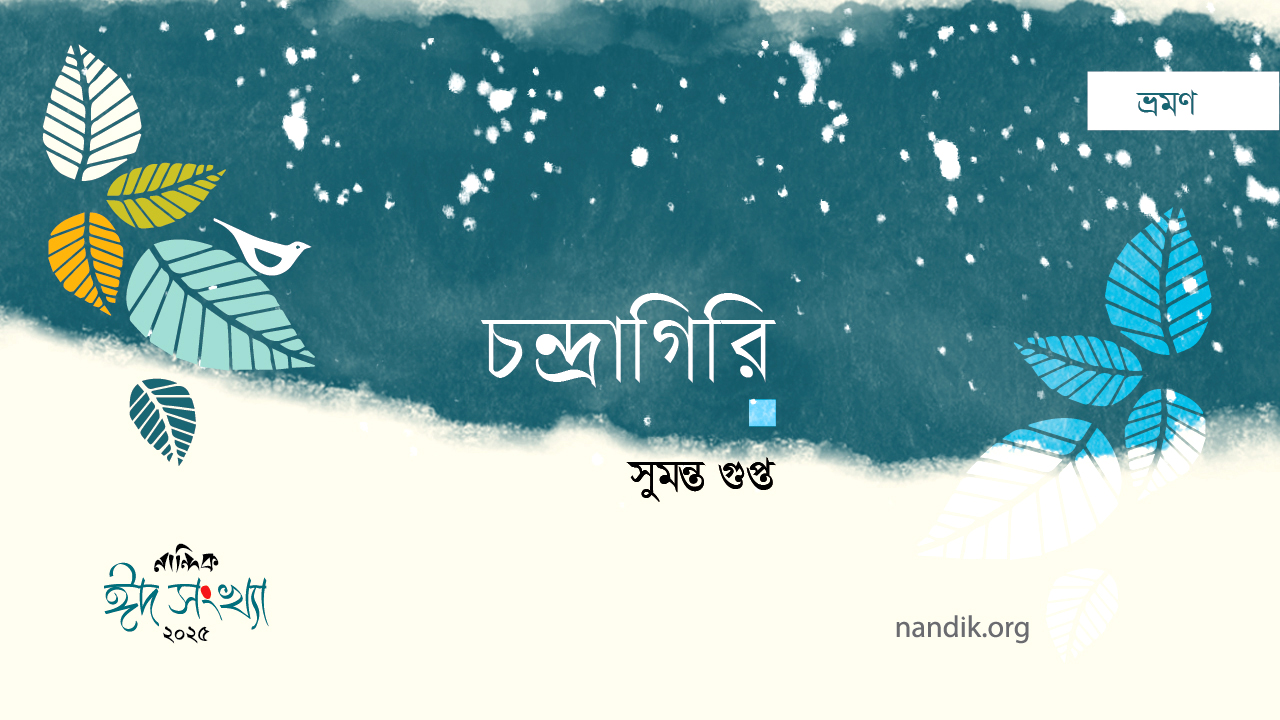সঙ্গ-অনুষঙ্গ মলয়: মেধার বাতানুকূল ঘুঙুর
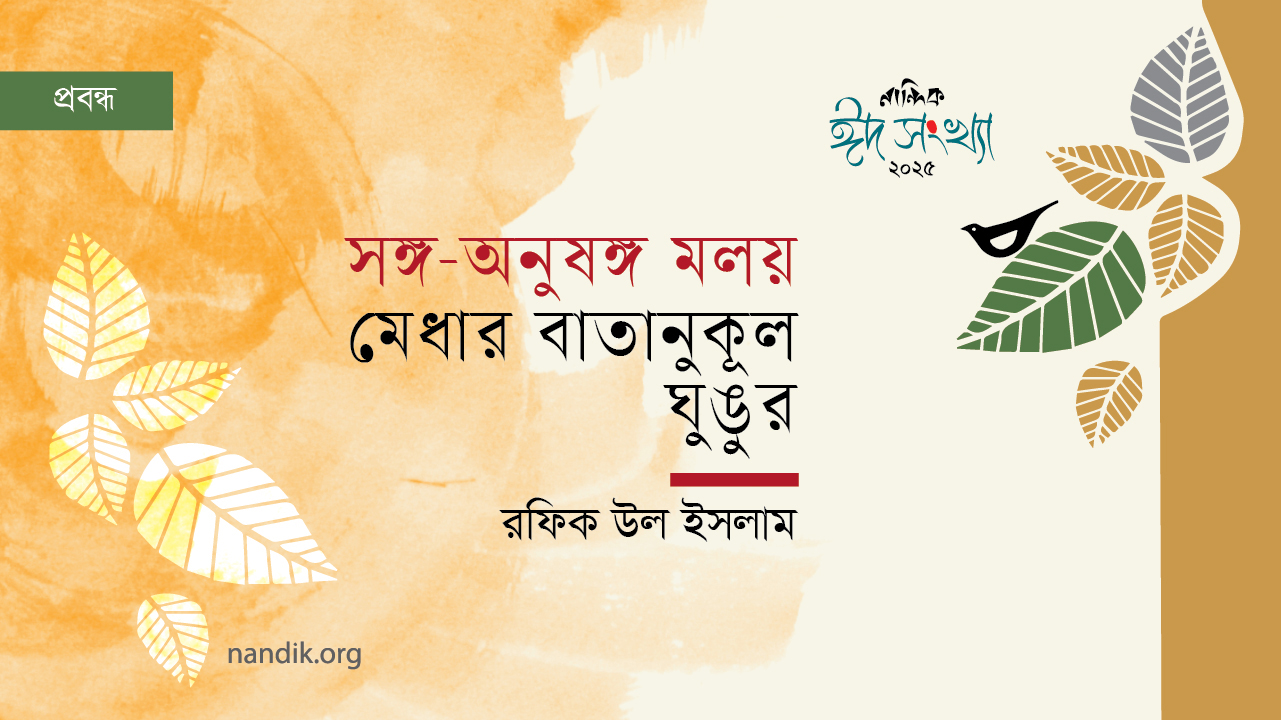
সঙ্গ-অনুষঙ্গ মলয়: মেধার বাতানুকূল ঘুঙুর
রফিক উল ইসলাম
কবি মলয় রায়চৌধুরীর কবিতায় ধ্বনিত হয় ধ্যান আর বারুদের যুগল ব্যঞ্জনা। পড়তে পড়তে অদ্ভুত এক ঘোর তৈরি হয়, যা প্রাত্যহিকতার যাবতীয় অভিজ্ঞতাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেয়। সুখটানের আমেজ কিংবা মদ্যপানের আচ্ছন্নতা নয়, বরং বলা যায় বিষধরের নিক্তি-মাপা ছোবল যেন দুমড়ে-মুচড়ে, উড়িয়ে-গুঁড়িয়ে অন্য এক পৃথিবীতে ছড়িয়ে দিতে চায় পাঠককে। তাঁর কাব্য কালোতীর্ণ হবে কিনা, তা মহাকালই বলবে। কিন্তু এটুকু স্পষ্ট ভাবে উচ্চারণ করা যায়, তিনি বাংলা ভাষার এতকালের কাব্যযাত্রাকে যেভাবে ছিন্নভিন্ন করে নবতর অভিধায়, নতুনতর ডাইমেনশনে স্থাপন করতে চেয়েছেন, সেখানে তিনি নিশ্চিতভাবেই সফল। এবং এই কর্মে তিনি সম্পূর্ণভাবেই একক এবং ব্যতিক্রমী। তাঁর সঙ্গে আমার ব্যক্তিপরিচিতি খুব বেশি গাঢ় ছিল না। কিছু পারিবারিক অনুষ্ঠানে অল্প দেখাসাক্ষাৎ এবং প্রথামাফিক কথাবার্তা। এটুকুই। পরবর্তী সময়কালে তিনি তো বঙ্গ-বিচ্ছিন্ন হয়েই কাটালেন। এই বিচ্ছিন্নতা ছিল শুধুমাত্র দূরত্বের, কিংবা তাও নয়। দু-বাংলার যাবতীয় চর্চা তাঁর নখদর্পনে ছিল এবং বিশ্বসাহিত্যের খুঁটিনাটিও। নিজস্ব লেখালেখির পরিমণ্ডলে নিরন্তর সক্রিয় ছিলেন তিনি। তা গল্প কবিতা প্রবন্ধ কিংবা সাক্ষাৎকার-ভিত্তিক যে কোনও বিভাগেই। শেষ বিদায়ের আগে পর্যন্তই অতিসক্রিয় ছিলেন, বলা যায়। আর আমরা সেসবের মূর্ছনা দেখতে পেতাম দু-বাংলার অগণিত পত্র-পত্রিকায়। শিহরিত হতে হতে মনের গভীরে ভেসে উঠত তাঁর দীর্ঘ চাবুক-দেহ, ভরাট অথচ মোলায়েম কণ্ঠস্বর, সেইসঙ্গে আপন হয়ে ওঠার তীব্র ব্যকুলতা।
২.
মলয় রায়চৌধুরীর কাব্য এবং সাহিত্যপাঠের ক্ষেত্রে আজও আমার একান্ত অবলম্বন মুর্শিদ এ এম। বিশিষ্ট এই কথাকার আমার বিশেষ আত্মজন এবং একালের একজন বিশিষ্ট প্রকাশকও (‘আবিষ্কার’ প্রকাশনী) বটে। মুর্শিদ-এর সঙ্গে কত কত সন্ধে রাত দুপুর বিকেল যে আমরা কবি-চিন্তক সমীর রায়চৌধুরীর বাসগৃহে সময়যাপন করেছি, তার ইয়ত্তা নেই কোনও। সক্কলেই জ্ঞাত আছেন যে, কবি সমীর রায়চৌধুরী সম্পর্কসূত্রে কবি মলয়দার নিজেরই অগ্রজ। এবং এই দু-ভাই হাংরি আন্দোলনের অন্যতম অগ্রদূত ছিলেন। প্রসঙ্গত বলে রাখা বাঞ্ছনীয়, কবিতা এককের শিল্প, সঙ্ঘ তৈরি করে কিংবা আন্দোলন করে আর যা-ই হোক, কবিতাচর্চা করা যায় না— এরকমের একটি ঘোরতর বিশ্বাসে নিজেকে নিয়োজিত রেখেছি এতকাল। কিন্তু তা সত্ত্বেও, কোনও রকমের সংকীর্ণতা কিংবা কুসংস্কারে বিশ্বাস ছিলাম না কখনও। ফলে, ধারাবাহিক ভাবে, যেমন গোগ্রাসে অনুধাবন করার চেষ্টা করেছি মলয় রায়চৌধুরীর কবিতা, ঠিক তেমন ভাবেই কবি সমীর রায়চৌধুরীকেও। পরবর্তী কালে এ-বিষয়টি আমার কাছে আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, সমীর রায়চৌধুরীর কাব্যভাষা পঞ্চাশের অন্যান্য কবিদের প্রায় অনুসারী, সেখানে হাংরি আন্দোলনের প্রত্যক্ষ কোনও প্রভাব খুঁজে পাইনি। কিন্তু মলয় ছিলেন ব্যতিক্রমী। তিনি যেন তাঁর দশকই শুধু নয়, বাংলা কাব্যযাত্রার সুললিত মানচিত্রটিকে ছিঁড়ে-কুটে নতুনতর একটি রূপরেখা উদ্ভাবনে মত্ত হয়ে উঠলেন। তীব্র বীর্যধারী ষাঁড়ের মতন দু-চোখে কালো কাপড় বেঁধে, ভ্রূক্ষেপহীন, লণ্ডভণ্ড, প্রথাভাঙা আর একই সঙ্গে তীব্র মননগ্রাহী সৃষ্টিশীলতায় আমৃত্যু ব্যাপৃত থাকলেন।
৩.
অধুনান্তিক ভাবধারার পথিকৃত ‘হাওয়া ৪৯’ সাহিত্যপত্রটি জন্মলাভ করেছিল কবি সমীর রায়চৌধুরীর বৌদ্ধিক চিন্তাভাবনার ফলশ্রুতিতে। কবি মলয়ের তীব্র আবেশ আর সানুগ্রহ সমর্থন ছিল তাতে। পর্যায়ক্রমে এই পত্রিকাটির সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল মুর্শিদও। হয়তো এই ত্রয়ীর মানসিক গঠন আর অগ্রসরমান চিন্তাভাবনা কোথাও একটা সমন্বয় তৈরি করেছিল। সমীর রায়চৌধুরীর প্রয়াণের পরও, এবং অবশ্যই মলয়দার অবাধ প্রশ্রয়ে, ‘হাওয়া ৪৯’-এর দায়িত্ব পরবর্তীতে একাই সামলাচ্ছিল মুর্শিদ। এখন তো মলয়দাও অনুপস্থিত হয়ে গেলেন চিরকালীন ভাবেই। তবুও এমন একটি জরুরি সাহিত্যপত্র কোনও দিন স্তব্ধ হয়ে যাবে, এমনটি ভাবতে বসলেই বুক দুরুদুরু করে ওঠে। কোথাও যেন একটা তীব্র আশার আলো আমাদের সাহস জুগিয়ে দেয়— মুর্শিদ তো আছেই! সমীরদার প্রয়াণের পর, জুন ২০১৭-তে, ‘হাওয়া ৪৯’-এর সমীর রায়চৌধুরী স্মরণ সংখ্যাটি প্রকাশিত হয়েছিল মুর্শিদ-এরই সম্পাদনায়। একটি অমূল্য সম্পাদনাকর্ম ছিল সেটি। সেখানে সমীরদা প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে লিখেছিলুম : ‘… আমার কাছে স্মৃতি বিদ্যালয়-এর ঠিকানা: বি-২৪ ব্রহ্মপুর নর্দার্ন পার্ক, কলকাতা ৭০০০৭০। যেখানে ঘুমিয়ে পড়তে চাওয়া কবিতাদের সামনে ধবধবে বিছানা পাতা। যেন তারা প্রিয় পাঠককে সঙ্গে নিয়ে ঘুমিয়ে পড়তে পারে। কিন্তু যেসব শব্দের ঘন ঘন হাই উঠছে, যেসব শব্দেরা গেছে স্নানঘরে, কিংবা যেসব ক্ষুধার্ত শব্দ এখনও আটকে আছে ডাইনিং রুমে, তাদেরকে নিয়েই চিন্তিত থাকতে হয় কবি কিংবা পণ্ডিতমশাইকে! বলাই বাহুল্য, উল্লেখিত স্মৃতি বিদ্যালয়-এর একমাত্র পণ্ডিতমশাই অষ্টপ্রহর চিন্তিত থাকতেন শব্দদের নিয়ে আর কবিতা-ভাবনায়। তিনি জানতেন, কিছু কিছু শব্দ ড্রাগ খেতে শিখেছে, আর তাদের শিরায় শিরায় ভয়ংকর ঘুম। আবার কিছু কিছু শব্দের সামনে ভোরের আলো প্রস্ফূটিত হচ্ছে। এসব অবলীলায় দেখতে পেতেন তিনি, আর দেখাতে চাইতেন আমাদেরকেও…।’ কথাটুকু উপস্থাপিত করলুম এই কারণে যে, এরও বহু বহু আগেই, এপ্রিল ২০০১-এ, কবি মলয় রায়চৌধুরীকে নিয়েও একটি অমূল্য সংগ্রহ সম্পাদনা করেছিল মুর্শিদ, গ্রন্থটির শিরোনাম ছিল ‘মলয়’। সেখানে মলয়ের লেখালেখি বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে সামগ্রিকভাবে বিশ্লেষিত হয়েছিল বহু গুণীজনের বলিষ্ট কলমের আঁচড়ে। কবি মলয় রায়চৌধুরীর কবিতা বিষয়ে আমার সেই আন্তরিক আশ্লেষের কথা এখানে অকপটে বিধৃত করতে চাইছি।
কবির আত্মপরিচয়
পৃথিবীর প্রথম প্রাণের স্পন্দন ঘিরে কবির আত্মপরিচয়। ক্রমে তা ছড়িয়ে পড়ে তৃণ থেকে সাগরে, সাগর থেকে গ্রহ গ্রহান্তরে। এই যে ইট কাঠ লতা তন্তু আর দৃশ্য অদৃশ্য সকল প্রাণী এবং জড়জগৎ সবখানেতেই আমাদের আত্মপরিচয় পোষিত হয়ে আছে। কোনও এক মহাপ্রাণ থেকে ছিটকে এসে নিজেকে টুকরো টুকরো করে ছড়িয়ে দেওয়া, আর সেই ছড়ানো ‘আমি’-কে সাধ্যমতন কুড়িয়ে আবার মহাপ্রাণে ফিরে যাওয়া— এই-ই আমাদের নিয়তি, একজন কবিরই নিয়তি। পূর্ণ থেকে ভগ্নাংশে, আবার সেই ভগ্নাংশ থেকে পূর্ণে— কোন মহাচালক যে আমাদের এমন বিচলিত করে, রক্তাক্ত করে, তার হিসেব পাই না। এর ভেতরেই নিজেদের অস্তিত্ব ঘিরে লড়াই। আর প্রাণে প্রাণে পথে পথে অস্ফুট গান গেয়ে যাওয়া। যদি কোথাও তা কোনও দিন লিপিবদ্ধ হয়ে যায়। যদি কোথাও সেই সাধকের আত্মলিপি গ্রথিত হয়ে যায়।
কবি মলয় রায়চৌধুরী কেমন ভেবেছেন তাঁর আত্মপরিচয় নিয়ে? খুঁড়ে খুঁড়ে দেখি। অল্প আয়াসেই যা খুঁজে পেয়ে যাই, তা দেখার পর এতখানি বিস্মিত হব, স্তম্ভিত হব, স্বপ্নেও তা কি ভেবেছি কোনও দিন? আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। কবিকে উদ্ধৃত করি।
ক.
“আমি ভূকম্পনযন্ত্র আণবিক যুদ্ধ দেখবো বলে বেঁচে আছি
নীল গর্দভের-লিঙ্গ-মানবের শুক্রজাত কাফ্রি খচ্চর।”
(মনুষ্যতন্ত্র)
খ.
“কীটনাশকের ঝাঁঝে মজে থাকা ফড়িঙের রুগ্ন দুপুরে
ভূজ্ঞানসম্পন্ন কেঁচো উঠে আয়
চাকুর লাবণ্য আমি আরেকবার এ-তল্লাটে দেখাতে এসেছি।”
(প্রস্তুতি)
গ.
“মরার জন্যে যারা জন্মায় আমি সেই ধর্মবংশ
বাঁচিয়ে রাখার জন্যে বারবার ঝুলিনা ফাঁসিতে।”
(আরেকবার উন্দুরু)
সময়, হে অশ্বারোহী
একজন কবি কীভাবে দেখেন বিস্তৃত এই কালপ্রবাহ এবং তাঁর সমকালকে? দুরন্ত অশ্বারোহীর মতন যে যে সময় আমাদের চতুষ্পার্শ্বে তুফান তুলে চলেছে, তার কতটুকুই বা গ্রহণ করা যায়! মর্মে মর্মে যে-ধ্বনি জাগরিত, সময়ই তার আদি এবং প্রকৃত নিয়ন্ত্রক। এই নিয়ন্ত্রণের ভিতরেই কবির চোখ মেলে দেখা। এই ধারাবাহিক গণ্ডি কি পুরোপুরি ডিঙিয়ে যাওয়া যায়? অতীত আর বর্তমানের, বর্তমান আর ভবিষ্যতের সূচকরেখায় দাঁড়িয়ে কবি আন্দোলিত হন, ক্ষতবিক্ষত হতে থাকেন, উজ্জীবিত হয়ে ওঠেন। এই উজ্জীবনের সামান্য আঁচড় ধরা পড়ে তাঁর কাব্যে, এবং অবশ্যই জীবনধারায়। তখনই কাব্য আর কবিজীবন সমার্থক হয়ে ওঠে। প্রকৃত কবির কাছে তাই কাব্য আর জীবনচারণের আদর্শগত সব পার্থক্য মুছে যায়। কাব্য থেকেই কবির প্রকৃত মুখ আমরা খুঁজে নিতে পারি। কাব্য থেকেই কবির সমকালকেও খুঁজে নিতে পারি, যা এই বিস্তৃত কালপ্রবাহে একাকার হয়ে আছে। এমনকি বিশিষ্ট কোনও উন্মত্ত সময়, যা ইতিহাস হয়ে আছে, স্মরণীয় হয়ে আছে, সেসবও কি ধরা পড়ে না কবির কলমে? সর্বত্রই আড়ি পেতে দেখি। যেমন পুলিশ আড়ি পেতেছিল সব চিঠিপত্রের ভেতর, আর চতুর্দিকে শুধুই হাতকড়া! আমরা কি ভুলে যেতে পারি সেইসব দিনগুলির কথা? কবিও ভোলেননি। তাঁর সমকালের সঙ্গে সঙ্গে তাই উঠে আসে আড়িপাতা আর হাতকড়ার গল্প, রোমশ সারেঙের গল্পও:
ক.
“পুলিশে নজর রাখে এখনও চিঠি খুলে পড়ে
ওপরঅলাহে— হাতকড়া পরে আর কতদিন যাবে
উবু হয়ে আছি চার হাতপায়ে ঝাঁপিয়ে ধরার টুঁটি দাঁতে”
(ধ্রুপদী জোচ্চোর)
খ.
“ভোর রাতে দরোজায় গ্রেপ্তারের টোকা পড়ে
একটা কয়েদি মারা গেছে তার স্থান নিতে হবে”
(অস্তিত্ব)
গ.
“নৌকোর গলুই থেকে ছুরি হাতে জ্যোৎস্নায়
বুকের ওপর বসবে লুঙি পরা রোমশ সারেঙ
নাসারন্ধ্র থেকে বন্দুকের ধোঁয়া
‘বল শালা শকুন্তলার আংটি কোন মাছে আছে?'”
প্রেম লিপ্সাই ত্যাকার প্রবাহ
সবখানেতেই প্রেম আমাদের। সবখানেতেই লিপ্সা। ঘাসবীজ থেকে মথের ডানা, চোরাগলি থেকে সুন্দরীর নাভি। কলম কোথাও সুস্থির থাকে না। ক্রমাগত লিপ্সা থেকে বিরহ, বিরহ থেকে নবতর লিপ্সায় আমাদের জড়িয়ে পড়তে থাকা। এ যেন এক চিরকালের খেলা। কবি মলয় রায়চৌধুরীও ব্যতিক্রমী নন। তাঁর সোচ্চার উচ্চারণ স্পষ্ট এবং অবগুণ্ঠিত নয়। প্রেম ও লিপ্সার ভিতর, মায়া ও সৌন্দর্যের ভিতর একটি রাগীচেতনা সর্বদাই তাঁর কবিতায় মিলেমিশে আছে। সবখানেতেই এক রাগী যুবকের উপস্থিতি আমরা সহজেই টের পেয়ে যাই। কোনও আন্দোলনকারী হিসেবে নন, একজন শুদ্ধ কবি হিসেবেই সেই রাগী যুবকের প্রেম, লিপ্সা অথবা রাগের ধরন খুঁজে নিতে চাইছি। তাঁকে ঘিরে যে সময়ের আবর্তন, যে অসম্ভব ধূর্ত আর প্রতারক জীবনযাত্রার আবর্তন, সেই আবর্তনের ভিতর ‘নারী’ কেমনভাবে বিস্তৃত হচ্ছে তাঁর কবিতায়? যে-কোনও লিপ্সার ভিতরেই একটি শুদ্ধ নারীচেতনা অদৃশ্যভাবে কাজ করে যায়। তাও স্মরণে রাখতে হবে আমাদের। উন্নত প্রেম কোনও প্রতিবন্ধকতা মানে না। এই প্রতিবন্ধকতাহীন, আড়ালহীন প্রেম কীভাবে শিল্পের কাছে আত্মসমর্পণ করে, তা তো দেখে নিতে হবে আমাদের।
ক.
“সঙ্গমের আগে মাদি পিপীলিকা ডানা খুলে রেখে দেবে পাশে”
(প্রস্তুতি)
এ পঙক্তি পড়ার পর মনে হয়, প্রেম-পরিণয়কে মাটির সাথে, রূঢ় বাস্তবের সাথে সম্পর্কযুক্ত করে তুলতে চেয়েছেন কবি। মনের দৃঢ়তা তো আছেই তাঁর। শুধু ইচ্ছে হলেই হল, সামান্য ইশারার।
খ.
“কতোদিন ইচ্ছে হয় সামান্য ইশারা করে আমার দলের লোকেদের
তোমাকে রাস্তা থেকে জোর করে তুলে নিতে বলি।”
(বাজারিনী)
গ.
কিন্তু তাঁর লিপ্সার কাছে এসে থমকে দাঁড়াই।শিউরে উঠি।
“ভিজে শায়া শাড়ি ভেতরের আঁটো জামা
দপশব্দে জ্বলে ওঠো আগুনের জিভ
চেটে নিক যোনির রেশম দুই মাই
লেলিহান কষ্টে নাভি ঝলসে উঠুক”
(কাঠামোতত্ত্ব)
এ তো গেল প্রেমের কথা, লিপ্সার কথা। এবার সেই রাগী যুবকটিকে খুঁজব। যার কোমরে সংগোপনে বাঁধা আছে পিস্তল, ক্ষুর বা ভোজালি, চুপচাপ। আর কাঁধের ঝোলা ব্যাগে থরে থরে বোমা সাজানো আছে। এমন যুবক সঙ্গে নিলে সতত সন্ত্রস্ত থাকতে হয়। যে-কোনও সময়েই লণ্ডভণ্ড হয়ে যেতে পারে সবকিছু। কেন এত রাগ আর অভিমান তার? এই সুষমামণ্ডিত পৃথিবীর কোনও অপরূপই কি পারে না তাকে শান্ত রাখতে! বিস্মিত হতে হয়। যে-জীবন পলাশের ডালে রং ছিটিয়ে দেয়, ঝাউশাখাকে আন্দোলিত করে তোলে, সে-জীবনের প্রতি কি কোনও টানই নেই তাঁর! আর এই যে সম্পর্কের বাতাবরণ, যাকে ঘিরে আমরা প্রস্ফুটিত হতে থাকি, আন্দোলিত হতে থাকি, শিহরিত হতে থাকি, সেসব কি কোনওই ছাপ ফেলে না ওই রাগী যুবকটির মর্মে? খুবই সংগোপনে ভাবি, ঘাসের ডগায় শিশিরে পা রেখে ভাবি, ধানের বুকের দুধে স্পর্শ করে ভাবি। আর কবি মলয় রায়চৌধুরী কী ভাবছেন তাঁর আপাদমস্তক ক্রোধ নিয়ে? সেই রাগী যুবকটি, যার কোমরে গোঁজা পিস্তল, আর কাঁধের ব্যাগে থরে থরে সাজানো বোমা, সেই ছায়ামুখ কেন তাঁর কবিতায় ফিরে ফিরে আসে! নাকি এই আপাতধ্বংস আর প্রলয়ের আড়ালে কোনও গূঢ় নবপল্লবের ইঙ্গিত দিতে চেয়েছেন তিনি?
ক.
“নেকড়ে বালিকার কাছে দীক্ষা নিয়ে দুর্গন্ধ মেখেছি টাকরায়
দুচোখে লঙ্কার গুঁড়ো ছুঁড়ে মারো
মুখাগ্নি করার কালে দেখবো কার থ্যাঁতা মড়া
তপ্ত সাঁড়াশি দিয়ে ছিঁড়ে নাও ধাতুকোষ বংশলোপ হোক”
(নেকড়ে বংশ)
খ.
“ছুটন্ত ঘোড়ার পিঠে দাঁড়িয়ে মশাল হাতে এগিয়ে চলেছি আমি
ঘাঁটি পতনের দিকে
দুপাশে শহর জ্বলছে
কাঁধে শিবলিঙ্গ নিয়ে ল্যাংটো মোহন্ত ছুটছে”
(পালটা মানুষ)
দখলের কথা
“দখল করছি না আপাতত কেননা এখনও অনেক বাড়ি বাকি” — এরকম পঙক্তি থেকেই একজন কবির সামগ্রিক শিল্পসত্তা আমাদের কাছে ইঙ্গিতপূর্ণ হয়ে ওঠে। দখল করা এবং তা অনায়াসে পরিত্যাগ করে অন্য দিগন্তে এগিয়ে যাওয়ার মধ্যে যে দৃঢ় আত্মবিশ্বাস আর অপূর্ণতার তৃষ্ণা খুঁজে পাই, তা একজন প্রকৃত কবিরই ক্ষরণজাত। এর সঙ্গেই যুক্ত আছে লড়বার মানসিকতা। আত্মতৃপ্তি যে-কোনও শিল্পীরই মৃত্যুর কারণ। সুখের কথা, এ-কবি অন্তত সেই শ্রেণীভুক্ত নন। নিরন্তর অতৃপ্তি তাঁকে পীড়ন করে চলেছে। ফলে অনেকদূর এগিয়ে আছেন তিনি। যা কিছু মুঠোর ভেতর, অধিকারলব্ধ, সেসব ছুঁড়ে ফেলে নতুনতর খেলায় মেতে উঠতে চান তিনি। ফলে তাঁর সৃষ্টি ব্যতিক্রমী হয়ে উঠতে চাইবে। সদাজাগ্রত মননের সঙ্গে ক্রোধ মিশিয়ে যে-বজ্রকণ্ঠ অর্জন করেছেন তিনি, একদিন এসবও হয়তো পরিত্যাগ করে নতুন বর্ণমালায় ধ্বনিত হয়ে উঠবেন।
সুরম্য এক অলীক প্রাসাদের খোঁজে আমাদের যাবতীয় গৃহহীনতা। আবার তা হয়তো খুঁজে পেয়েও দু-হাতে ঠেলে সরিয়ে নবতর প্রসাদের অন্বেষণ— এভাবেই চলতে থাকা সারাটা জীবন। এক জীবনে ঠিক কতগুলি প্রাসাদ দখল করা যায়? কতগুলিই বা পরিত্যাগ করে ডিঙিয়ে যাওয়া যায়? উত্তর মেলে না কোথাও। যেমন আমি একসময় ভেবেছিলুম: “ঠিক কতগুলি খড়খড়ি থাকে জীবনে! /কতগুলি খোলা যায়?” কোনও প্রাসাদে বন্দি হলেই কবির মৃত্যু— এমন ধারণা কি চিরকালের সত্য হয়ে উঠবে! যদি তাই-ই হয়, এমন মৃত্যু ইপ্সিত নয় কখনও। তাই এই কবির “বাড়িদখল”-এর দিকে সাগ্রহে তাকিয়ে থাকি। একদিন স্বেচ্ছায় এ-বাড়িও পরিত্যাগ করবেন তিনি, নতুন বাড়িদখলের লক্ষ্যে। আমরা তাঁর লক্ষ্যের সঙ্গে নিজেদের লক্ষ্য জুড়ে-গেঁথে দিতে থাকি।
” দরোজায় লাথি মেরে বেহায়া চিৎকার তুলছি মাঝরাত্তিরে
যারই বাড়ি হোক এটা খুলতে হবেই নাতো ভেঙে ঢুকে যাবো
সামলাও নিজস্ব স্ত্রীলোক বাঁদি সোনাদানা ইষ্টদেবতা
ফেরেবের কাগজপত্তর নথি আজ থেকে এ বাসা আমার
ভোর হলে রাস্তায় সমস্ত আসবাব ছুঁড়ে ফেলে দেবো
শস্যের গ্রীষ্মবর্ষা পাপোশের নারিকেল সারি ছায়া পোষাকের মেঘলা দুপুর
গয়নার ভালোবাসা বাসনের দিনান্তের খিদে
সদর দরোজা দিয়ে ধাক্কা মেরে বের করে দেবো
দখল করছি না আপাতত কেননা এখনও অনেক বাড়ি বাকি”
(বাড়িদখল)
ঠিক এভাবেই, সেই ২০০১-এর বহু কাল আগে থেকেই ক্রমাগত কবি মলয় রায়চৌধুরীকে চিনতে শুরু করেছিলুম, তাঁর ‘আভাঁগার্দ’ কবিতাবলীতে এসে যার পরিসমাপ্তি ঘটল।
৪.
কপিরাইট সংক্রান্ত বিষয়টিকে তিনি এতটাই গুরুত্বহীন করে তুলেছিলেন, তাঁর লেখালেখি প্রকাশনার ক্ষেত্রে বিভিন্ন সময়ে নানাবিধ দ্বন্দ্ব আর জটিলতা সৃষ্টি হয়েছে। তবুও এর ভেতরেই ২০০৬-এ আমরা হাতে পেয়েছিলাম অত্যন্ত সুমুদ্রিত ‘মলয় রায়চৌধুরীর কবিতা’ (১ম খণ্ড। প্রকাশক: আবিষ্কার)। যে-সংগ্রহে ১৯৬১ থেকে ২০০৪ পর্যন্ত লেখা কবির যাবতীয় কবিতা সন্নিবেশিত হয়েছে।স্বাভাবিক ভাবে এই সংগ্রহে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে কবির ‘শয়তানের মুখ’ (১৯৬৩), ‘জখম’ (১৯৬৫), ‘মেধার বাতানুকূল ঘুঙুর’ (১৯৮৭), ‘চিৎকারসমগ্র’ (১৯৯৫) থেকে শুরু করে ‘কৌণপের লুচিমাংস’ (২০০৩) পর্যন্ত কবিতাগ্রন্থগুলি। যেখানে ‘মালাউন’ শিরোনামের একটি কবিতায় কবি লিখেছিলেন:
“আমি লোকটা দুটো আঙুল কাটা হওয়ায় পাঁচ অব্দি গুণতে পারি না বলে
পূর্ণিমাচাঁদের শেষ কিস্তি পেয়ে নাভির তলায় জড়ুল দেখে ঠিক চিনেছি
‘তোদের এদিকটায় ভবিষ্যতের কেমন রেট যাচ্ছে রে’ জিজ্ঞেস করায়
উত্তর দিলে: ‘ফুটিসনিকো রক্তজবা নইলে পুজোর জন্যে বাজারে বিকোবি”(কৌণপের লুচিমাংস)
কী দগ্ধ সমাজবীক্ষা! ভাবতে ভাবতে বিস্মিত হতে হয়। ইতিমধ্যে গ্রন্থটির আরও দুটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে যথাক্রমে ২০১৪ আর ২০১৯-এ। এ থেকে কবির পাঠকপ্রাপ্তির কিছুটা আভাস পাওয়া যায়। গ্রন্থটির ব্লার্বে কবি উৎপলকুমার বসু লিখেছিলেন: ‘… তবে, সংক্ষেপে এটুকু বলা যায় যে মলয় রায়চৌধুরী অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়েই যুদ্ধে নেমেছিলেন…।’ ১৯৬১ – ৬৫-র মলয়ের যে নৈরাজ্যিক প্রতিষ্ঠান বিরোধিতা, যা একসময় নঞর্থক আর সামাজিক দায়হীন মনে হয়েছিল, প্রাবন্ধিক পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে ‘আজকের অবসন্নতায় ওই বিদ্রোহকে সদর্থক মনে হয়।’ এরপর গত ২০২২-এ এসে ‘আবিষ্কার’ থেকেই আমরা হাতে পেয়ে গেছি কবির পরবর্তীকালের কবিতাবলীর সুমুদ্রিত সংগ্রহ ‘মলয় রায়চৌধুরীর কবিতা
২.
গ্রন্থটির ভূমিকালিপিতে প্রকাশক আমাদের জানাচ্ছেন: “… দীর্ঘ সতেরো বছর পর ‘মলয় রায়চৌধুরীর কবিতা ২’ প্রকাশ করতে পেরে আমরা গর্বিত ও আনন্দিত। এই ব্যবধান গ্রন্থপ্রেমী মলয়ের পাঠককে আশাহত করলেও অনুরাগীদের বঞ্চিত হতে হয়নি, কারণ বিভিন্ন সোশাল মিডিয়ায় কবির দুর্দান্ত উপস্থিতি। তাঁর কবিতার পোস্ট, কবিতার আলোচনা, পাঠ, অন্য কবিদের কবিতা পাঠ, লাইভ ভিডিয়ো, সাক্ষাৎকার এবং সামাজিক নানা পোস্ট— সব মিলিয়ে কবিকে আমরা কখনোই অনুপস্থিত থাকতে দেখিনি। এই ব্যবধান কালে তাঁর কবিতার কী কী বদল ঘটেছে তা পাঠকের অধিগম্যতার বিষয়। শুধু এটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে, তিনি যেমন অনায়াসে প্রেম তথা শরীরী যৌনতায় কবিতাকে সিক্ত করেন, তেমনই সমাজবীক্ষণেও তাঁর স্বর তীব্র তীক্ষ্ণ বিস্ফোরক। সেক্ষেত্রে অতীত ও বর্তমানে কোনও প্রভেদ আছে বলে মনে হয় না…।’ এই সংগ্রহে তাঁর কবিতাবলীর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ৬৪টি হাইকু এবং ৫০টি আভাঁগার্দ কবিতা। শেষ দুটি হাইকু এখানে উদ্ধৃত করি।
ক.
মাইকে বলিউডিগান
পোস্টারে মার্কস
বিশ্বকর্মা পুজো
খ.
ওনার বিড়াল
আমার বাড়ির মাছ
তাঁর আনন্দ
কবিকে নতুনভাবে চিনতে শুরু করেছিলাম তাঁর আভাঁগার্দ কবিতাবলীতে। চিরবিদায়ের আগে পর্যন্ত এই কবিতারই চর্চায় নিমগ্ন ছিলেন তিনি। কী অসহ্য উত্তাপ আর চাবুকের পরাক্রম তাঁর কলমে, যে কোনও একটি আভাঁগার্দ কবিতা উদ্ধৃত করলেই স্পষ্ট হয়ে যাবে। এখানে ৫০ তম কবিতাটি উদ্ধৃত করছি:
“ম্যান, সিরিয়াসলি! আব ওঁম শান্তি! আঁতেলদের চারটেই হাত রাজনীতির ললনা নীল পশ্চাদ্দেশ তলে তলে আর কাক বসবে না বোঝো! মা কম্যুনিস্ট, বাপ গেরুয়া, প্রথম ধূমকেতু বাহ সাদা লোম ভালোবাসার মাত্রা শিউরে ওঠা কাণ্ডজ্ঞানহীন নরম চাই রোমকূপের শয়তান এর কারখানা তোমার কি ওফ গুটিকয় মুগ্ধ জলপরি হওয়ার ট্রায়াল যদি পোলাদের ইস্কুলের খরচ দেয় কেউই সারাজীবন ভার্জিন থাকে না। একটা সময় আসে যখন ভার্জিনিটি কেড়ে নেয়া হয়। বললেন মেঘনা। তারপর যোগ করলেন, পুরুষেরাও ভার্জিনিটি হারায়। সে নিজেই টের পায় না। পুরুষের ভার্জিনিটি শুধু মেয়েরা কাড়ে না, রাষ্ট্র, সমাজ, মতবাদ, স্বপ্ন, টাকাকড়ি, লোভ, কার্পণ্য, ক্রোধ, ক্ষোভ, দুঃখ, গ্লানি, প্রতিশোধের ইচ্ছা, হত্যা, আত্মহত্যা পুরুষের ভার্জিনিটি কেড়ে নেয়।”
এতসব কথার পরেও, প্রাবন্ধিক বাসব রায়ের ধারণাটিকে আমার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়। তাঁর ধারণা, মলয় সেরা লেখা লিখতে চাননি কখনও, চেয়েছিলেন চলমান সাহিত্যের ওপর হাতুড়ির ঘা মেরে নিজের ভাষাকে প্রতিষ্ঠা করতে। এবং কোনও সন্দেহ নেই যে তিনি সফল। আবারও একবার বলি, আমার নিজের বিশ্বাসও অনেকটা সেরকমই।
বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমিতে ফারুক আযমের কবিতা
nandik2026-01-11T20:35:04+00:00January 11, 2026|
Obsessed by Mahbubul Islam
Mahbub Islam2025-11-14T16:55:18+00:00November 14, 2025|
ফটিকছড়ির মফিজ
Fattah Tanvir2025-11-10T17:45:19+00:00November 10, 2025|
জোড়া প্রেম
Yasin Dhawan2025-11-06T16:46:09+00:00November 6, 2025|
শারীরিক সম্পর্ক কোনো দুর্ঘটনা নয়
Sudipto Mahmud2025-11-05T19:33:30+00:00November 5, 2025|