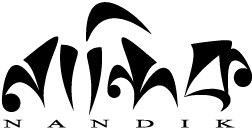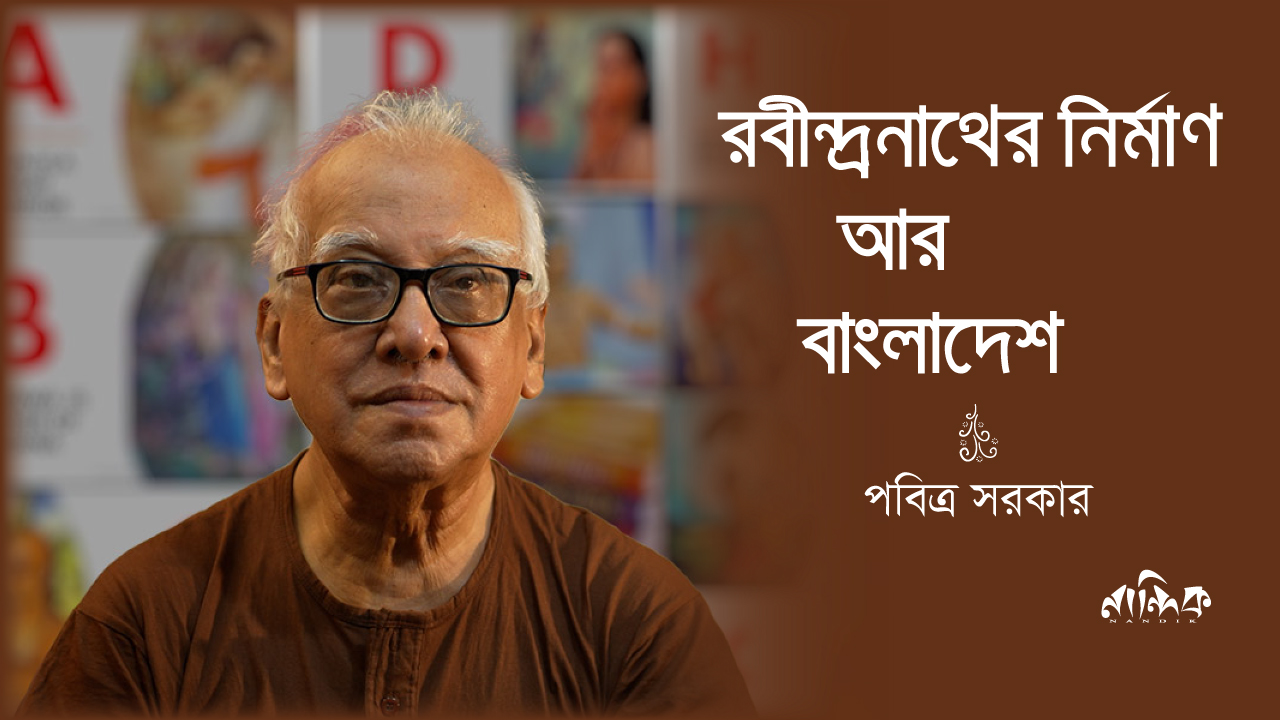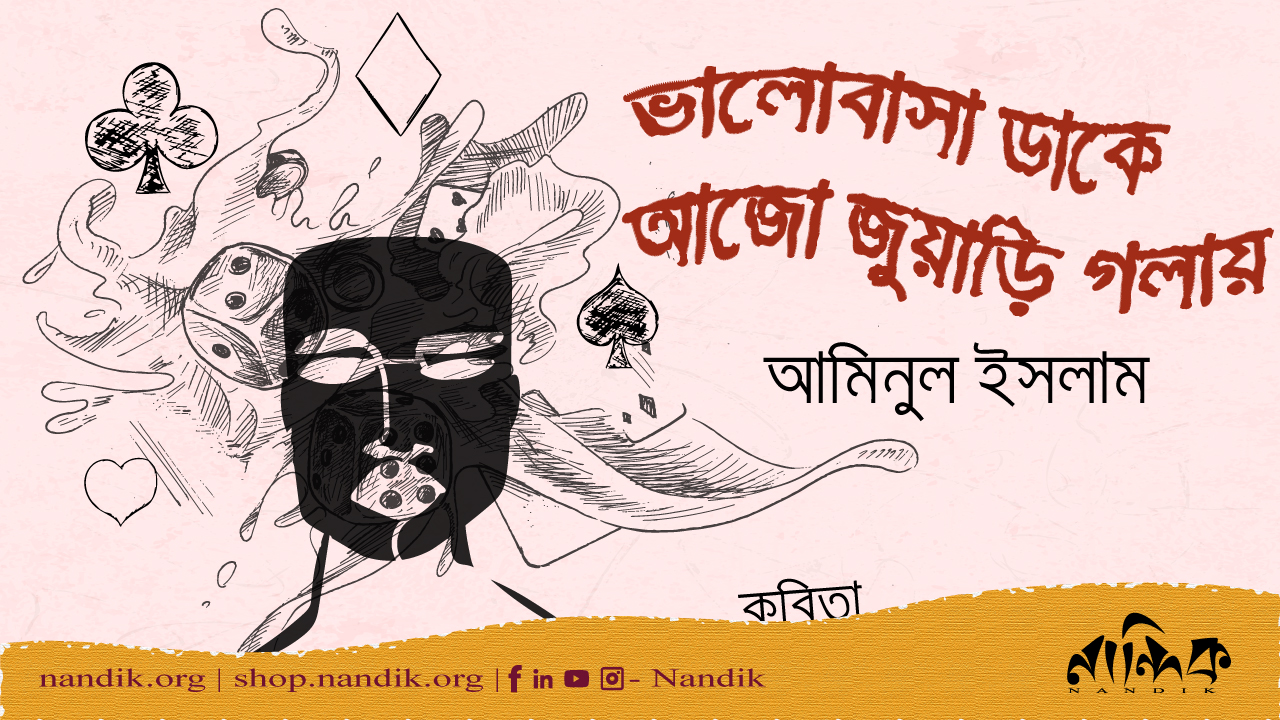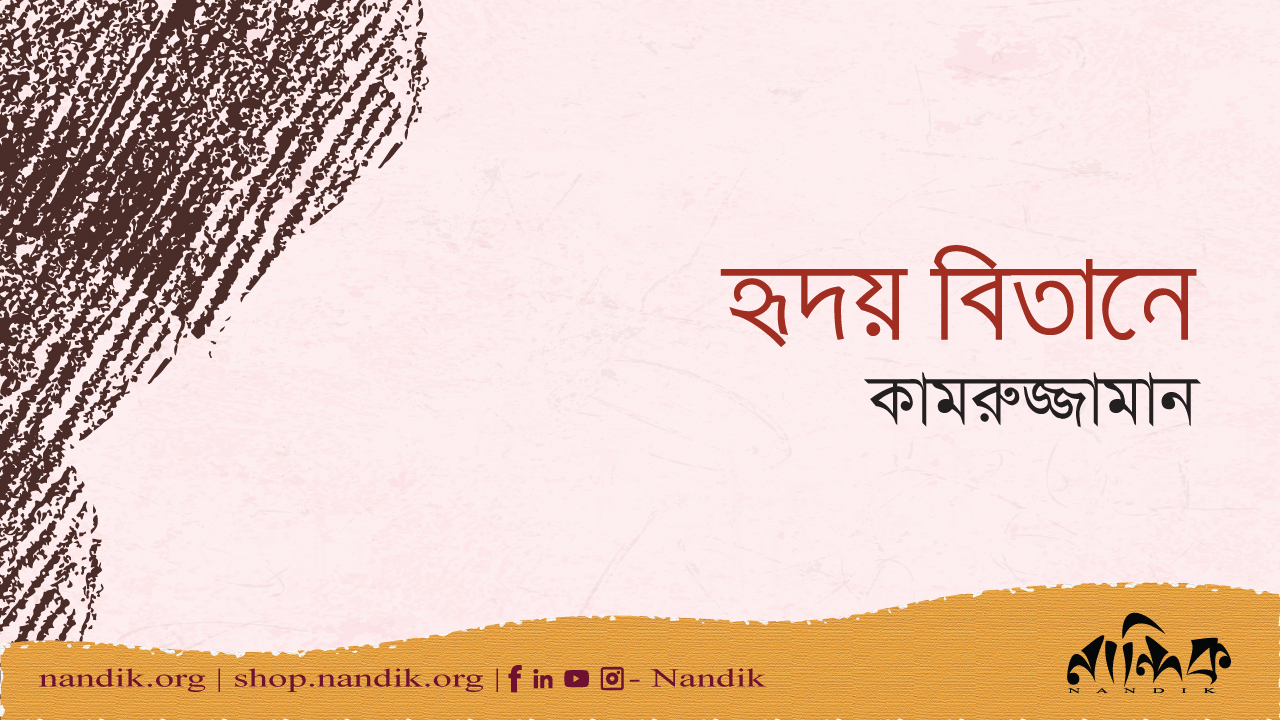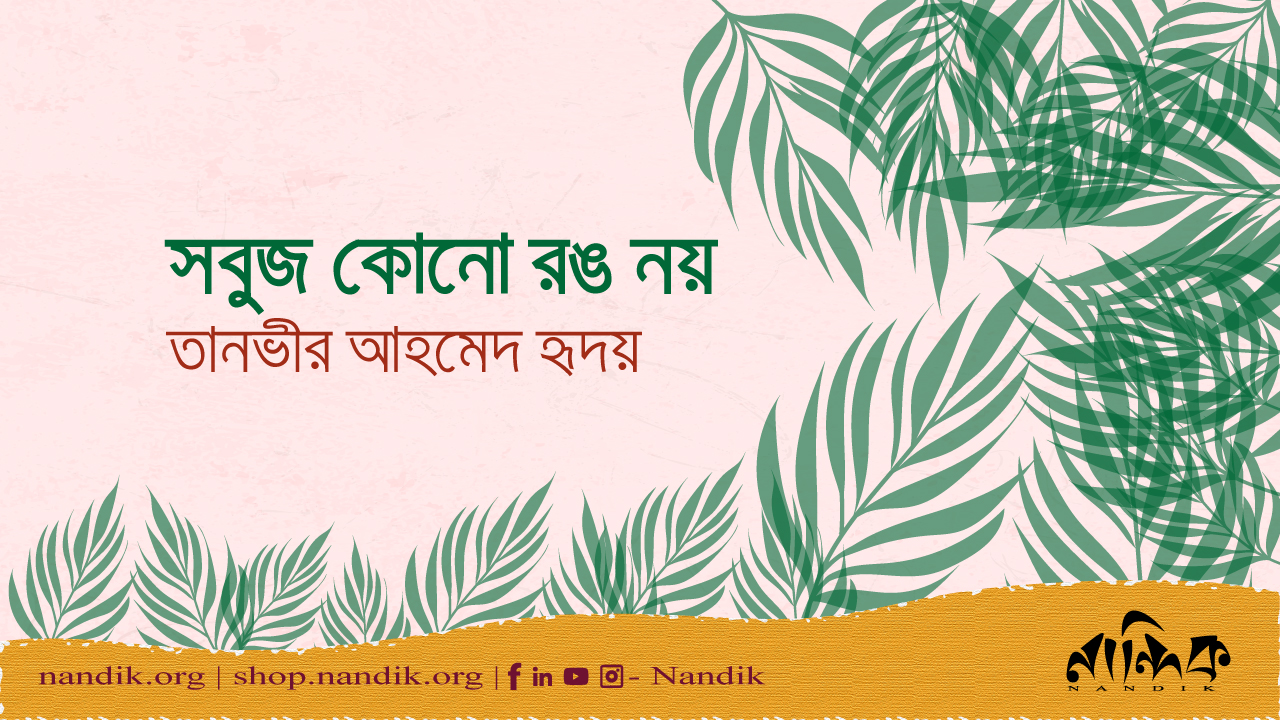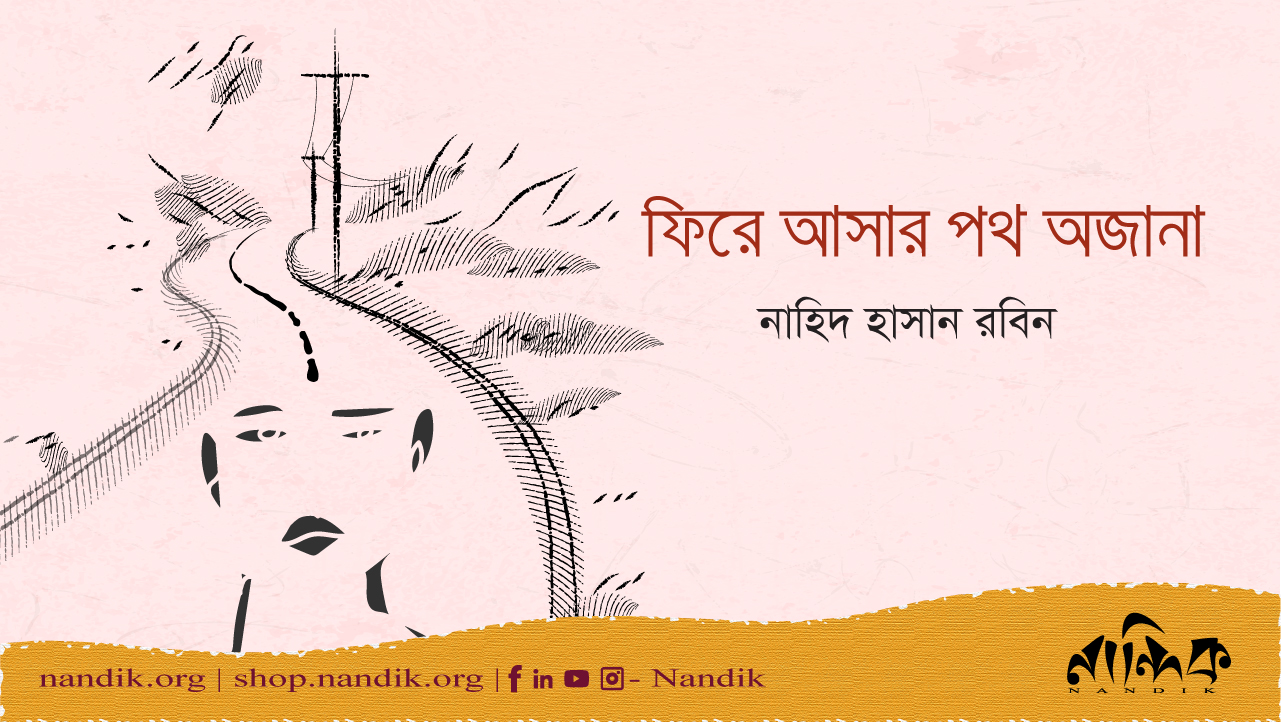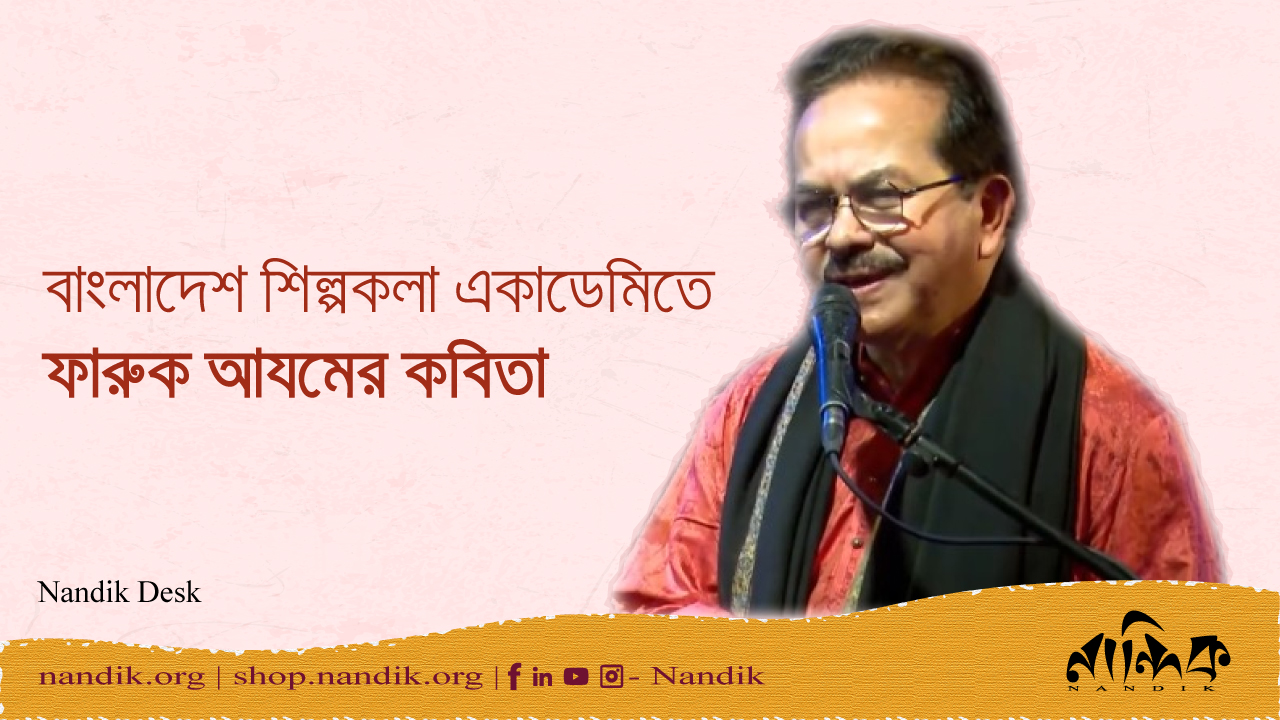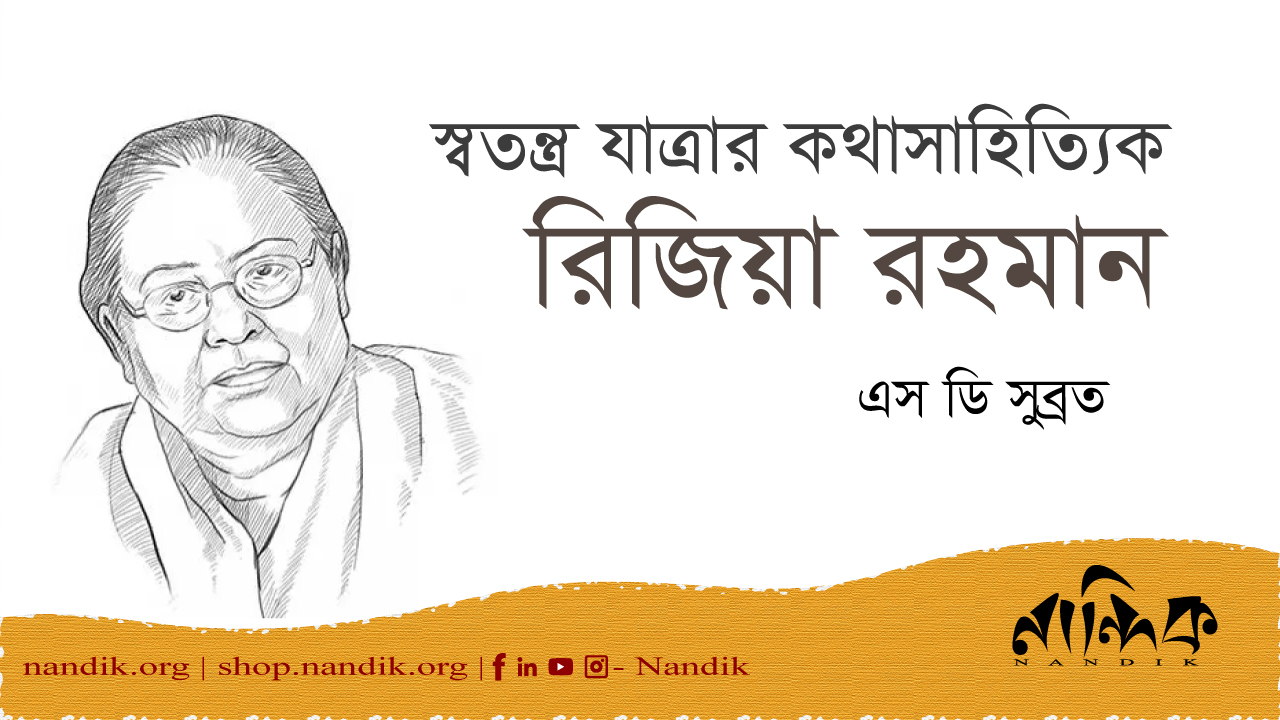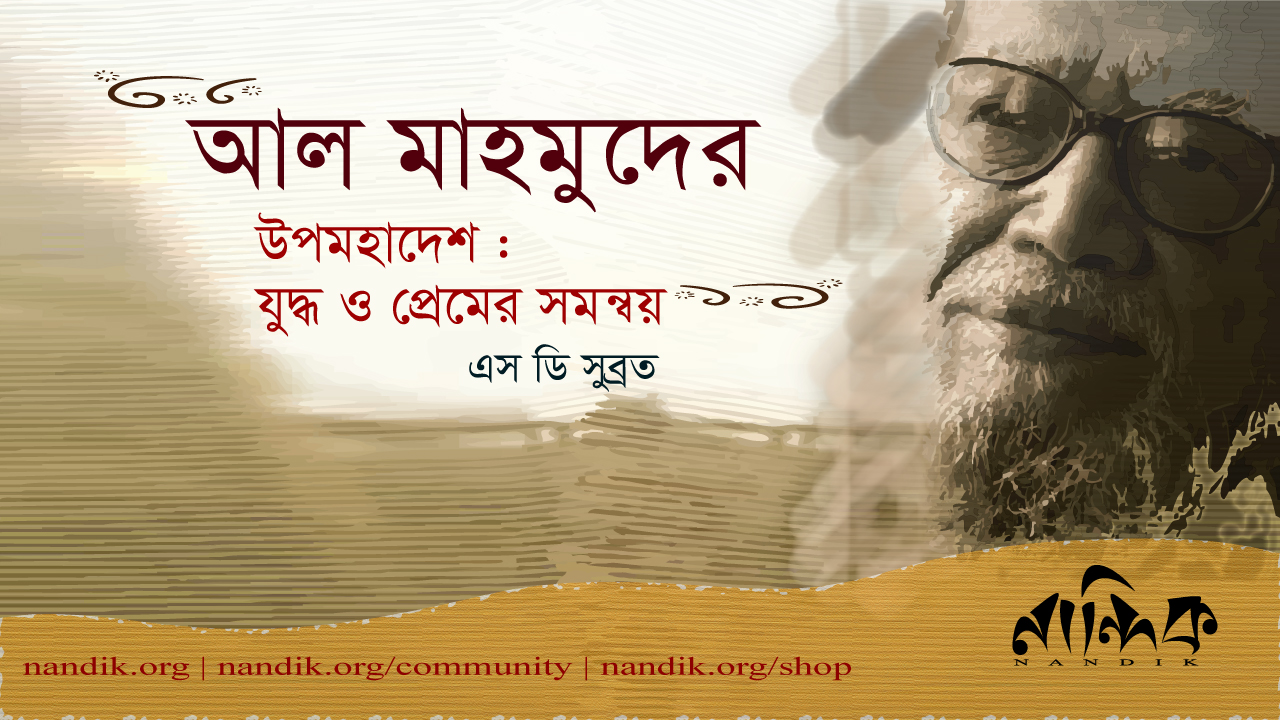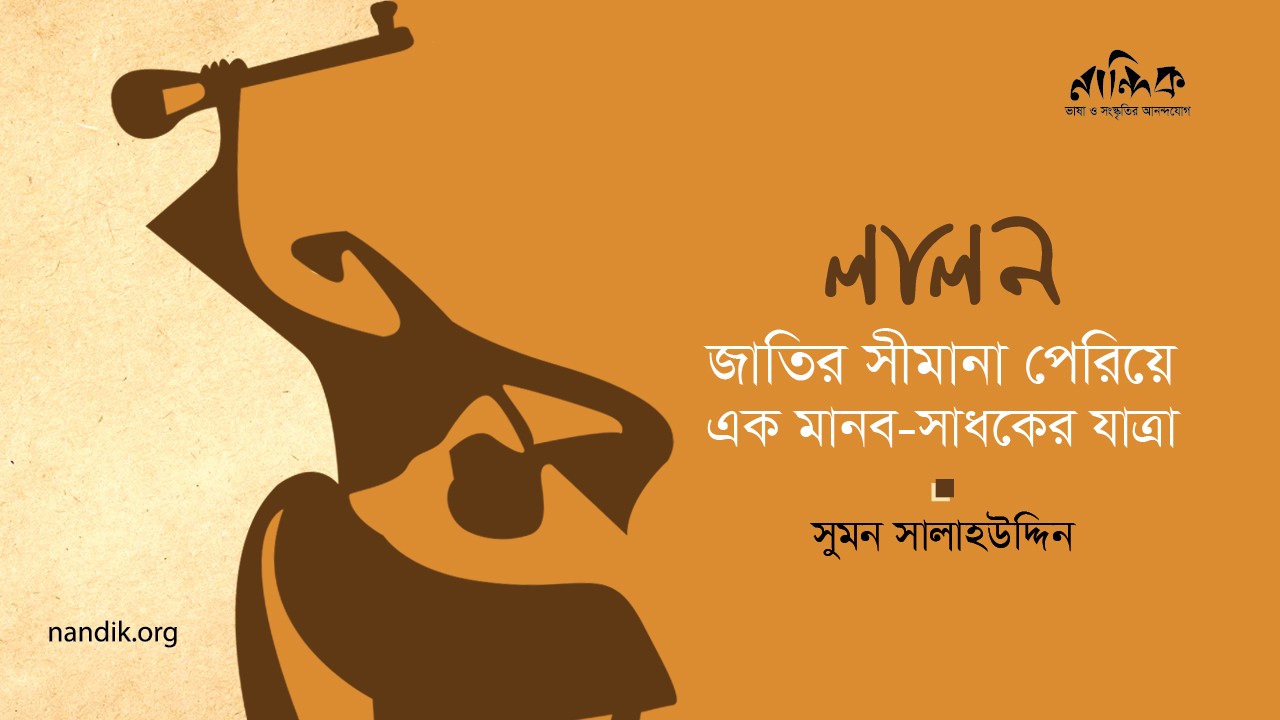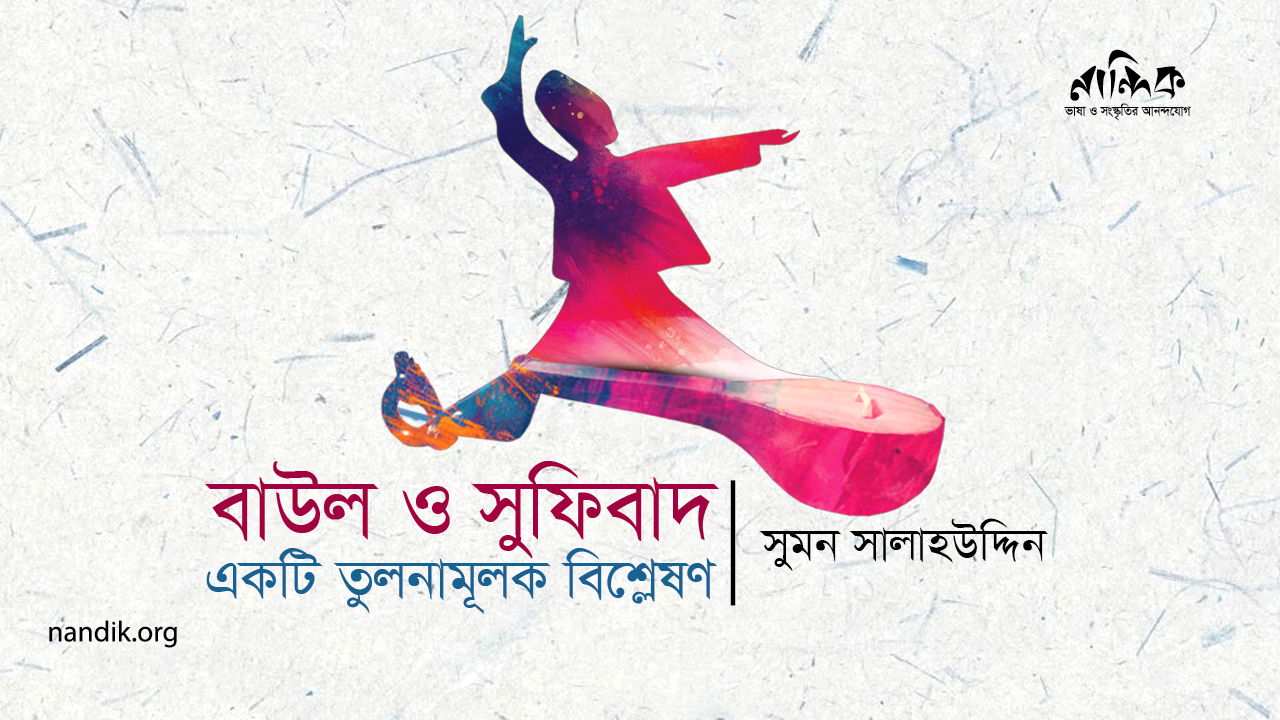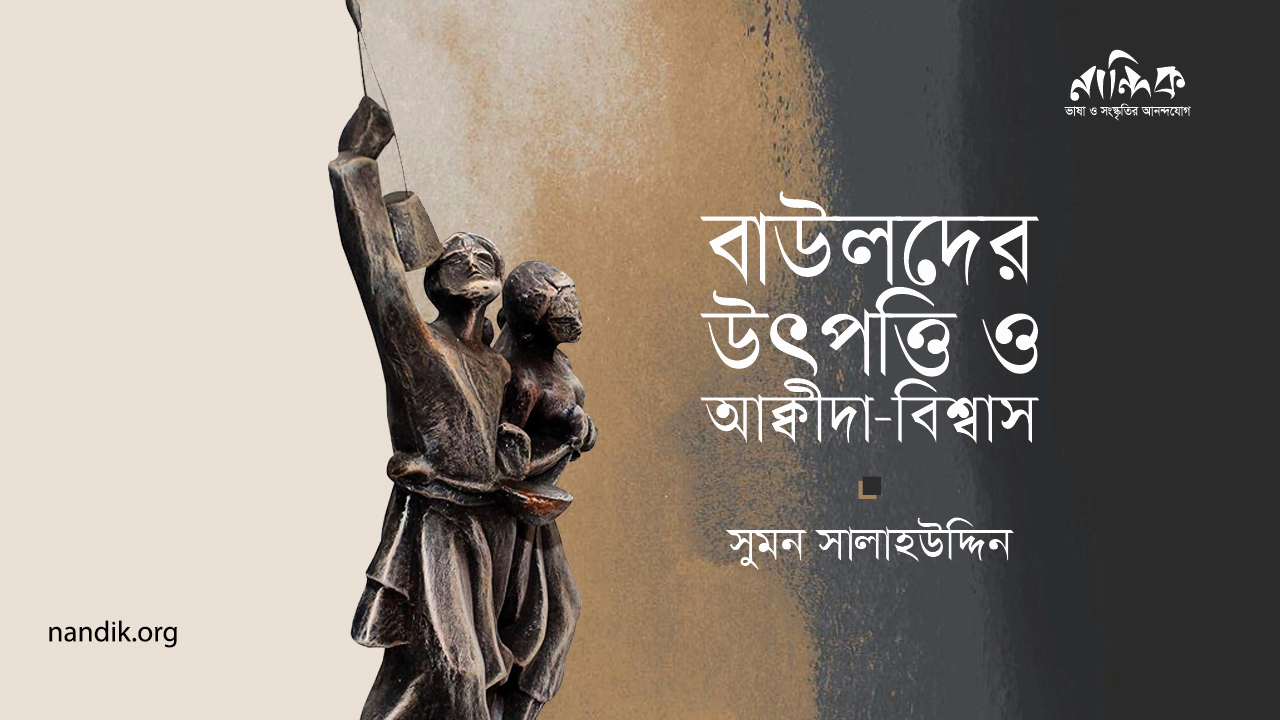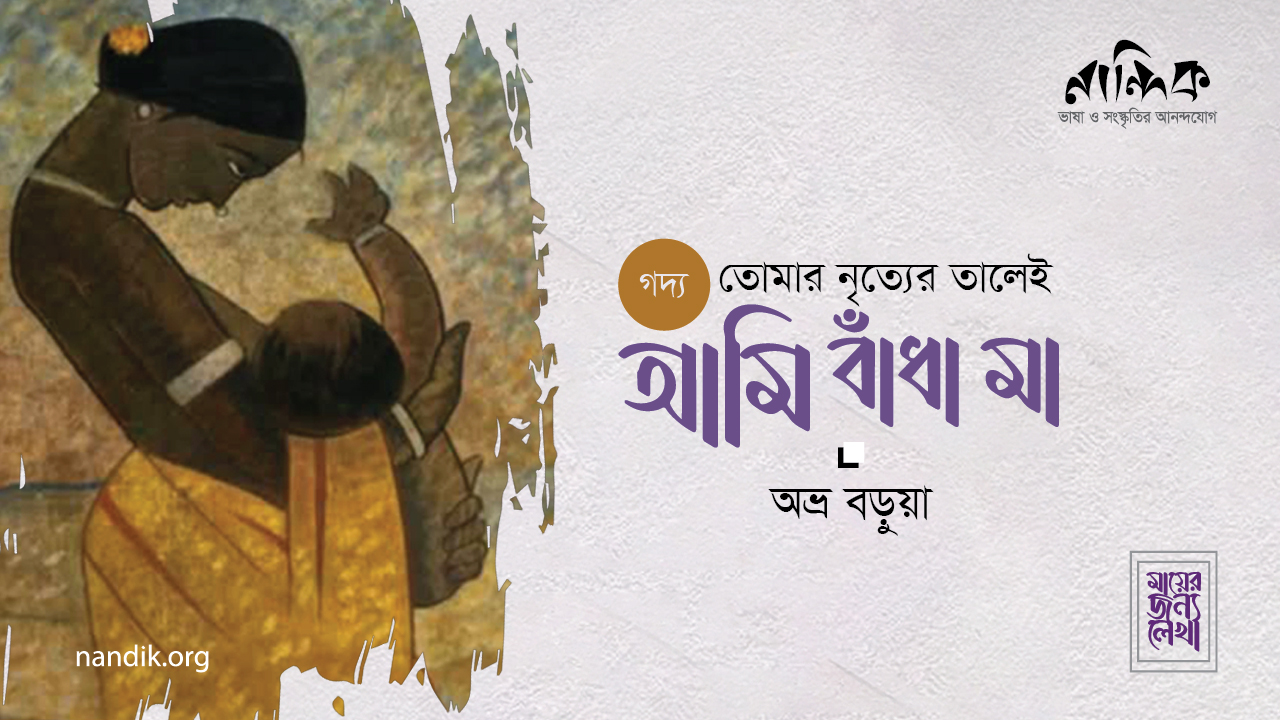রবীন্দ্রনাথের নির্মাণ আর বাংলাদেশ – পবিত্র সরকার
১
এই বিষয়ে বহুবার লেখা হয়েছে, আরও লেখা হবে। তবু প্রতিটি লেখা, অন্তত পক্ষে আলাদা আলাদা ব্যক্তির লেখা আলাদা হওয়ার কথা, এমনকি একই ব্যক্তির একই বিষয়ে আলাদা লেখা আলাদা হওয়ার কথা। সেই ভরসায়, একটি পুরোনো লেখা নতুন করে সাজিয়ে দেওয়া যাক। রবীন্দ্রনাথকে কী করে সাবেক পূর্ববঙ্ঘ, অধুনা বাংলাদেশ পূর্ণাঙ্গ করে নির্মাণ করেছিল, সে সম্বন্ধে একটি ব্যক্তিগত, সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা। এ সম্বন্ধে গ্রন্থও আছে একাধিক, তবু একটু সাহস করে লেখার চেষ্টা, একটু নতুন করে ভাবার।
কলকাতার নগরবলয়ে যাঁর জন্ম, তিনে শৈশবে প্রকৃতিকে “আড়াল-আবডাল হইতে” দেখতেন, বা শুনতেন। আস্তে আস্তে কয়েকটি ধাপে বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে তাঁর পরিচয়ের বিস্তার ঘটল। পেনেটির বাগানবাড়ি, হিমালয় যাত্রা, বিদেশে প্রবাস, যাত্রাপথের নানামুখী অভিজ্ঞতা– ঘরে ফিরে এখানে ওখানে ছোটখাটো ভ্রমণ, তার পরে একেবারে নদীমাতৃক পূর্ববঙ্গের বিশাল আকাশবিস্তার, ১৮৯১ থেকে ১৯০১ পর্যন্ত যার ধারাবাহিক অভিভব।
ইংরেজি ‘ইকোলজি’ কথাটার বাংলা ‘প্রতিবেশ’ খুব সাদামাঠা শোনায়। ইংরেজি কথাটার মূল জোর নিসর্গ-প্রতিবেশের উপর, কিন্তু আমাদের মনে হয়, প্রতিবেশকে যদি নিছক বিমূর্ত ও ভাববদ্ধ অস্তিত্ব হিসেবে না দেখি, তাকে ব্যক্তিমানুষের সঙ্গে আদানপ্রদানবদ্ধ এক জীবন্ত ও সক্রিয় সত্তা হিসেবে দেখি, তা হলে ‘ইকোলজি’ কথাটার অর্থের মধ্যে মানুষকেও ধরে নিতে হবে।
আবার প্রকৃতিরে সঙ্গে যুক্ত হয় মানুষের নানা নির্মাণ, মূর্ত, বাস্তব আর আধিমানসিক—যার সবটা মিলিয়ে তার সংস্কৃতি। তার সঙ্গে নিসর্গ-প্রতিবেশের সম্পর্ক জটিল—কখনও বন্ধুত্বের, অধিকাংশ সময় শত্রুতার। মানুষ নিসর্গকে ব্যবহার, শোষণ এবং অনেক ক্ষেত্রে ধ্বংস করেই নিজের আগ্রাসী আরামস্পৃহার প্রতিষ্ঠা দিতে চায়। এও আর-এক ধরনের ‘প্রতিবেশ’—যার সঙ্গে ব্যক্তিমানুষের নিত্য দেওয়া-নেওয়া চলে। এ লেখা পাশ্চাত্য ইকো-ক্রিটিসিজমের মধ্যে পড়বে কি না জানি না, কিন্তু একটি প্রতিবেশ কীভাবে একজন স্রষ্টাকে নানাভাবে উন্মোচিত ও প্রকাশিত হতে সাহায্য করে পূর্ববঙ্গের বিস্তীর্ণ নদীবিধৌত শ্যামল ভূমিতে রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার এক ধরনের বিস্ফোরণ তার সাক্ষ্য। প্রতিবেশকে কারণ এবং রবীন্দ্রনাথের বিপুল ও বহুমুখী সৃষ্টি-উৎসারকে তার কার্য বললে যদি কেউ কোনো যান্ত্রিক নির্ধারণবাদের (ডেটারমিনিস্ম) গন্ধ পান, তা হলে তাঁকে বলব, ওই প্রতিবেশটিকে বাদ দিয়ে রবীন্দ্রনাথের দশ-বারো বছরের বহুধাবিচ্ছুরিত সৃষ্টিকে ভাবা সম্ভব কি না সে প্রশ্নের তাঁকে উত্তর দিতে হবে।
সেই সূত্র ধরে যদি বলি রবীন্দ্রনাথ শেষ পর্যন্ত যা, তার শতকরা পঞ্চাশ ভাগ নির্মাণ করেছে পূর্ববঙ্গ—সেই হিসেব নিয়ে তর্ক উঠতেই পারে—কেউ বলবেন আরও বেশি, কেউ সামান্য কম ধরবেন ; বেশি বললে আপত্তি করব না। কিন্তু পূর্ববঙ্গকে বাদ দিয়ে কবিতা-গল্প-উপন্যাস-নাটক-সংগীত আর জীবনভাবনায় এক অভাবিত সম্পূর্ণতার ছবি যে রবীন্দ্রনাথ, তাঁকে একেবারেই পাওয়া যাবে না।
অবশ্যই এই নিয়ে বহুবিধ অনুসন্ধান ও গবেষণা হয়েছে। প্রমথনাথ বিশীর আলোচনা আছে ছোটগল্পের নির্দিষ্ট পরিসর থেকে। শচীন্দ্রনাথ অধিকারীর বহু বিবরণও দুর্লভ নয়। অধ্যাপক গোলাম মুরশিদের ভিত্তিসূচক বইটি আছে, আছে আরও বহু গবেষকের আলোচনা। সে সব আলোচনাকে শ্রদ্ধা জানিয়ে আমি আমার মতো করে পূর্ববঙ্গের পটভূমিকায় দুই রবীন্দ্রনাথকে দেখতে চাই। একজন হলেন স্রষ্টা রবীন্দ্রনাথ, আর একজন হলেন ব্যক্তি রবীন্দ্রনাথ। অবশ্যই এ দুয়ের মধ্যে নিছক ব্যাখ্যার জন্যই আমরা তফাত করছি, কারণ অন্নদাশঙ্কর রায় যেমন বলেছেন, ‘জীবনশিল্পী’ রবীন্দ্রনাথ নিজের ব্যক্তিজীবনকেও একটি রচনা এবং প্রকাশ হিসেবে লক্ষ্য করেছেন। সবই তাঁর সৃষ্টি—শিল্প এবং জীবন। তবু, দুটিকে কিছুটা কৃত্রিমভাবে হলেও, আলাদা করে আনলে আমাদের হয়তো বুঝতে সুবিধে হবে।
প্রথম রবীন্দ্রনাথের জন্য, স্রষ্টা রবীন্দ্রনাথের জন্য, পূর্ববঙ্গ—শিলাইদহ-পতিসর-শাহাজাদপুরের ওই আকাশব্যাপ্ত চিরশ্যামল, পদ্মা-পরিকীর্ণ অনন্তবিস্তারিত ভূখণ্ড রবীন্দ্রনাথকে দিয়েছিল এমন এক নির্জনতা আর সৌন্দর্য-পরিসর, যা যে কোনো স্রষ্টার পরম কাম্য। এমন নয় যে এখানে রবীন্দ্রনাথ জনবিমুখ আত্মবৃত্তবদ্ধ কোনো অন্তরালবর্তী জীবন যাপন করেছেন। এখানে তাঁর পরিবার ছিল সঙ্গে, জমিদারির কর্মচারীরা ছিল, বন্ধুবান্ধবেরা কলকাতা ও অন্যত্র থেকে এসেছেন আতিত্য নিতে, ছিল তাঁর প্রজাদের সঙ্গে নিত্য দেখাশোনা। তবু দিনের একটা মুল্যবান অংশ—সকাল, বিকেল, সন্ধ্যা ও রাত্রের একান্ত অবকাশ, পদ্মা বোটে তাঁর একার জীবন, চারপাশের প্রাকৃতিক সুবিস্তারে তাঁর বিচরণ, সূর্যের আলো, বর্ষাশরৎশীতগ্রীষ্মের উপগম, পাখির ডাক—নিসর্গের রূপরসশব্দগন্ধস্পর্শ তাঁকে এমন একটি সৃষ্টির অবকাশ দিয়েছিল যা তিনি অন্যত্র, বিশেষত মহানগর কলকাতায়, পেতেন না তা নিঃসন্দেহে বলা যায়।
রবীন্দ্রনাথ মাঝে মাঝেই সৃষ্টির জন্য, ধ্যানের জন্য ‘ঘূর্ণচক্র জনতাসঙ্ঘ’ থেকে এইরকম আত্মপ্রত্যাহারের কথা বলেছেন। ‘সময় হয়েছে নিকট, এবার বাঁধন ছিঁড়িতে হবে।’ একদিকে মানবসমাজ ও কর্মময় পৃথিবী, অন্যদিকে নিজের সৃষ্টির জন্য কিছুটা নির্জন একান্ত অবকাশ—এ দুই কোটিতে তিনি কতবার দ্বিধাগ্রস্ত থেকেছেন, তার তালিকা দীর্ঘ। কিন্তু মূল কথা হল, পূর্ববঙ্গ তাঁকে এই বিশ্রান্তি দিয়েছিল। “এই লোকনিলয় শস্যক্ষেত্র থেকে ওই নির্জন নক্ষত্রলোক পর্যন্ত একটা স্তম্ভিত হৃদয়রাশিতে আকাশ কানায় কানায় পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে, আমি তার মধ্য অবগাহ্ন করে অসীম মানসলোকে একলা বসে থাকি।” রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীকে লেখা একটি চিঠিতে তাঁর স্বীকারোক্তি—“আমি সূর্য চন্দ্র নক্ষত্র এবং মাটি পাথর জল সমস্তের সঙ্গে এক সঙ্গে আছি এই কথাটা এক শুভ মুহূর্তে যখন আমার মনের মধ্য স্পষ্ট সুরে বাজে তখন একটা বিপুল অস্তিত্বের নিবিড় হর্ষে আমার দেহমন পুলকিত হইয়া উঠে। ইহা আমার কবিতা নহে, ইহা আমার স্বভাব। এই স্বভাব হইতেই আমি কবিতা লিখিয়াছি, গান লিখিয়াছি, গল্প লিখিয়াছি।” তাই তাঁর সৃষ্টির উৎসধারা খুলে গিয়েছিল ১৮৯১ থেকে ১৯০১-এর মধ্যে, এবং তার পরেও শিলাইদহ তাঁকে নানাভাবে পুষ্ট করেছে, সমর্থন দিয়েছে। গানে, কবিতায়, ছোটোগল্পে, উপন্যাসে, নাটকে, প্রবন্ধে—সে সৃষ্টিধারার তালিকা করা এখানে সম্ভব নয়। এমনকি তাঁর ছবি আঁকারও সূত্রপাত সম্ভবত এখানে—জগদীশচন্দ্র বসুকে লেখা চিঠিতে তাঁর স্কেচের খাতায় প্রাণপণ স্কেচ করার খবর পাই। আর যে ইংরেজি ‘গীতাঞ্জলি’র কবিতা তাঁর জন্য ছিনিয়ে আনবে নোবেল পুরস্কার, তারও অনুবাদকর্মের অনেকটাই ঘটেছে শিলাইদহে, ১৯১২ সালে, অসুস্থতার বিশ্রামসূত্রে, সেখানে “চৈত্রমাসে আমের বোলের গন্ধে আকাশে আর কোথাও ফাঁক ছিল না এবং পাখির ডাকাডাকিতে দিনের বেলার সকল কটা প্রহর একেবারে মাতিয়ে রেখেছিল।”
আর পরে আমরা দেখব, রবীন্দ্রনাথের যে বিশেষ জীবনদর্শন—“হে জীবন তোমার সঞ্চয় দিনান্তে নিশান্তে শুধু পথপ্রান্তে ফেলে যেতে হয়”—তা আমাদের মতে তাঁর পদ্মানদীর দীক্ষা, যে নদী “চলার বেগে পাগলপারা”, যে পৃথিবীর মতো নির্মম ও উদাসীন। তাই পদ্মা আর মধ্যপূর্ববঙ্গের জীবন তাঁকে সারা জীবন সঙ্গ দিয়েছে, তাঁকে নির্মাণ করে গেছে, তাঁর জীবনক্ষেত্রে একটি বিচ্ছিন্ন অধ্যায়মাত্র হয়ে থাকেনি। তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে পুব বাংলার গগন হরকারা, সিরাজ সাঁই, হাসন রাজা ও অন্যান্য বাউল-ফকিরদের গান শুনে তাঁর আত্মবীক্ষণ—যা তাঁর ধর্মদর্শন এবং ধর্মচিন্তাকেও চূড়ান্ত রূপ দিয়েছিল। তাঁর ‘সোনার বাংলা’ গানটি সুরে ও ছবিতে মূলত পূর্ববঙ্গকেই ধারণ করেছে।
২
এবার ব্যক্তিটির কথা। জমিদারি দেখতে এলেন এক জমিদার-তনয়। জমিদারির সঙ্গে ‘আশমানদারি’ও চলল তাঁর, সে খবর আমরা উপরে বলেছি। জমিদার-গনয়টি দীর্ঘস্থায়ী আবাসসূত্রে পূর্ববঙ্গে পৌঁছানোর ছয় বছর আগে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ঠাকুর পরিবার তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মনে হয়েছে ওই ‘বাবু’দের কংগ্রেস “আপন মায়েরে নাহি জানে।” কেন এ কথা মনে হল তাঁর ? কারণ সম্ভবত এর মধ্যেই তিনি পড়েছেন রবার্ট লুই স্টিভন্সনের লেখায় জাপানি বিপ্লবী ইয়োশিদা তোরাজিরোর কথা (দ্র. ‘ছাত্রদের প্রতি সম্ভাষণ’), যিনি নিজেকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, আমি জাপানকে ভালোবাসি, জাপানের জন্য আমি জীবন উৎসর্গ করব। কিন্তু কোন্ জাপানকে ? আম্মার দেশকে কি আমি চিনি ? দেশকে চেনার জন্য তোরাজিরো “চাল-চিঁড়া বাঁধিইয়া পায়ে হাঁটিয়া ক্রমাগতই সমস্ত দেশ কেবলই ভ্রমণ করিয়া বেড়াইয়াছেন।” এইভাবে “দেশকে তন্ন তন্ন করিয়া” জনা রবীন্দ্রনাথের ঘটল পূর্ববঙ্গে এসে—তিনি দেশকে বুঝলেন, বুঝলেন যে, দরিদ্র, শোষিত, বঞ্চিত মানুষই সত্যকার ভারতের মুখ, তাদের বাদ দিয়ে দেশ কেবল ভূগোলমাত্রে নয়, কল্পনামাত্র নয়। এই মানুষগুলিকে বাদ দিয়ে ‘ভারতমাতা’, ‘ভারতলক্ষ্মী’ ইত্যাদি কথাগুলি অন্তঃসারশূন্য। ওই প্রবন্ধ থেকেই অসামান্য কয়েকটি ছত্র উদ্ধার করি, “ভারতমাতা যে হিমালয়ের দুর্গম চূড়ার উপরে শিলাসনে বসিয়েয়া কেওলই করুণ সুরে বীণা বাজাইতেছেন, এ কথা ধ্যান করা নেশা করা মাত্র—কিন্তু ভারতমাতা যে আমাদের পল্লীতেই পঙ্কশেষ পানাপুকুরের ধারে ম্যালেরীয়া-জীর্ণ প্লীহারোগীকে কোলে লইয়া তাহার পথ্যের জন্য আপন শূন্য ভাণ্ডারের দিকে হতাশদৃষ্টিতে চাহিয়া আছেন, ইহা দেখাই যথার্থ দেখা।” এই দেখার সূত্র রবীন্দ্রনাথকে দিয়েছিল পূর্ববঙ্গ। তাই জমিদার রবীন্দ্রনাথ এসে দাঁড়িয়েছিলেন দরিদ্র প্রজার পাশে, তাদের জমির মাটি পরীক্ষা, জমিতে চাষের জন্য ট্রাক্টরের ব্যবহার, মাদ্রাজ থেকে ভালো আলু-বীজের ব্যবস্থা করা, একফসলি চাষে বছরের নিষ্কর্মা সময়ে তাদের বিকল্প প্রশিক্ষণের (কলাই-করা বাসন বা মৃৎশিল্প বা ছাতা তৈরি), তাদের জন্য পতিসরে সমবায় ব্যাংক স্থাপন করে তাতে নোবেল পুরস্কারের টাকা অর্পণ (যা আর তাঁর কাছে ফিরে আসবে না)। এমনকি পুত্র রথীন্দ্রনাথ আর ছোটো জামাতা নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়কে যে আরবানাতে ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়ে কৃষিবিজ্ঞান পড়তে পাঠিয়েছিলেন তাও এই ভূখণ্ডের প্রজাদের কথা ভেবেই। রবীন্দ্রনাথের গোরা যথার্থ দেশকে চিনেছিল ওই চরঘোষপুর গ্রামে গিয়েই। এই কল্পিত গ্রামকে পূর্ববঙ্গের ভূগোলেই রবীন্দ্রনাথ স্থাপন করেছেন।
শিলাইদহ ও পূর্ববঙ্গের সঙ্গে তাঁর প্রত্যক্ষ যোগ ছিন্ন হওয়ার পর ১৯১৫ থেকে শ্রীনিকতনকে ভিত্তি করে যে গ্রামোন্নয়নের কর্মসূচির সূত্রপাত হয়, তার মূলে আছে তাঁর পূর্ববঙ্গের এই উদ্যম ও আগ্রহের প্রেরণা। সেই সঙ্গে আমাদের এও মনে হয় যে, লোকসৃষ্টি ও লোকশিল্পের প্রতি রবীন্দ্রনাথের আজীবন সঞ্চারিত আকর্ষণের পিছনে আছে তাঁর পূর্ববঙ্গের হাট-বাজার-মেলার অভিজ্ঞতা।
তাই মনে হয়, রবীন্দ্রনাথের দেশপ্রেম আর জাতীয়তাবাদের ধারণাও তৈরি করে দিয়েছিল পূর্ববঙ্গ, যা এখন বাংলাদেশ। আর, আগে উল্লেখ করেছি, তাঁর যে জীবনের চলতার জীবনদর্শন, তথাকথিত গতিবাদ, তাঁর উৎস ফরাসি দার্শনিকে বের্গসঁ- Elan vital কি না তা আমি পরিষ্কার বলতে পারব না। এবং তা ‘বলাকা’ কাব্যে হঠাৎ উদ্গত হয়নি, তার আঘেও বহুবার তাঁর রচনায় দেখা দিয়েছে। কিন্তু আমাদের মনে হয়, তাও তৈরি করে দিযেছিল পদ্মানদী, যে নদী কেবলই চলে, উদাসীন তার চলা, সব কিছুকে পিছনে ফেলে চলে যেতে তার ভ্রুক্ষেপ নেই। মনে পড়বে ‘পোস্টমাস্টার’ গল্পের শেষের আগের অনুচ্ছেদের কয়েকটা লাইনে—“যখন নৌকায় উঠিলেন এবং নৌকা ছাড়িয়া দিল, বর্ষাবিস্ফারিত নদী ধরণীর উচ্ছলিত অশ্রুরাশির মতো চারিদিকে ছলছল করিতে লাগিল, তখন হৃদয়ার মধ্যা অত্যন্ত একটা বেচনা অনুভব করিতে লাগিলেন—একটা সামান্য গ্রাম্য বালিকার করুণ মুখচ্ছবি যেন এক বিশ্বব্যাপী বৃহৎ অব্যক্ত মর্মব্যথা প্রকাশ করিতে লাগিল। একবার নিতান্ত ইচ্ছা হইল, ‘ফিরিয়া যাই, জগতের ক্রোড়বিচ্যুত সেই অনাথিনীকে সঙ্গে করিয়া লইয়া আসি’—কিন্তু তখন পালে বাতাস পাইয়াছে, বর্ষার স্ৃোত খরতর বেগে বহিতেছে, গ্রাম অতিক্রম করিয়া নদীকূলের শ্মশান দেখা দিয়াছে—এবং নদীপ্রবাহে ভাসমান পথিকের উদাস হৃদয়ে এই তত্ত্বের উদয় হইল, জীবনে এমন কত বিচ্ছেদ, কত মৃত্যু আছে। ফিরিয়া ফল কী। পৃথিবীতে কে কাহার।”
পরে ‘যাত্রার পূর্বপত্র’ প্রবন্ধেও (‘পথের সঞ্চয়’, ১৯১২) তাঁর উচ্চারণ ছিল, “চলো, চলো, চলো, প্রভাতের পাখির মতো চলো, অরুণোদয়ের আলোর মতো চলো”, কিন্তু আমাদের মতে বিশেষ নদী পদ্মাই তাঁর ‘বলাকা’য় নির্বিশেষ’ এক ‘নদী: (“হে বিরাট নদী, অদৃশ্য নিঃশব্দ তব জল, …চলে নিরবধি”) হয় রবীন্দ্রনাথের ‘বলাকা’য়, তার পর তা জীবনে নিরন্তর চলতাধর্মের প্রতীক হয়ে ওঠে।
এখন যদি কেউ দাবি করেন রবীন্দ্রনাথকে শতকরা ৯০ শতাংশ নির্মাণ করেছে পূর্ববঙ্গ, তা হলেও আমার আপত্তি খুব দুর্বল হবে।
ভালোবাসা ডাকে আজো জুয়াড়ি গলায়
Aminul Islam2026-02-20T15:47:05+00:00February 20, 2026|
হৃদয় বিতানে
Quamruzzam Swapan2026-02-12T17:43:42+00:00February 12, 2026|
সবুজ কোনো রঙ নয়
Tanvir Ahmed Hridoy2026-02-07T16:29:37+00:00February 7, 2026|
ফিরে আসার পথ অজানা
Nahid Hasan Robin2026-02-06T17:10:29+00:00February 6, 2026|
বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমিতে ফারুক আযমের কবিতা
nandik2026-01-11T20:35:04+00:00January 11, 2026|