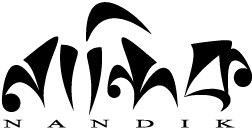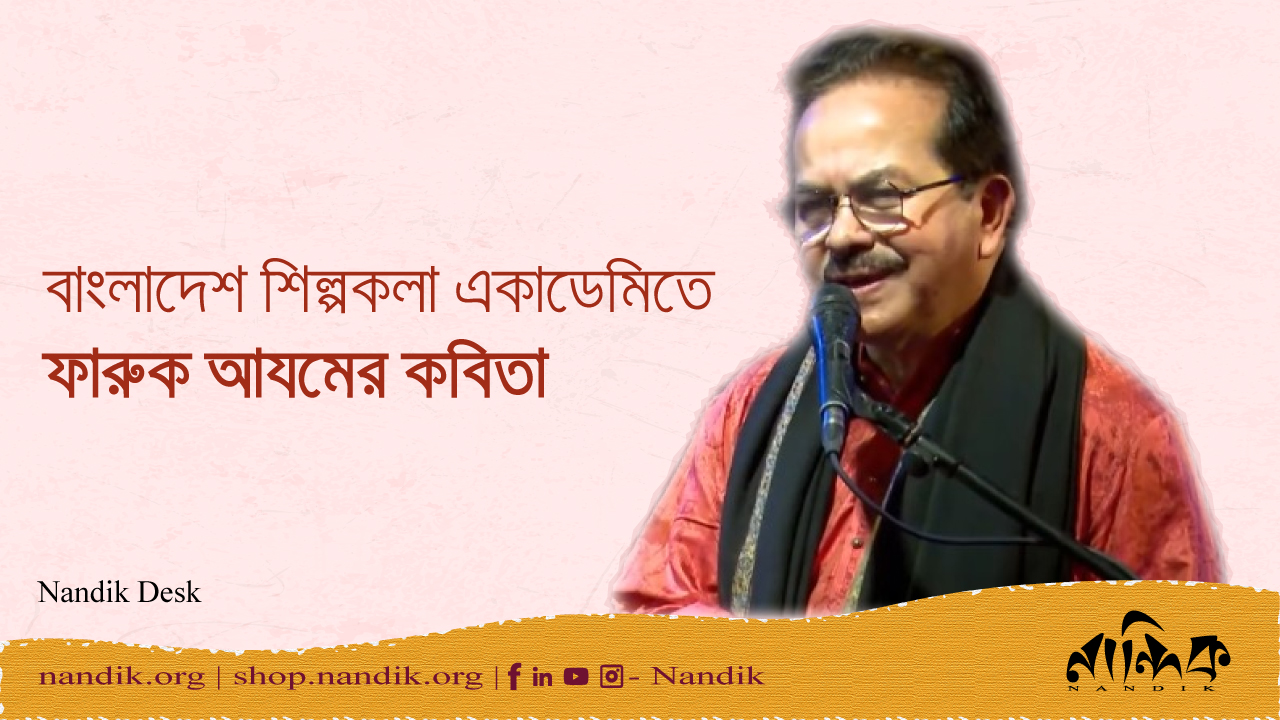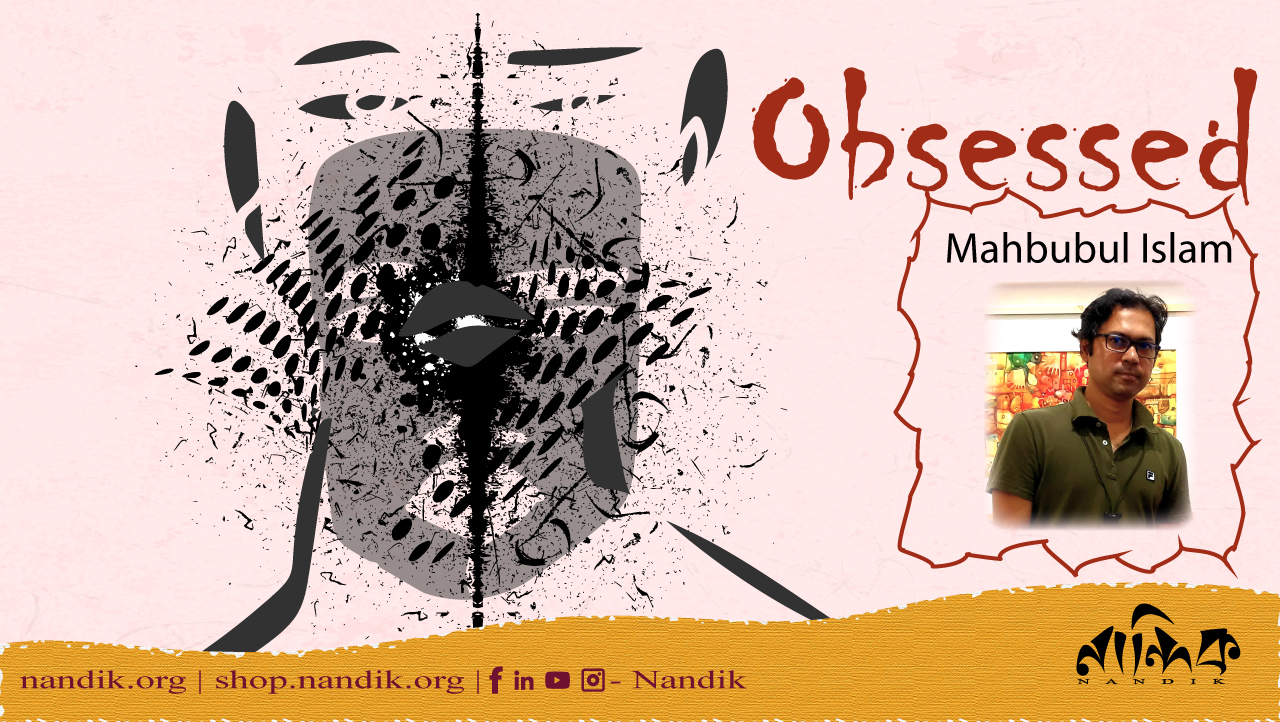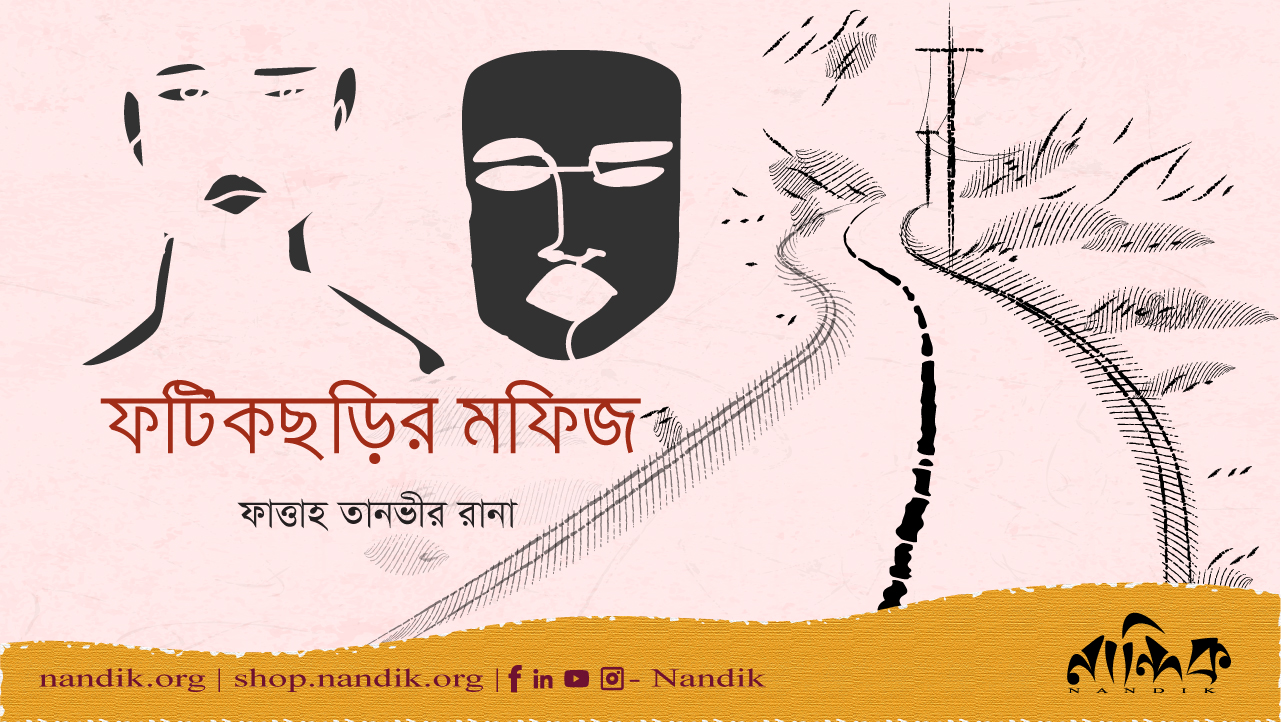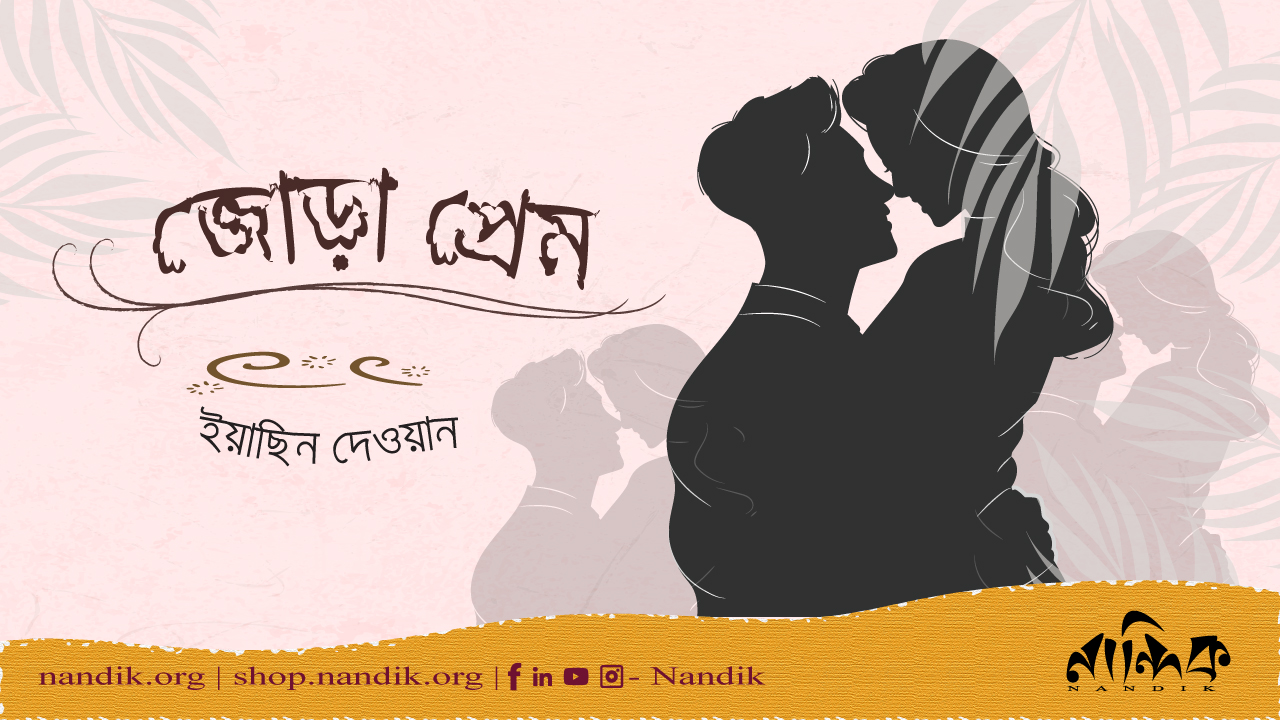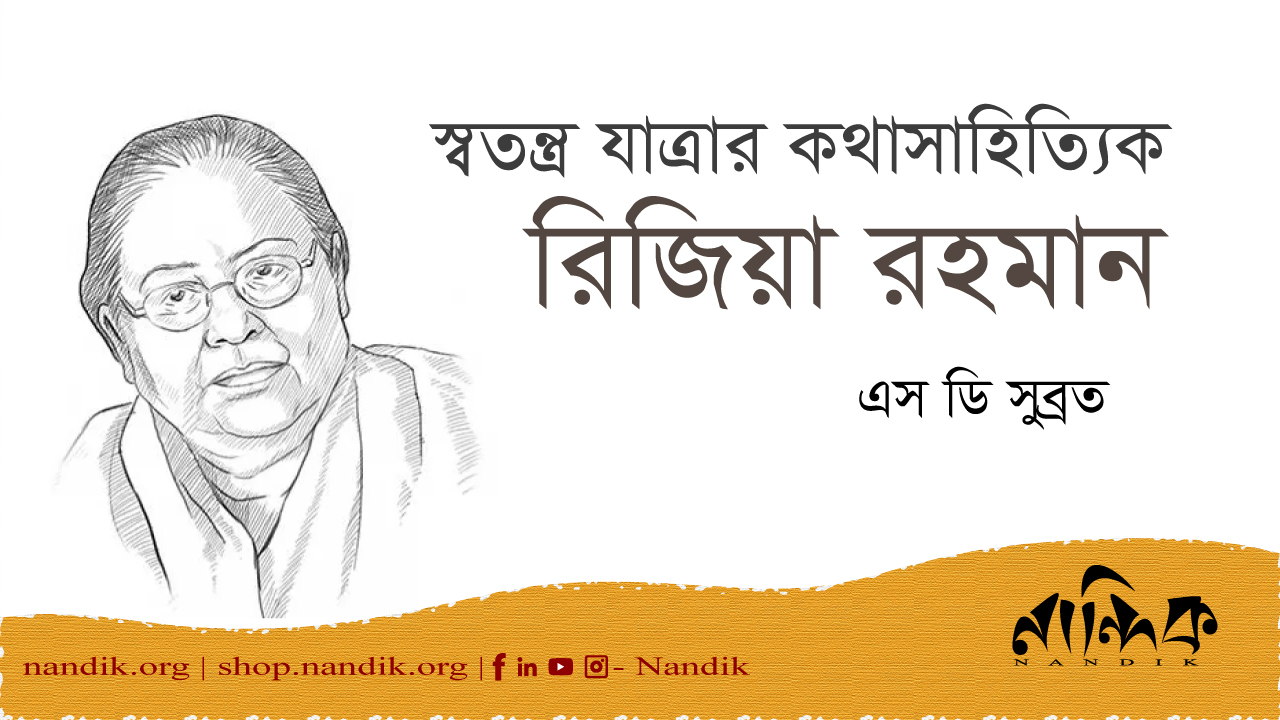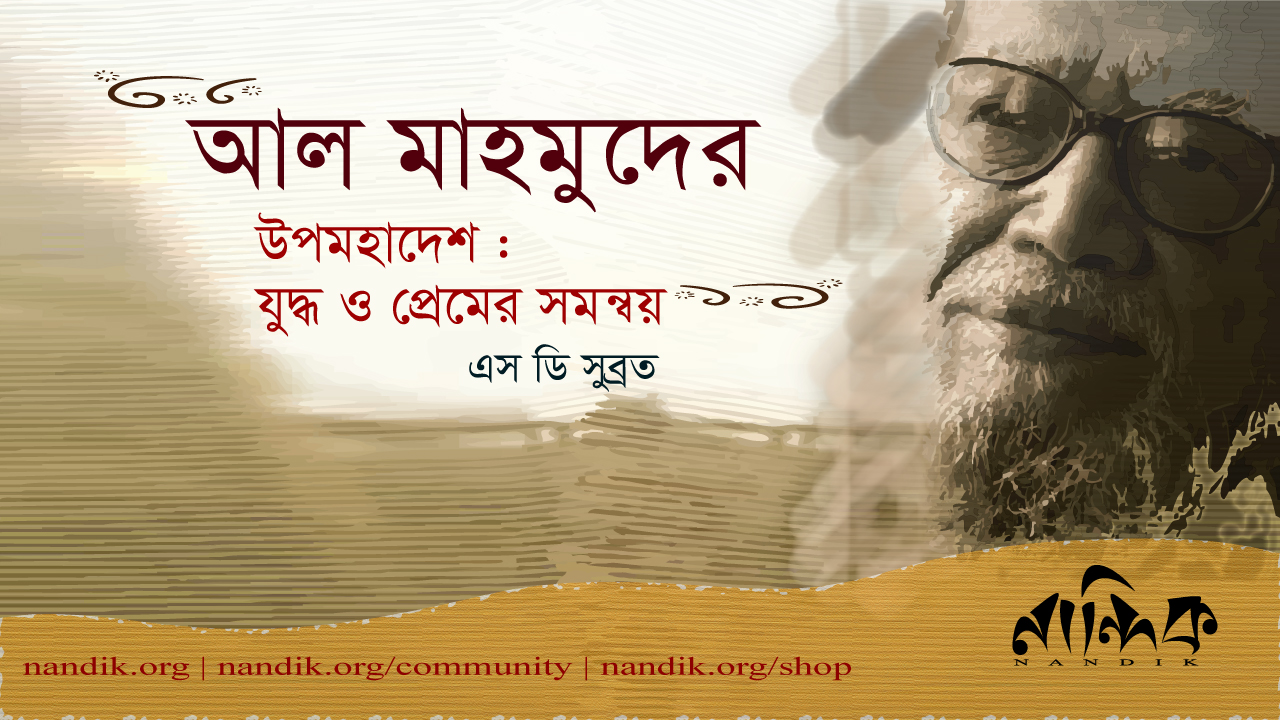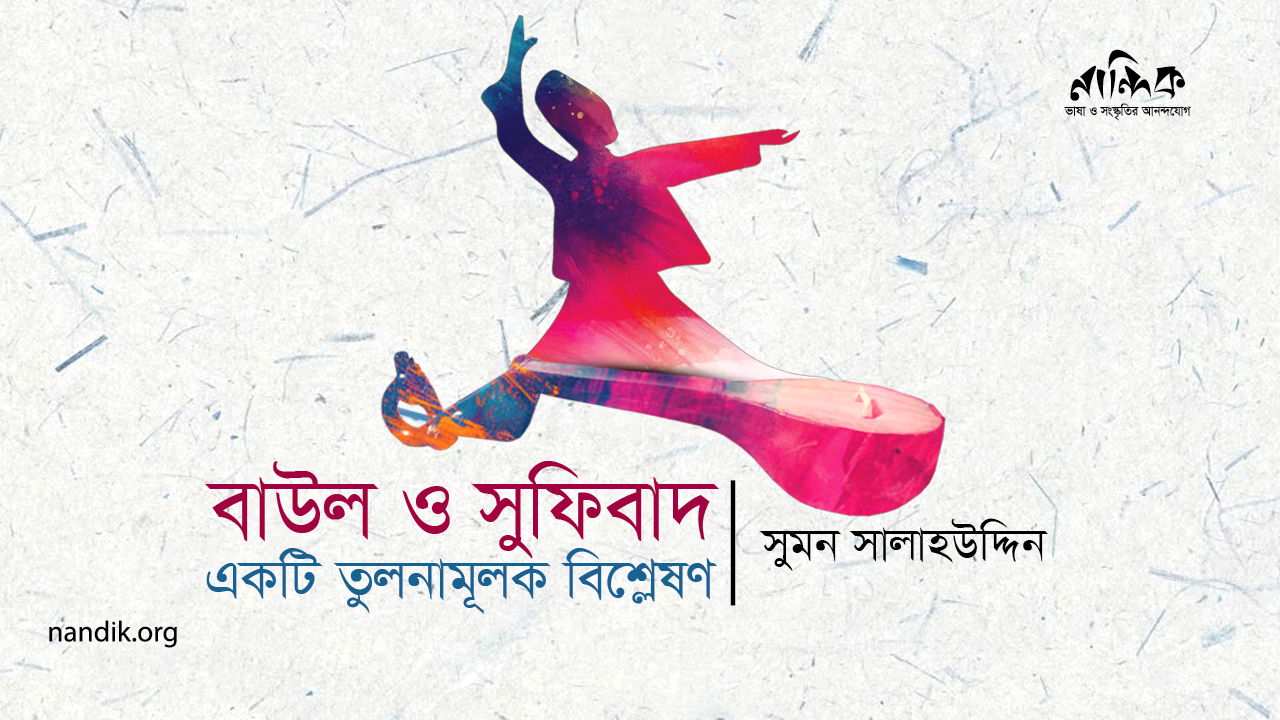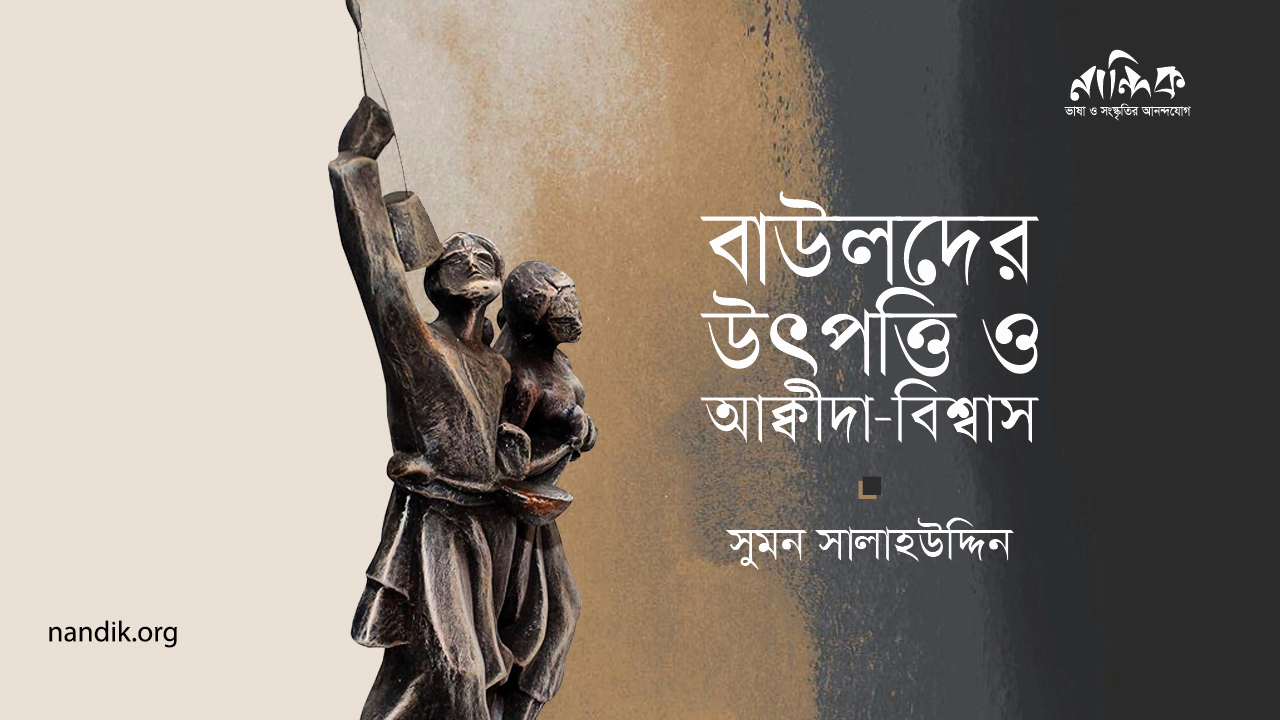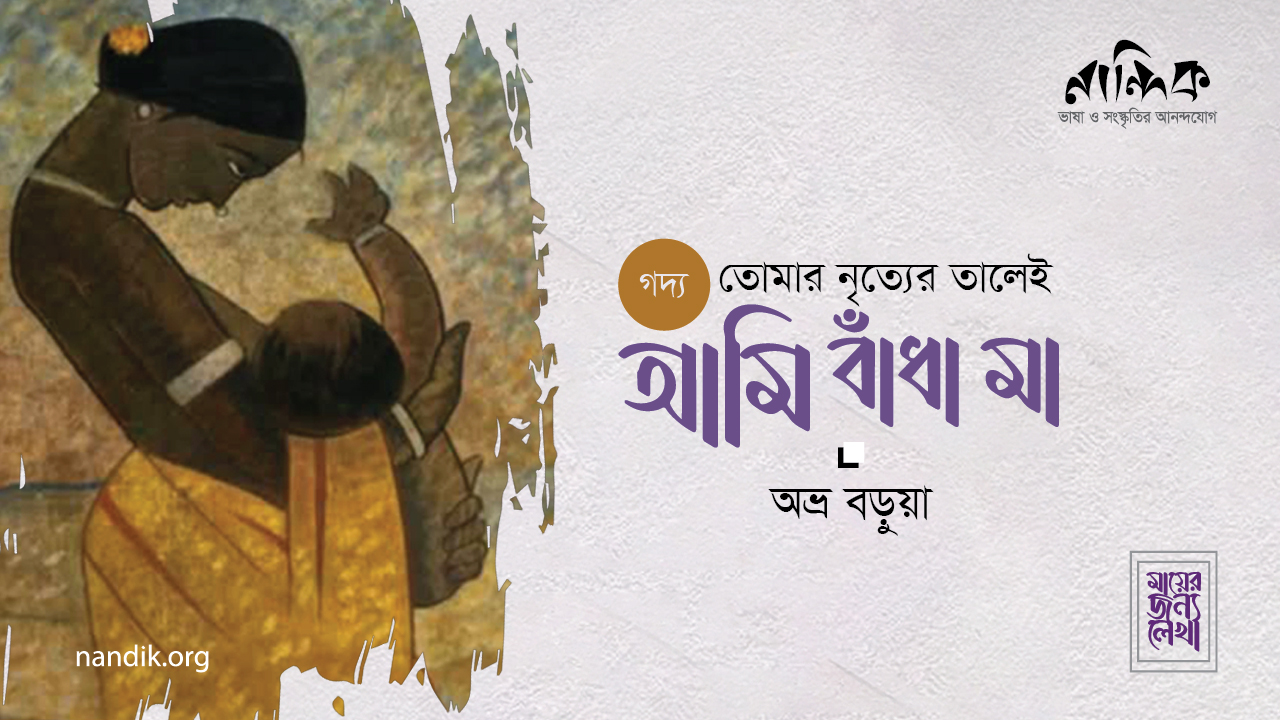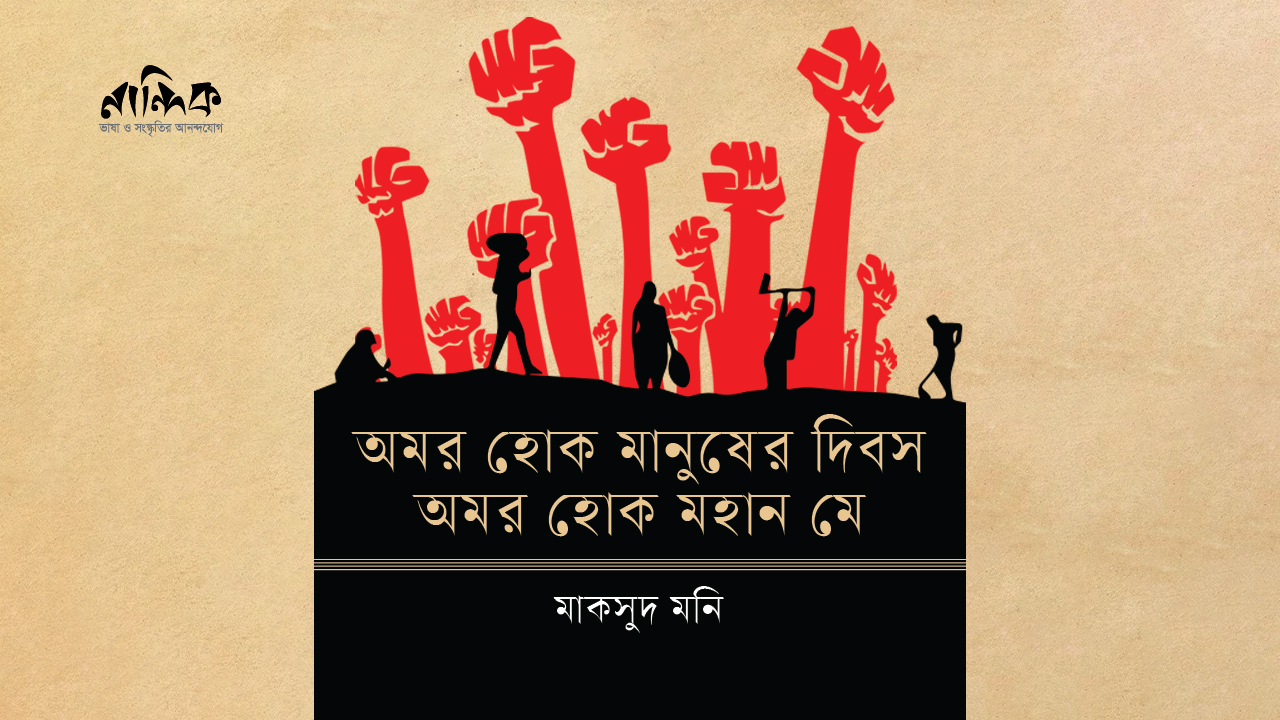লালন: জাতির সীমানা পেরিয়ে এক মানব-সাধকের যাত্রা
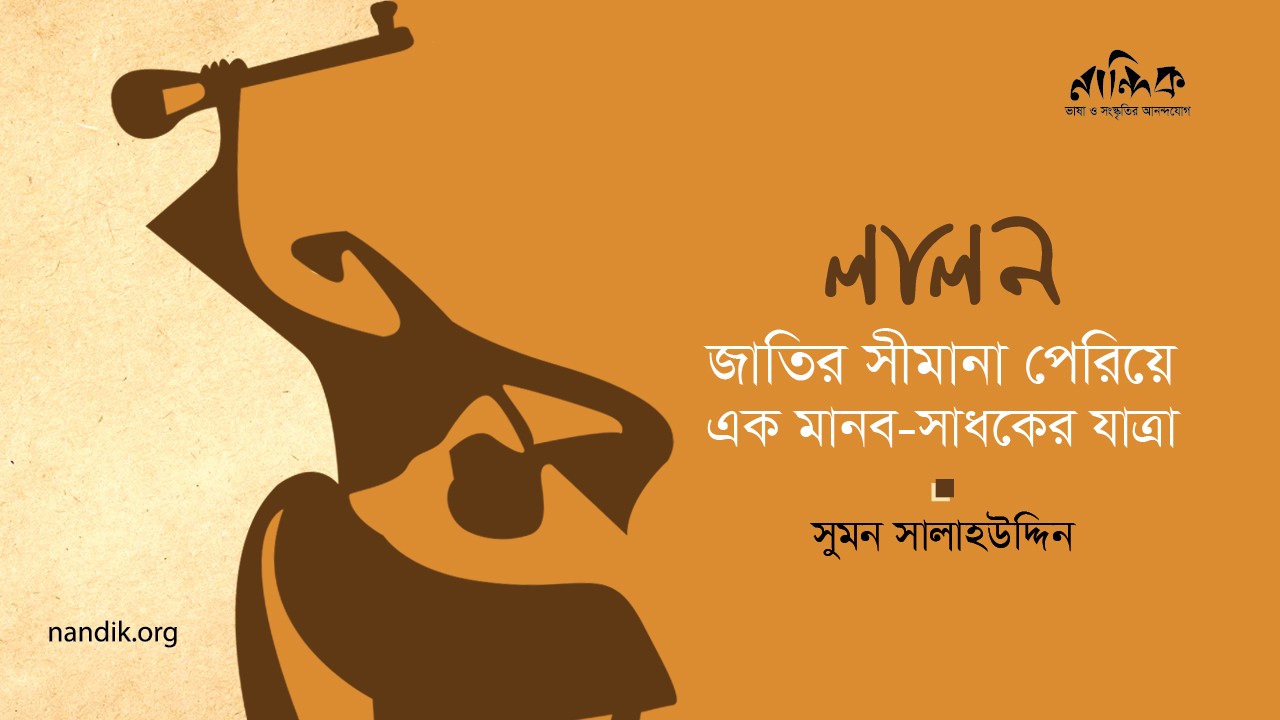
৩ লালন: জাতির সীমানা পেরিয়ে এক মানব-সাধকের যাত্রা
সুমন সালাহউদ্দিন
লালন ছিলেন না কেবল একজন সাধক বা কবি, তিনি ছিলেন জাতির সীমানা পেরিয়ে সত্যকে জানার এক ক্ষুধার্ত অনুসন্ধানী।
অন্ধকার আর বিভেদের মধ্যেও কখনো কখনো উদিত হয় এমন এক আলোর রেখা, যা ধর্ম, বর্ণ, জাত-পাতের সকল প্রথাগত সীমাকে অগ্রাহ্য করে শুধুই “মানুষ” হওয়ার দর্শন প্রচার করে। এমনই একজন ছিলেন লালন— ইতিহাস যাঁকে চিনেছে ‘ফকির’ নামে, আর ভবিষ্যৎ তাঁকে স্মরণ রেখেছে ‘দর্শন’ হিসেবে।
লালনের জন্ম এক হিন্দু কায়স্থ পরিবারে, বর্তমান কুষ্টিয়ার কুমারখালীর চাপড়া-ভাঁড়ারা গ্রামে। তাঁর প্রকৃত জন্মতারিখ আজো ঐতিহাসিক ধোঁয়াশার মধ্যে রয়ে গেছে। কারও মতে, তিনি জন্মেছিলেন ১৭৭৪ সালে, তবে সেই দাবি জোরালো তথ্যপ্রমাণে প্রতিষ্ঠিত নয়। কৌলিক পদবি ছিল ‘কর’, গোত্র ‘ঘৃত-কোশিকী’। পিতামাতার নাম— মাধবচন্দ্র কর ও পদ্মাবতী। তাঁদের পূর্বপুরুষরা ছিলেন ভারতের পানিহাটি অঞ্চলের অধিবাসী, যারা বর্গির আক্রমণের প্রেক্ষিতে আশ্রয় নেয় পূর্ব বাংলায়।
লালনের ছেলেবেলার নাম ছিল ‘ললিতনারায়ণ’। ডাকনাম ‘লালু’। একেবারে অল্প বয়সেই তাঁর বিয়ে হয়। এরপর একবার তীর্থযাত্রায় বেরিয়ে আসার পথে বসন্ত রোগে আক্রান্ত হন এবং অসুস্থ অবস্থায় পৌঁছে যান ছেঁউড়িয়ার এক কারিগর পাড়ায়। সেখানেই মুসলমান কারিগর মলম এবং তাঁর স্ত্রীর সেবায় ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে ওঠেন। পরে সিরাজ সাঁই নামের এক ফকিরের সহানুভূতি ও পথনির্দেশে তার জীবন পায় এক নতুন বাঁক— সমাজচ্যুত লালু হয়ে ওঠেন ‘লালন ফকির’।
এই রূপান্তর কিন্তু কেবল ধর্মান্তর নয়— এটা ছিল এক আত্মদর্শনের উন্মেষ। তাঁর ‘মুসলমান’ হয়ে ওঠা ছিল নিছক নামমাত্র, লালনের সত্যিকার পরিচয় খুঁজতে হলে তাকাতে হবে তাঁর গানে, তাঁর দর্শনে। তিনি কোনো ধর্মের গণ্ডিতে নিজেকে আটকে রাখেননি। বরং যাপন করেছেন এমন এক জীবন যেখানে মানুষই একমাত্র সত্য।
ছেঁউড়িয়ার আখড়াবাড়িতে নিজের মতাদর্শ প্রচার করতে থাকেন তিনি। তাঁর গানে ফুটে ওঠে জাতপাতের ঊর্ধ্বে এক মানবধর্মের জয়গান। সেই গানে প্রশ্ন উঠে—“সব লোকে কয় লালন কী জাত সংসারে?”
আর উত্তরে পাওয়া যায়, “লালন কয়, জাতির কী রূপ, দেহে তো জাত নাই…”
লালনের জীবন ছিল নিঃসঙ্গতাকে সঙ্গী করে আত্মসন্ধানের অভিযাত্রা। তাঁর কোনো সন্তানের উত্তরাধিকার থাক না থাক, তাঁর চিন্তার উত্তরাধিকার আজো জীবন্ত। তাঁকে ঘিরে গড়ে ওঠা মরমিয়া সংগীতধারা শুধু সংগীতের নয়, এক আত্মতত্ত্বের আলো।
লালন ছিলেন না কেবল একজন সাধক বা কবি, তিনি ছিলেন জাতির সীমানা পেরিয়ে সত্যকে জানার এক ক্ষুধার্ত অনুসন্ধানী। সেই তীব্র সাধনারই প্রতিফলন আমরা দেখি তাঁর প্রত্যেকটি পঙক্তিতে, যেখানে প্রশ্ন করা হয়, প্রতিস্থাপন করা হয়, এবং ভেঙে ফেলা হয় সমাজের গড়ে তোলা অলিখিত নিয়মগুলো। আজও যখন ছেঁউড়িয়ার আখড়ায় বাজে তাঁর গানের সুর, তখন মনে হয়— লালন আজো হারিয়ে যাননি। তিনি আছেন, সেই মাটির ঘ্রাণে, সেই সুরের আবহে, আর প্রতিটি মানুষের হৃদয়ে, যে মানুষ চায়— কেবল মানুষ হয়ে বাঁচতে।
সাধনার সুরে মানবতার বাণী: লালন ফকিরের জীবন ও দর্শন
অখণ্ড বাংলার লোক-ঐতিহ্যের বর্ণাঢ্য ধারায় সাধক লালন ফকির এক অনন্য ব্যক্তিত্ব। চিরায়ত ধর্মীয় কূপমণ্ডূকতা ও জাতিভেদের দেয়াল ভেঙে তিনি গড়ে তুলেছিলেন এক অন্তর্জাগতিক মানবধর্ম, যেখানে মানুষই পরমসত্যের প্রকাশ। তাঁর গান, জীবনদর্শন ও সাধনপথ বাংলা সংস্কৃতির এমন গভীর স্তরে প্রোথিত, যা কেবল ফকিরদের আখড়ায় নয়, ছড়িয়ে গেছে কবিতায়, সঙ্গীতে, এমনকি দার্শনিক চিন্তায়।
জন্ম ও জীবনরহস্য:
লালনের জন্মকাল সম্পর্কে নিশ্চিত তথ্য পাওয়া যায় না। ধারণা করা হয়, তিনি অষ্টাদশ শতকের শেষভাগে জন্মগ্রহণ করেন। তবে একটি নির্ভরযোগ্য প্রামাণ্য সূত্র থেকে জানা যায় যে, তাঁর মৃত্যু হয় ১৮৯০ সালের ১৭ অক্টোবর (১ কার্তিক ১২৯৭ বঙ্গাব্দ)। দীর্ঘ জীবন ধরে তিনি বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে ঘুরে বেড়িয়েছেন, গান গেয়েছেন, সাধনা করেছেন, আবার সমাজ-সংস্কার নিয়ে প্রতিপক্ষের রোষও বরণ করেছেন।
গুরু ও আখড়া:
লালনের গুরু ছিলেন সিরাজ সাঁই, যিনি নিজেও একজন মরমি সাধক ও গীতিকার ছিলেন। তাঁর প্রভাবে গড়ে ওঠে লালনের আধ্যাত্মিক বোধ। লালনের আখড়াটি কুষ্টিয়ার ছেউড়িয়ায় অবস্থিত, যা আজও এক তীর্থক্ষেত্র—যেখানে জাত, ধর্ম, বর্ণ, লিঙ্গ—সব বিভেদের বাইরে এক মানবিক মিলনের পরিবেশ সৃষ্টি হয়।
গান ও ভাবতত্ত্ব:
লালনের গান শুধু সঙ্গীত নয়, এক মননশীল আত্মজিজ্ঞাসা। তাঁর সৃষ্টিতে যেমন আছে মৌলিক তত্ত্বের বিনির্মাণ, তেমনি আছে অন্তর্জাগতিক উন্মোচন। তিনি প্রশ্ন করেন, “সব লোকে কয় লালন কি জাত সংসারে?”
এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি জাত-বর্ণ-বিভেদকে অস্বীকার করে বলেন, “কাজে মানুষ কহো, জাত কি রে?”
তাঁর গানে উঠে এসেছে দেহতত্ত্ব, গুরুবাদ, ব্রহ্মচিন্তা, নারীরূপে আত্মার প্রতীকায়ন, এবং সর্বোপরি মানবতাবাদ। তিনি ধর্মীয় গোঁড়ামি ও আচারের গাম্ভীর্যতা ভেঙে বলেছেন, “ধর্মের কাহার জন্ম/ কে দিয়েছে এর মর্ম?”
সমালোচনা ও লালনবিরোধিতা:
লালনের জীবদ্দশাতেই উগ্র ধর্মান্ধরা তাঁর বিরুদ্ধে নানা অপপ্রচার চালায়। কারণ, তাঁর গান ও সাধনা ধর্মীয় অনুশাসনের বাইরের সত্যকে সামনে এনেছিল, যা প্রথাগত সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে একপ্রকার প্রতিবাদ। তবে সে প্রতিকূলতাকে জয় করে তাঁর গান ছড়িয়ে পড়ে উপমহাদেশের নানা প্রান্তে।
লালন-আলোচনার পথিকৃৎ:
লালনের ভাবধারার লিখিত ঐতিহ্য সংরক্ষণে যারা উদ্যোগী হয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে প্রথম ও অন্যতম ছিলেন কাঙাল হরিনাথ মজুমদার। তিনি ‘গ্রামবার্তা প্রকাশিকা’য় লালনের গান ও জীবনবৃত্তান্ত প্রকাশ করেন। পরবর্তীতে বসন্তকুমার পাল তাঁর ‘মহাত্মা লালন ফকির’ বইয়ে একটি সংক্ষিপ্ত জীবনী সংকলন করেন, যা আজও গুরুত্বপূর্ণ রেফারেন্স হিসেবে ব্যবহৃত হয়।
রবীন্দ্র-প্রভাব ও জোড়াসাঁকোর সংযোগ:
জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির সঙ্গে লালনের একটি অনন্য সংযোগ ছিল। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর লালনের প্রতিকৃতি একেছিলেন, যা লালনচর্চার ইতিহাসে এক দুর্লভ দৃষ্টান্ত। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর স্বয়ং লালনের গানে প্রভাবিত হন। তাঁর অনেক গানে, বিশেষ করে দার্শনিক রচনায়, লালনের প্রভাব পরোক্ষভাবে প্রতিফলিত হয়েছে।
আজকের প্রাসঙ্গিকতা:
বর্তমান বৈষম্যপূর্ণ সমাজে, যেখানে ধর্মীয় অসহিষ্ণুতা ও বিভেদের বাতাবরণ ক্রমেই ঘনিয়ে আসে, সেখানে লালনের গান এক প্রবল মানবিক প্রত্যয়। তাঁর বাণী আজও উচ্চারিত হয়:
“মানুষ ভজলে সোনার মানুষ হবি।” এই সোনার মানুষই তাঁর আরাধ্য—যেখানে ঈশ্বর ও মানুষ একাকার।
লালন শুধু একজন গীতিকবি বা সাধক নন, তিনি বাংলা সংস্কৃতির অন্তর্যামী। তাঁর সৃষ্টি কেবল অতীতের সম্পদ নয়—আজকের সংকটময় সময়ে মানবতার জ্যোতিঃপথ। তাঁর গান, জীবন ও দর্শন—সবই আমাদের শেখায় সহনশীলতা, প্রশ্ন করার সাহস, এবং ভালোবাসার সর্বজনীনতা।
দেহতত্ত্বমূলক লালনের একটি গান, “আট কুঠুরি নয় দরজা আঁটা, মধ্যে মধ্যে ঝরকা কাটা”
লালন এই গানটিতে প্রতীকী ভাষায় মানবদেহকে একটি খাঁচার সঙ্গে তুলনা করেছেন। এখানে “আট কুঠুরি” বলতে বোঝানো হয়েছে মানুষের শরীরের আটটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ—মাথার খুলি, ডান ও বাম ফুসফুস, হৃৎপিণ্ড, পাকস্থলী, দুটি কিডনি এবং কোলন। এই কুঠুরিগুলোর সঙ্গে “নয় দরজা” যুক্ত, যা মানবদেহের ইনপুট ও আউটপুট পয়েন্ট হিসেবে বিবেচিত।
এই নয়টি দরজা হলো—দুই চোখ, দুই নাসারন্ধ্র, মুখ, দুই কর্ণছিদ্র, জননেন্দ্রিয় ও গুহ্যদার। আর “ঝরকা” বলতে বোঝানো হয়েছে ‘কালবের রন্ধ্রসমূহ’—যা থেকে চেতন-অচেতনের ইঙ্গিত মেলে। এই রন্ধ্রগুলির মাধ্যমে বাহ্যিক জগতের প্রভাব আমাদের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে এবং অভ্যন্তরের প্রভাব বাইরে প্রকাশ পায়।
“তার উপরে সদর কোঠা আয়নামহল তায়”
এই লাইনটিতে লালন দেহতত্ত্বের এক গভীর ব্যাখ্যা দিয়েছেন। সদর কোঠা বলতে তিনি বোঝাতে চেয়েছেন মানবদেহের চেতনার সর্বোচ্চ স্তর—যার অবস্থান মস্তিষ্কের উপরের দিকে, যা আধ্যাত্মিক চিন্তায় হায়ার সেল্ফ বা আত্মার আবাসস্থল।
বিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করলে দেখা যায়, আমরা চারপাশে যা দেখি তা আসলে আলোর নির্দিষ্ট তরঙ্গদৈর্ঘ্যের প্রতিফলন মাত্র, যা আমাদের চক্ষু গ্রহণ করতে পারে। এই দৃশ্যমান আলোকে ভিজিবল লাইট বলা হয়। এর বাইরে রয়েছে আরও বহু তরঙ্গ—রেডিও ওয়েভ, এক্স-রে, ইনফ্রারেড ইত্যাদি—যা আমরা দেখতে পাই না, তবে ব্যবহার করি। এর মানে হলো, আমাদের ইন্দ্রিয়সীমার বাইরে আরও অনেক বাস্তবতা রয়েছে যা আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় না।
আমরা যে জগতকে বাস্তব মনে করি, তা আসলে আয়নায় দেখা প্রতিচ্ছবির মতোই। আপনি যখন আয়নায় নিজের মুখ দেখেন, সেটি তো আসল আপনি নন—সেটি একটি প্রতিবিম্ব মাত্র। সেই প্রতিবিম্বে প্রাণ নেই, কর্মক্ষমতাও নেই। কিন্তু আয়নার বাইরে আপনি যিনি আছেন, তিনিই বাস্তব। এই ধারণা থেকেই লালন ‘আয়নামহল’-এর কথা বলেছেন।
আমরা যেটাকে বাস্তবতা মনে করি, তারও ওপরে রয়েছে আরও উচ্চস্তরের বাস্তবতা—যা আমাদের আত্মা অবলোকন করে। এই আত্মিক চেতনার স্তরই হচ্ছে ‘আয়নামহল’। এটি আমাদের চেতন মন নয়—বরং বিজ্ঞান যাকে বলে অবচেতন বা অর্ধচেতন মন (Subconscious mind)—তাতেই এর অবস্থান।
যারা আত্মসাধনার মাধ্যমে নিজের অন্তর্জগতে প্রবেশ করতে সক্ষম হয়েছেন, তাঁরাই কেবল এই আয়নামহলের আসল রূপ উপলব্ধি করতে পারেন। অধিকাংশ মানুষের পক্ষেই তা অনুধাবন করা সম্ভব নয়—এ কথাও লালন তাঁর গানে ইঙ্গিতপূর্ণভাবে প্রকাশ করেছেন। লালনের এই গানটি কেবল কবিত্বের দৃষ্টিতে নয়, দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকেও গভীরভাবে বিশ্লেষণযোগ্য। এটি আত্মজিজ্ঞাসা, আধ্যাত্মিকতা ও চেতনার স্তর নিয়ে ভাবতে উদ্বুদ্ধ করে, যা আজকের যুগেও সমানভাবে প্রাসঙ্গিক।
বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমিতে ফারুক আযমের কবিতা
nandik2026-01-11T20:35:04+00:00January 11, 2026|
Obsessed by Mahbubul Islam
Mahbub Islam2025-11-14T16:55:18+00:00November 14, 2025|
ফটিকছড়ির মফিজ
Fattah Tanvir2025-11-10T17:45:19+00:00November 10, 2025|
জোড়া প্রেম
Yasin Dhawan2025-11-06T16:46:09+00:00November 6, 2025|
শারীরিক সম্পর্ক কোনো দুর্ঘটনা নয়
Sudipto Mahmud2025-11-05T19:33:30+00:00November 5, 2025|